শতানীক রায়ের প্রবন্ধ
সেই আমি-র মৃত্যু
মৃত্যু হল সেই চরম শূন্যতা যা আমাদের চেতনার ওপরের অন্য স্রোত। সেখানে অসম্ভব এক দোলন, দেহের চারপাশে বহমান সে-শূন্য কেবলই অজানা থেকে যায়। মঙ্গল চিহ্নে যাকে বাঁধা যায় না, আবার অমঙ্গল বলেও তাকে দাগিয়ে দেওয়া স্পর্ধার হয়ে ওঠে। আমার দেহ আছে সে আমার বোধের আয়তনের মধ্যে পড়ছে তবে যবে আমি থাকব না তখন!! আমার দেহের বিনষ্টকরণের পর আমি কী করে জানব আমি নেই ? আমি যে দেহে মনে সংযুক্ত ছিলাম পৃথিবীতে, সমাজে, মহাবিশ্বে, ব্রহ্মাণ্ডে আর দেহের ক্ষয় হওয়ার পর সমস্ত বোধ দেহহীন হওয়ার পর আমি কি আদতেও জানব যে আমি আর নেই? মৃত্যু নামক একটি প্রক্রিয়া আমার কাছ থেকে আমার সত্তাটুকু কেড়ে নিয়ে আমাকে দেহশূন্য করে ছাড়বে। আমি জানতে পারব, বুঝতে পারব একটা সময় শরীরের ক্ষয়িষ্ণু আচরণ এবং এমন একটি সময় আমি বোধ পুরোপুরিভাবে এই শরীর থেকে মুছে যাবে। এই না থাকাটাই আমাকে বড্ড বেশি ভাবায়। তখন মৃত্যু নামক ক্রিয়াকে বুঝেও বুঝি না।
অস্তিত্বের তল অবধি খুঁড়ে বের করলেও যা মেলে না তা আসলে মৃত্যু? পেঁয়াজের খোসা ছাড়াও পেঁয়াজের আসল শরীরের খোঁজ পাওয়া দুষ্কর! শরীর ছাড়িয়ে যাও, আরও শরীর, বিরাম নেই— তাহলে এখান থেকেই শুরু এমন এক ক্ষয়ের যার অভিপ্রায় বলে কিছু নেই, ভাষা বলে কিছু নেই কেবল এমন একটি চাপা প্রক্রিয়া যার পেছনে বৃথা আমরা দৌড়ে বেড়াই, জাপটে ধরার চেষ্টা করি আর যখন তা পারি না, সে-মুহূর্তে জন্মায় শূন্যতার বোধ। আমার একান্ত মত— মৃত্যু সেই খোঁজ যার পেছনে ছুটতে ছুটতে আমরা টের পাই আসলে সে নেই। না থাকার মধ্যে দিয়ে তার প্রকাশ এবং বিবেচ্য বিষয় হল তবে মৃত্যু অথবা না-মৃত্যু?
পুরাণে মৃত্যুকে নারীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। অভীক বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যপ্রিয় ঘোষ স্মারক বক্তৃতা “জড় মন চেতনা— মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে” থেকে কিছুটা তুলে ধরছি— ‘কমললোচনা এক নারী করুণস্বরে বিলাপ করে চলেছেন; মৃত্যু তার নাম। প্রজাপতি ব্রহ্মার জীব-ধ্বংসে অক্ষমতার ক্রোধকে নির্বাপিত করার এবং তাঁর কর্ম সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে এই নারীর ওপর, কিন্তু অধর্মের ভয়ে ভীতা হয়ে করজোড়ে ব্রহ্মাকে নিবেদন করছেন “আমি কদাচ বিলপমান প্রাণীগণের প্রিয়তম প্রাণ বিনাশ করিতে সমর্থ হইব না। হে পিতামহ! আপনি, আমাকে অধর্ম হইতে রক্ষা করুন।“ কিন্তু কে এই মৃত্যু ? কেনই বা তার এত বলবীর্য ও পৌরুষ ? সত্যযুগের রাজা অকম্পনের পুত্র হরি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হওয়ার পর শোকাকুল রাজা এই প্রশ্ন করলেন নারদকে।‘[১] যেখানে পুরাণে মৃত্যুকে দেবীরূপে, নারীরূপে কল্পনা করা হয়েছে সেখানে শোকাকুল রাজা অকম্পন তাঁর পুত্রের মৃত্যুর পর ‘মৃত্যু’-কে পুরুষের পৌরুষের অভিধায় ভূষিত করেছেন। একজন মানুষের শেষ হয়ে যাওয়ায়, চিরতরে পৃথিবী থেকে তাঁর শরীরী সত্তা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় গভীর এবং প্রচণ্ড তীব্র শূন্যতার জন্ম হয়। এই চলে যাওয়া মৃতের আত্মজনের মনে এত তীব্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয় যে তখন সে রাজা অকম্পনের মতো মৃত্যুকে পুরুষের পৌরুষ এবং বলবীর্যের সঙ্গে তুলনা করে তাঁর অস্তিত্ব নিয়ে, তাঁর ক্রিয়াশক্তি নিয়ে প্রশ্ন করে বসে। এই মৃত্যুই তবে জীব জগতে এক মুখ্য শক্তি যার ওপরে কোনও শক্তি নেই যা জীবনের মাহাত্ম্য আমাদের চরমভাবে বুঝিয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ এখানে প্রশ্ন মৃত্যুর অস্তিত্ব নিয়ে। অদতেও কি মৃত্যু আছে? আমাদের জন্ম আছে মাতৃগর্ভে, আমাদের আত্মপ্রকাশ আছে পূর্ণাঙ্গ মনুষ্য দেহে এবং পৃথিবীতে তার ভূমিষ্ঠ হওয়াও আছে। নারদ এ বিষয়ে যা শুনেছিলেন তাই বললেন রাজাকে : ‘সর্বলোকের পিতামহ ব্রহ্মা মনুষ্যসহ সকল প্রাণীকুল সৃষ্টি করার সময়ে দেবী বসুন্ধরার কাতর অনুনয়ে বিরত হলেন। বসুন্ধরা বিশাল প্রাণীকুলের ভারে নিপীড়িতা, অথচ পিতামহ কিছুতেই সৃষ্টি সংহারের পথ নির্ণয় করতে পারছেন না। এমন অবস্থায় তাঁর ক্রোধ প্রভাবে আকাশে অগ্নি উৎপন্ন হয়ে সমস্ত সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে লাগল। এগিয়ে এলেন রুদ্র, সৃষ্টি রক্ষার জন্য ব্রহ্মাকে কাতরভাবে প্রার্থনা জানালেন। “অনন্তর লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রজাদিগের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত পুনরায় অন্তরাত্মাতে স্বীয় তেজ ধারণপূর্বক অগ্নির উপসংহার করিয়া সৃষ্টিহেতু প্রবৃত্তিধর্ম ও মোক্ষহেতু নিবৃত্তিধর্ম কীর্তন করিলেন। তিনি যখন ক্রোধজনিত হুতাশন সংহার করেন, তৎকালে তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার হইতে কৃষ্ণ, রক্ত ও পিঙ্গলবর্ণ, রক্তজিহ্বা, রক্তাস্য ও রক্তলোচন, বিমল-কুণ্ডলালঙ্কৃত, বিবিধ ভূষণে বিভূষিত এক নারী প্রাদুর্ভূত হইলেন।“'[২] এখানে মৃত্যুরূপা নারীর রূপ লক্ষণীয়। তীব্র ভয়ঙ্কর তাঁর রূপ আর মৃত্যুর গাঢ় প্রাজ্ঞতা ও প্রক্রিয়াশীলতা প্রকাশ পায়। ‘যেহেতু তিনি উদ্ভূত হয়েছেন ব্রহ্মার সংহার বুদ্ধি প্রভাবিত ক্রোধ থেকে তাই এই নারীকে মৃত্যু আখ্যা দিয়ে তাকে পৃথিবীর সমুদয় প্রজাগণকে সংহার করার দায়িত্ব দেওয়া হল। কিন্তু নারীর স্নেহ-বাৎসল্য-করুণারসবোধ মৃত্যুর মনে সংশয় আনল। মৃত্যু তখন বহু সহস্র বছর তপস্যা করে প্রজাপতির কাছে এই আশ্বাস পেলেন যে, লোভ, ক্রোধ, অসূয়া, ঈর্ষা, দ্রোহ, মোহ ও নির্লজ্জতা নামক পুরুষ-ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ প্রাণীগণের দেহ ভেদ করবে। এই কাজে লোকপাল যম, ব্যাধিসকল এবং ব্রহ্মা স্বয়ং মৃত্যুকে সহায়তা করবেন; মৃত্যুর কোনো অধর্ম হবে না। পিতামহ বললেন, “আমার করতলে তোমার যে সমুদয় অশ্রুবিন্দু নিপাতিত রহিয়াছে, উহা প্রাণীগণের আত্মসম্ভূত ব্যাধিরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রাণ সংহার করিবে ; তাহা হইলে তোমার অধর্ম হইবে না।“…’[৩] আমাদের বারবার একই জায়গায় এনে দাঁড় করাচ্ছে, পূর্ণ জীবনের শেষ প্রান্তে যেখানে জড়া, ব্যাধি সব মিলে দেহের ক্ষয় করছে আর মৃত্যু নামক একটি জাগতিক ঘটনা ঘটছে যার পরে দেহ বলে আর কিছু থাকে না কেবল সেই মানুষের বিনাশের পরে সে থেকে যায় সবার মধ্যে, কেবল তাঁর দেহের জায়গায় এসে যায় চরম শূন্যতা— বাক্যমনাতীত।
মৃত্যুর অস্তিত্ব এবং রূপতত্ত্ব থেকে এখানে উঠে এল মৃত্যুর ‘ধর্ম’। ধর্ম আর অধর্মের তুলনামূলক, চিরাচরিত দ্বন্দ্বে দৃষ্টান্ত দেখানো হলেও এখানে মৃত্যুর ‘ধর্ম’ এসেছে অর্থাৎ বৈশিষ্ট। মৃত্যু সে তো একা ক্রিয়াশীল নয়, সঙ্গে ব্যাধি, যম এবং ব্রহ্মাও পাশাপাশি সহায়তা করেন। এই নারীস্বভাব বিশিষ্টা মৃত্যু আসলে কোমল স্বভাবের, সে দেহের বিনাশ করেন। কোথায় সে? মৃত্যু বলে কিছু হয়? সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন অর্থাৎ জন্ম আর এখান থেকে জানলাম তিনি মৃত্যুর সহকারী। জন্মের পাশেই মৃত্যু, মনে হচ্ছে জন্মও আসলে মৃত্যুর নির্মাণ অন্য কথায় তাঁকে বলব না-মৃত্যু। মৃত্যু অথবা না-মৃত্যু— এক পরাযৌগিক ক্রিয়া।
আমি ছেলেবেলা থেকে এমন বহু মানুষ দেখে আসছি যাঁরা মৃত্যুর প্রসঙ্গ এলেই নানা কথায় প্রসঙ্গ বদলানোর চেষ্টা করে। মৃত্যু তাঁদের কাছে এক ভীতির কারণ। এমন অনেক বয়স্ক মানুষদের দেখেছি যাঁরা মৃত্যুর ভয়ে সবসময় ক্লিষ্ট হয়ে থাকে। মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর প্রথম মহাকাব্য, গিল্গামেশ্ রচিত হয়েছিল। হোমারের দুটি মহাকাব্যের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে সম্ভবত অনামিক রচয়িতার রচনা, গিল্গামেশ্ যার মূল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি মৃত্যুকে ঘিরে। মৃত্যু অর্থাৎ দেহের ক্ষয়ক্রিয়া ও সার্বিক রক্তমাংসের সত্তার বিনাশ।
এই মহাকাব্যে, গিল্গামেশ্ মৃত্যুকে জয় করতে চেয়েছিলেন, অনন্ত জীবন (Eternal Life) লাভ করতে চেয়েছিল। বন্ধু এনকিডুর মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত হয়ে দিনের পর দিন বিলাপ করেছিল গিল্গামেশ্। তারপর একদিন এনকিডুর মৃতদেহে কীট দেখা গেলে গিল্গামেশ্ একটি রাজকীয় অন্ত্যেষ্টির আয়োজন করে সমাধির ভেতরে অলংকৃত করলেন বন্ধুর মৃতদেহকে। তারপর শুরু হয় গিল্গামেশের দীর্ঘ বিলাপ। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, মৃত্যুকে জয় করার এবং অনন্ত জীবন লাভ করার। গিল্গামেশ্ মহাকাব্যে মৃত্যুর পাশাপাশি আরও অনেক অনুসঙ্গ আছে যা কাহিনির মূল দর্শনকে অলংকৃত করেছে। আমরা এখানে মহাকাব্যটিকে সংক্ষেপে একটু জানব:
“গিল্গামেশ্ উরুক দেশের রাজা ছিলেন, তাঁর মা এক দেবী, যাঁর কাছ থেকে তিনি আশ্চর্য সৌন্দর্য, শক্তি এবং চঞ্চলতা পেয়েছিলেন। মানুষ পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন মরণশীলতা। এক দিক থেকে বলতে গেলে গিল্গামেশের মা তাঁর জীবনে গৌণ চরিত্র, কখনও সখনও তাঁর গিল্গামেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা হতো, এটুকুই। পিতা কোনও মর্ত মানুষই হবেন, কিন্তু মাঝে মধ্যে মানসিক সংকটে তিনি ‘লুন্ডল্বান্ডা’-কে পিতৃরূপে, অথবা পিতৃস্থানীয়রূপে ডাকেন। এই গিল্গামেশ্ দুই তৃতীয়াংশ দেবতা, এক তৃতীয়াংশ মানুষ। সে ঘুরে বেড়াত জন্তুদের মধ্যে, অত্যন্ত উদ্ধতভাবে। কিন্তু তাঁর হৃদয়ের আর্তি ছিল মানুষ বন্ধু পাবার জন্যে, একটি ভাইয়ের মতো বন্ধুর জন্যে। এ জন্যে সে দেবতাদের অনুনয় করত। দেবতারা তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করলেন, এনকিডুকে সৃষ্টি করলেন, গিল্গামেশের সোদরোপম বন্ধু হিসেবে। এই এনকিডু স্বাস্থ্যবান, বীর এবং স্থির। দেবী ঈশতার তাকে পাবার জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠলেন এবং এনকিডু তাঁর কামনাকে চরিতার্থ করলেন। এক সপ্তাহ তাঁরা উন্মাদনায় কাটানোর পর এনকিডু তাঁকে ত্যাগ করে এলেন। ফিরে যখন এলেন, তাঁর জীবজন্তু বন্ধুরা তাঁকে পরিহার করতে লাগল, তখন তিনি গিল্গামেশের কাছে এলেন। গিল্গামেশ্ অত্যন্ত সমাদরে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।”[৪] গিল্গামেশ্ জঙ্গলে ( Forest of Cedar)-এ অভিযানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এনকিডু বারবার সাবধান করেছিল যে, সেই জঙ্গলের রক্ষী হামবাবা নামক একটি দানব। সেই দানবের বর্ণনায় অদ্ভুতভাবে মৃত্যুর প্রসঙ্গ এসেছে : ‘Humbaba, his voice is the Deluge / his speech is fire, and his breath is death…’[৫] মৃত্যুর সঙ্গে ভয় মিশ্রিত হয়ে এখানে সেই রক্ষীর নিশ্বাসকে মৃত্যুর সঙ্গে কল্পনা করা হয়েছে। মৃত্যুর নিয়ে চিরকাল মানুষের ভয় কাজ করে। আসলে মৃত্যু কোনো প্রক্রিয়া নয় এবং পাশাপাশি বলতে গেলে মৃত্যু একটি প্রক্রিয়াও। দ্বন্দ্ব চরমভাবে আছে। আসলে জীবদেহের life span আছে এবং আমাদের শরীরে ক্ষয়ের ক্রিয়া চলতেই থাকে প্রতিদিন প্রতিক্ষণে যা এক অনন্ত প্রক্রিয়ার রূপ নেয়। এই শরীরের শেষ পরিণতি বৃহৎ মৃত্যু। মৃত্যুর দর্শনে একটি স্ব-বিরোধ বারবার আসে ও আসবেও কারণ মৃত্যুকে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, তবুও মৃত্যু হয়। প্রত্যেক জীবের মৃত্যু হয়। প্রতিদিনের মৃত্যু-কে আমরা বিজ্ঞানের ভাষায় Cell Death বলে থাকি কিন্তু সে হল আংশিক বিনাশ। এই আংশিক মৃত্যুতেও আমাদের মনের মৃত্যু হয়— Metaphysical Death. এই দেহ কোষের মৃত্যু আমাদের বিষণ্ণ করে দেয়, তাই বিভিন্ন সময়ে দার্শনিক এবং কবিদের লেখায় অজান্তেই মৃত্যু প্রসঙ্গ নানা পরিধি নিয়ে উঠে আসে। একটি রক্তমাংসের পিণ্ড যা চেতনযুক্ত এবং পুরোপুরিভাবে তাঁর অস্তিত্বের বিনাশ হচ্ছে, কিন্তু বিশেষ একজনের দেহ কোষের মৃত্যুকে আমরা মৃত্যু বলে গণ্য করি না। বিপরীত কিন্তু পূর্ণ-মৃত্যু এমন এক ঘটনা যাকে আমরা ধরতে পারবই না এবং অদৃশ্য সে-মৃত্যু থেকে ভয়ের জন্ম হয়, আস্তিত্বিক ভীতি। আসলে মৃত্যুর পরিভাষা আমাদের (মানুষদের) তৈরি। এই বর্তমান থাকা থেকে আমাদের মৃত্যুর পর দেহ থেকে চলে যাওয়া মায়ার জন্ম দেয়, শরীরের প্রতি মায়া!! ঘুরে-ফিরে আত্মার প্রসঙ্গ চলে আসে। গিল্গামেশ্ মহাকাব্যেও মৃত্যু নামক ঘটনাকে ঘিরেই কাহিনির নির্মাণ। পরের অংশে দেখি : অনেক দেবতা গিল্গামেশের আশ্চর্য শৌর্য ও শক্তির জন্য তাকে ঈর্ষা করতেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে তার শান্তিক্ষয়ের জন্য কৌশলে তাকে এক গণিকার কাছে পাঠালেন। কিন্তু গিল্গামেশের যৌন উগ্রতা এত প্রবল ছিল যে কুমারী, সধবা ও বিধবার আর্তনাদে বাতাস ভারী হয়ে উঠল। এ আর্তনাদ যখন দেবতাদের কানে উঠল তখন তাঁরাও বিচলিত হলেন। এ দিকে এনকিডু গিল্গামেশের সান্নিধ্য হারিয়ে খুবই বিমর্ষ বোধ করলেন। একা একা বনে বনে ঘুরে কান্নাকাটি করতে লাগলেন। এনকিডু কেঁদে কেঁদে শীর্ণ হয়ে যেতে লাগলেন এবং দেবতাদের ওপর দোষারোপ করতে লাগলেন, লঘুপাপে গুরুদণ্ডের জন্য। ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হতে হতে একদিন তাঁর মৃত্যু হল। গিল্গামেশ্ বন্ধুর উদ্দেশে উচ্চস্বরে বিলাপ করতে লাগলেন। দিনের পর দিন যেতে যেতে মৃতদেহের শরীরে যখন কীট দেখা গেল তখন তিনি একটি রাজকীয় অন্ত্যেষ্টির আয়োজন করলেন। তারই অনুষ্ঠিত হল এক উৎসব। তারপর গিল্গামেশ্ এনকিডুর দেহ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলেন। দেহটি অলংকারে মুড়ে দিলেন এবং সমাধির অভ্যন্তরে নামিয়ে দিলেন।
এইবার শুরু হল গিল্গামেশের অশান্ত বিলাপ, যা কোনও প্রবোধই মানল না। তিনি নিরন্তর কেঁদেই চলেছেন। দিনের পর দিন উচ্চৈস্বরে আর্ত বিলাপ করার পরে গিল্গামেশ্ সিদ্ধান্ত নিলেন, মৃত্যুকে জয় করতে হবে, এবং অনন্ত জীবন লাভ করতে হবে। একজনই অমরত্বের অধিপতি, তাঁর কাছে গিয়ে অমৃত ছিনিয়ে আনতে হবে। এর জন্যে প্রথম কাজই হল যে, এর উপায় বিধান করতে পারে, তেমন লোকের সন্ধান করে তার নির্দেশমতো চলে অমরত্ব লাভ করা। এনকিডুর মৃত্যুতে তিনি জানলেন তাঁকেও একদিন এভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং শেষ পরিণতি সমাধিতেই। এইটে কোনও মতেই মেনে নিতে পারছিলেন না বলে দেবতারা তাঁকে শাস্তি দিলেন। এনকিডুর মৃত্যু সেই শাস্তি। গিল্গামেশের কাছে এনকিডু ছাড়া জীবন দুর্বহ। তাই তিনি যে-কোনও মূল্যে বন্ধুর শেষ পরিণতি থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করে মৃত্যুকে জয় করে দেবতাদের মতোই অমর হবেন—এই সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তার নিঃসঙ্গতার নীরব আর্তনাদ বুকে চাপা রইল। অবশেষে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন ‘উতনাপিশ্তিম্’—যাকে লোকে ‘দূরের মানুষ’ বলে, তাঁর কাছে যাওয়ার। সেই দিকে যেতে যেতে তাঁর দেখা হল অর্ধ-দেবী সিদুরির সঙ্গে, যিনি সুরা নির্মাণ করতেন। সিদুরি গিল্গামেশকে পথের নির্দেশ দেবেন। সিদুরির কাছে গিল্গামেশ্ নিজের শৌর্য নিয়ে বড়াই করলেন, বললেন বনের সব সিংহ তিনি মেরেছেন এবং ‘হুম্বাবা’ নামক দানবকে যুদ্ধে হারিয়ে হত্যা করেছেন। কিন্তু সিদুরি তাঁকে স্পষ্টই বলে দিলেন যে, তাঁর অমৃত অন্বেষণে ব্যর্থ কারণ, দেবতারা অমৃতকে নিজেদের জন্যই সংরক্ষণ করেছেন, অতএব গিল্গামেশের উচিত ভোগবিলাসের জীবন বেছে নেওয়া। কিন্তু গিল্গামেশ্ তাঁর সংকল্পে অটল। তিনি সিদুরিকে রাজি করালেন পথের নদীটি পেরোবার জন্যে একজন মাঝির সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিতে। শেষপর্যন্ত সিদুরি সেই নাবিকের সঙ্গে গিল্গামেশের পরিচয় করিয়ে দিলেন যে, সেই পথের সবই জানে।[৬] পথে দুষ্প্রবেশ্য অরণ্য পেরোনোর পর এসে পৌঁছলেন দিগন্তবিস্তৃত নদীর ধারে। দীর্ঘদিনের শ্রমের পর গিল্গামেশ্ এসে পৌঁছলেন সেই বিখ্যাত ‘উতনাপিশ্তিম’-এর নগরীর বন্দরে। গিল্গামেশ্ উতনাপিশ্তিমকে তাঁর বন্ধুর মৃত্যুর কথা জানালেন এবং তাঁর বিমর্ষতার কারণ জানালেন এবং তাঁর কাছে অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা করলেন। এ কথাগুলো শুনে উতনাপিশ্তিম তাঁকে বলেন, অমরত্ব দেবতাদের একমাত্র অধিকার, কোনও মূর্ত মানুষ তা পেতে পারে না। গিল্গামেশের মৃত্যু অবশম্ভাবী এবং সে জন্যে এখন তাঁর উচিত ভোগবিলাসের মধ্যে জীবন কাটানো।
গিল্গামেশ্ নাছোড়বান্দা, অমরত্বের সন্ধান তাঁর চাই।উতনাপিশ্তিম গিল্গামেশকে একটি নদীর খোঁজ দিলেন। সেখানে বিশেষ একটি ছোটো গাছের পল্লব আছে যা খেয়ে নিলে সে অমর হতে পারবেন। পল্লবটি সংগ্রহ করলেও একটি সাপ সেটিকে আত্মসাৎ করল। গিল্গামেশ্ হতাশ হয়ে তাঁর উরুক নগরের দিকে যাত্রা শুরু করলেন।
আসলে গিল্গামেশের মৃত্যু জয়ের আকাঙ্ক্ষা—অমরত্বের সন্ধান আমাদের চেতনার মধ্যে থাকা এক অমোঘ ভয়কে উজাগর করে। তাঁর অমরত্বের সন্ধান সমস্ত বাধা পেরিয়ে, জঙ্গল পেরিয়ে, নদী পেরিয়ে যেন এক বিভ্রমের দিকে যাত্রা। আমরা আজীবন এক বিভ্রমের মধ্যে থেকে কর্মের দিকে, বাস্তবের দিকে নজর না দিয়ে কাটিয়ে দিই। আসলে যা নেই তারই খোঁজে আমরা বিভ্রম পোষণ করে চলি। এই বিভ্রমের গোপন অন্তঃস্রোতে মিশে আছে যৌনতার তীব্র অনুসন্ধান। একসময় মৃত্যু ভ্রমোনাশ করে। দীর্ঘ খোঁজ সেই অপূর্ণ রমণের প্রতীক। আর এই সন্ধানের ভেতর এক শরীর শরীর ভাব আছে; এর বিপরীতে মৃত্যু শরীরের বিনাশ ঘটায়,অস্তিত্বের বিনাশ ঘটে। এই শরীরহীন হওয়ার ভয় আমাদের মনের ও শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জড়িয়ে আছে। এখানে অদ্ভুত তত্ত্ব সামনে আসে যা শরীর-মনকে পৃথক করে বুঝতে সহযোগিতা করে যেখানে মৃত্যু কেবলই শরীর বিষয়ক। আর মন হল সেই চিন্তার আধার, যা মৃত্যুর পরেও থেকে যায়, যা অবিনশ্বর। এই মৃত্যু ও শরীরের কথা আমরা গিল্গামেশের কথাতেও পাই : ‘O Uta-napishti, what should I do and where should I go?/ A thief has taken hold of my [flesh!]/ For there in my bed-chamber Death does abide,/ and wherever [ I ] turn, there too will be Death.’[৭] ভয় বারবার ঘুরে ফিরে আসে!! আরেকটি প্রসঙ্গ আমাদের এড়িয়ে গেলে চলবে না যে, মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মৃত্যু জড়িয়ে আছে। সেই কারণেই হয়তো পৃথিবীর এক অতি পুরোনো মহাকাব্যের কাহিনি মৃত্যুকে ঘিরে। আরও একটা প্রসঙ্গ না বললে হবে না, সেটি হল—যে সময় গিল্গামেশ্ রচনা করা হয়েছিল সেই সময়ে সম্ভবত মানুষের মানসিক উন্নতির পর্যায় ততটা ছিল না। তখন জীবনের প্রাথমিক বোধ ছাড়া তেমন কিছু ভাবার অবকাশ মানুষের ছিল না। এই মহাকাব্যেও যৌনতা, মৃত্যু, ক্ষুধা, বন্ধুত্ব— এ সব ছাড়া বিশেষ অন্য কোনো চারিত্রিক দিকে আলো ফ্যালা হয়নি।
হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে।।( কঠোপনিষদ্ ১।২।১৯ )৮
‘ন হন্যতে’— আমার মৃত্যু হল কিন্তু আমার শরীর থেকে গেল। এখানে মৃত্যু হল আমার আমি-র। অদ্ভুত এক তত্ত্বের সম্মুখীন হব আমরা যে, আমি যখন বেঁচে ছিলাম তখন আমার অস্তিত্বের প্রকাশ ছিল আমার চলায়, আমার বলায়। চলমানতা তবে প্রাণের প্রতীক কিন্তু একজন মানুষ Coma-তে তলিয়ে গেলেও তো স্তব্ধ হয়ে যান!! মৃত্যু কিন্তু আমাদের পৃথক করে দেয় শরীর থেকে। যে শরীর থাকাকালীন আমি আছি এই বোধ থাকলেও নিজেকে বহুভাবে সর্বতোরূপে স্পর্শ করা যায় না। আমি ‘আত্মার’ প্রসঙ্গে যাব না কিন্তু শরীরী বোধ আমাকে শরীর করে তোলে এবং সম্পূর্ণরূপে আরেক অনুভূতির জন্ম দেয় তা হল— আমি মন। এখানে উপনিষদের ভাষায়— ‘আমিই (সেই) আত্মা’। শরীরে থেকেও আমার শরীর আমার মনকে বুঝতে পারে না অর্থাৎ যে শরীর এই মন দ্বারা পরিচালিত সেই মনকেই আবার শরীর দিয়ে বোঝা। সাধনার পথ আমাদের সেদিকে নিয়ে যায় যেখানে শরীর দিয়ে আত্মতত্ত্ব-কে জানা। প্রথমে শরীরের জীবিতাবস্থায় শরিরবোধকে মারা, তবেই তো আত্ম-কে জানব আমি!! কিন্তু এ মৃত্যু সে মৃত্যু নয়। এখানে ‘ন হন্যতে’ তত্ত্বের নতুন দিক খুলে যাবে যদি আমরা দেখার চেষ্টা করি যে, এই মৃত্যু আমকে জন্মের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তবুও আমার হনন হচ্ছে না, আমার শরীরও অক্ষত থাকছে আমার মনও অক্ষত থাকছে। অস্তিত্বের বিনাশ তবে নতুন জন্মের দিকে। এখানে কোথাও মৃত্যু নেই তবুও মৃত্যু সমগ্রে মিশে আছে। আত্মবিরোধের মধ্যে দিয়ে মৃত্যুর দিকে যেতে যেতে না-মৃত্যুর মধ্যে মিশে যাওয়া। আমি যদি নিজেকে শরীর ভাবি তবে আমাকে হনন করা যাবে কিন্তু মন ভাবলে, আত্মা ভাবলে হনন করা যাবে না। এখানেই আবার আমি-কে আমার থেকে পৃথক করে দেখা। শরীরের ‘আমি’ আর আমার পৃথক ‘আমি’ দুটো আলাদা । আমার পৃথক ‘আমি’-র তাই মৃত্যু নেই। এখানেও দার্শনিক দ্বন্দ্ব।
সৃষ্ট এ শরীর যখন ধীরে ধীরে বিনষ্ট হচ্ছে এবং একদিন তার মৃত্যু হবে। যদিও দেহটা আমি রেখে গেলাম, এখানে আমি আর থাকলাম না দেহে। মুছে গেল আমার দেহবোধ। গন্ধ-স্পর্শের এ শরীরে গভীরভাবে সংযোগে আবদ্ধ আছে বহির্বিশ্ব। মন যুক্ত করেছে আমাকে আমার শরীরের সঙ্গে। আমি আছি তাই আমার আমি আছে। দেহের সঙ্গে মনের সংযোগ, বহির্বিশ্বের সঙ্গে আমার শরীরের যোগাযোগ আমার মনের যোগাযোগের ফসল। এর মাঝে জড়িয়ে আছে আমার সংবেদী মন এবং সংবেদনের ধারণা। এমন একটা সময়ে যখন আমি আর আমি থাকব না এবং থাকার কোনও অনুভূতিই খেলবে না শরীরে তখন ‘আমি’ না জানলেও অথবা জানতে না পারলেও ‘আমার সে মুহূর্তে মৃত্যু হয়ে যাবে’— এটাই সত্য। বেঁচে থাকাকালীন আমি কত চিন্তার জন্ম দিয়েছি ( মন ) এবং কত কিছুর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি শরীরের মাধ্যমে, এটাও সত্য। সেখানে সংবেদন প্রসঙ্গ এসে যায়। সার্ত্রে প্রদত্ত সংবেদন প্রসঙ্গে আমি যাব না তবে এটুকু বলতে পারি যে, আমাদের মন অনেকাংশেই তৈরি হয় বহির্জগতের অস্তিত্বের সঙ্গে প্রবল ঘর্ষণে। এই ‘আমি’ পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর আদি অবস্থায় থাকে, সংযোগহীন, কেবল তার মায়ের শরীর ও মনের সঙ্গে যোগ। পরবর্তীতে সে তার অস্তিত্ব নিয়ে গড়ে ওঠে। আমার মৃত্যুর পর আমার সংবেদন ছিন্ন হবে।
আমার শরীর মৃত্যুলাভ করবে কিন্তু আমার ‘আমি’-র কোনো বিনাশ নেই, সে থেকে যাবে আমার আত্মজনের মনে, আমার কর্মে, আমার সৃজনে। আমার সংবেদনের বহু অংশ এ পৃথিবীতে থেকে যাবে আমার আত্মজনের মনে। আমার আত্মজনের মৃত্যুর সঙ্গে আমার থাকার স্মৃতিটুকু ধীরে ধীরে মুছে যাবে। একটা সময় আমি তো ছিলামই না তারপর যখন একটি কোষ থেকে আমার বহুতে প্রকাশ হল তখন আমার জন্ম হল। আসলে এই দেহ যা কেবলই আমার বাবা এবং মায়ের দেহাংশের মিলিত সত্তা। ভাবতে বসলে মনে হয়, এই দেহে আমি কোথায়!! আমি নেই— আমার আমিত্বও নেই। বহু বিনাশের পর আমার মানুষ হয়ে ওঠা শরীরে। মাতৃগর্ভে আমি বহুবার মরেছি, দেহের বহু অংশের মৃত্যু হয়েছে তারপর জন্মক্রিয়ার প্রতিফলিত রূপ এই আমার দেহ (যদিও এই দেহ বহু পরে তৈরি হয়েছে, প্রথম যে-দেহ নিয়ে আমি জন্মেছিলাম সেটাই আমার প্রথম দেহ যা বহু মৃত্যুর ফসল)। আমার জন্মের পর আমার যে কান্না ঠিকরে বেরিয়ে এসেছিল আমার শরীর ও মন থেকে তা কেবলই আমার বহু মৃত্যুর বিষাদ।
আমি এখনও বিষাদে পীড়িত হয়ে আছি। রোজ রাতে আমি মরে গিয়ে আবার জন্মাই। সে এমন এক হয়ে ওঠার দুঃখ যা মনে মুখে কখনই বলে প্রকাশ করা যাবে না, কেবলই স্তরের পর স্তর খুলে দেখি বিষাদ। শরীর এবং মনের তীব্র সে যোগে আমি আমাকে খোঁজার চেষ্টা করি। গতকাল আমি মরে গিয়ে যখন এক নতুন আমি-র সৃজনে মগ্ন হই তখন সৃজনের আনন্দ আমাকে প্রফুল্ল করে রাখে, দুঃখ ভুলিয়ে রাখে। আমার সৃষ্টি আমিই করছি, আমার দেহ আমার দেহকেই বিনাশের পরে আবার সৃষ্টি করছে। আমার বহু শরীর ছিল। অর্থাৎ আমার অতীতেও মৃত্যু ছিল, জন্মও ছিল। আমার বহু অতীত আছে। তবুও তো আমার শরীরের অক্ষয় অংশের বিনাশ হয়নি, তার বিনাশ হয় না মৃত্যু হয় না—সে আছে, সে থেকে যাবে তার তিনকাল নিয়ে। আমার ‘আমি’ ( আমার ধর্ম ) থেকে যায়। এই মৃত্যুর ভেতর পরম এক আনান্দ যেমন আছে তেমনই আছে কুণ্ডলিনীর ভেতর থেকে জেগে ওঠার পরম ক্রিয়া। সাধকেরা দেহকে মেরে রাখে অর্থাৎ ষড় রিপুকে দমন করে রাখে যার সহযোগে কুণ্ডলিনীর পূর্ণ জাগরণের পরে তাঁদের জন্ম হবে নতুন শরীরবোধে। মন ও শরীরের এখানে নতুনভাবে জেগে ওঠা ‘উত্তিষ্ঠত জাগ্রত/ প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।‘( কঠোপনিষদ্ ১।৩।১৪)[৯]
জীবনানন্দ দাশ ‘মৃত্যুর আগে’ কবিতায় বলেছেন : ‘যে-মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে/ চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ—কোনো সাধ নাই ফসলের তরে;’[১০] একটি শরীরের মৃত্যু হওয়ার আগের দৃশ্য মনে পড়ে গেল। দীর্ঘ জীবন যাপিত করার পরে একটি দেহ ফসলহীন হয়। যে মৃত্যু বারবার আসে এই দেহে তা অন্তিম বারে আমাকে দেহ শূন্য করে ছাড়ে। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন : ‘বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়/ নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি।/ তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-/ ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২।২২ )[১১] এখানে আমার সেই শূন্য দেহের কথা মনে হয়, আত্মায় বিশ্বাসী না হয়েও মনে হয় সে আছে। এখানে থাকার এক আস্তিক্য বোধে জারিত হই আমি। একটা সময় সে জীর্ণ দেহ ছেড়ে চলে যায় নতুন দেহে জন্ম নেবার জন্য। বিশাল একটি জনমানবহীন বাড়ির দৃশ্য মাথার মধ্যে ঘোরাফেরা করতে থাকে। আর জীর্ণ দেহ এবং জীর্ণ বস্ত্রের প্রসঙ্গে মাথায় আসে স্পর্শের অনুভূতি। এক বৃদ্ধের দেহ স্পর্শ করার অনুভূতি আমাকে স্তম্ভিত করে। যার ত্বক একটি বস্ত্রের মতো। আমি ঘুরতে থাকি সেই চিন্তার মধ্যে, সেই স্পর্শের দার্শনিক বলয়ে। রোজ এই আমাদের জন্মান্তরের পর বিষণ্ণতার জন্ম হয়। ‘নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার-বার তিরটিরে মাখে,’[১২] নদীর সঙ্গে তার তীরের মেখে যাওয়া হল গিয়ে মৃত্যুর প্রতীক। ‘আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর? জানিনা কি আহা,/ সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মত এসে জাগে/ ধূসর মৃত্যুর মুখ;—একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিল— সোনা ছিল যাহা/ নিরুত্তর শান্তি পায়;— যেন কোন্ মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে।/ কি বুঝিতে চাই আর?…রৌদ্র নিভে গেলে পাখি-পাখালীর ডাক/ শুনিনি কি? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে কাক!’[১৩] রক্তমাংসের মৃত্যু এবং সমস্ত চেতনার মৃত্যু জড়িয়ে আছে এই মৃত্যু নামক ঘটনার সঙ্গে। আমার সব কিছু থেমে যাবে মৃত্যুর পর। নিজেকে যদি ভাঙা আয়নায় দেখি, তাহলে দেখতে পাব মৃত্যুর চরম ক্রিয়াশীলতা। আয়নার প্রত্যেক ভাঙা অংশে নিজেকেই ছোটো ছোটোভাবে পাওয়া, এও হল গিয়ে মৃত্যুর দিকে যাওয়া। অস্তিত্ব থেকে অসীম অনস্তিত্বে । ‘আমি’ তারপর বহু অসংখ্য টুকরোয় ভেঙে যাব।
তথ্যসূত্র :
১) অভীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘জড় মন চেতনা— মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে’, নীললোহিত, সম্পা. বাসব দাশগুপ্ত, ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, জুলাই –ডিসেম্বর ২০০৬ ও ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি–জুন ২০০৭, কলকাতা, পৃ.১৪।
২) তদেব।
৩) তদেব।
৪) সুকুমারী ভট্টাচার্য, ‘প্রবন্ধসংগ্রহ ৪‘, ২০১৪, কলকাতা : গাঙচিল, পৃ.৩৪৪।
৫) Andrew George (Translator), ‘The Epic Of Gilgamesh‘, 2003, England : Penguin Books, pp.21.
৬) সুকুমারী ভট্টাচার্য, ‘প্রবন্ধসংগ্রহ ৪‘, ২০১৪, কলকাতা : গাঙচিল, পৃ.৩৪৪-৩৪৫।
৭) Andrew George (Translator), ‘The Epic Of Gilgamesh‘, 2003, England : Penguin Books, pp.97.
৮) স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পা., ’উপনিষদ গ্রন্থাবলী প্রথম ভাগ‘, ২০০৯, কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, পৃ.৮০।
৯) তদেব, পৃ. ৯২।
১০) জীবনানন্দ দাশ, ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি‘ ২০১৫, কলকাতা : সিগনেট প্রেস, পৃ. ৮৭।
১১) স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূ. এবং স্বামী জগদানন্দ সম্পা., ‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা‘, ২০১৬, কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, পৃ.৪৭।
১২) জীবনানন্দ দাশ, ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি‘, ২০১৫, কলকাতা : সিগনেট প্রেস, পৃ.৮৭।
১৩) তদেব, পৃ.৮৮।




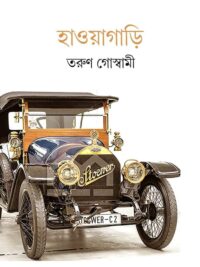





Facebook Comments