হাসান রোবায়েতের গদ্য
ধরমপুর
 অনন্ত শূন্যতার ভেতর যেতে যেতে একদিন হঠাৎ করেই শিশুরা দেখতে পায়— পৃথিবীর ঘাসের উপর ছোটো ছোটো ফুল। মাটিতে রোদের গন্ধ। নক্ষত্রের থেকে যে-আভা হাজার হাজার ছায়াপথ পার হয়ে লেগে আছে পেয়ারা-পাতায়, কুণ্ডুলি পাকিয়ে ধাতব খেলনার গায়ে আছড়ে পড়ছে রাতে, একটা কি দুইটা দাঁতে সে তারার আলোও কামড়ে ধরে শিশুরা। সে তখন ধীরে ধীরে টের পায় মায়ের অশ্রুত ঘ্রাণ। হামাগুড়ি অথবা প্রথম পায়ে হাঁটার দিনগুলি মনে না পড়ার মধ্য দিয়েই কোথায় যেন হারাতে থাকে। এর আগে সেও শূন্যের শিশু। যেন এক মহাস্তব্ধতার ঢেউয়ে সাঁতরে সাঁতরে এই রূপনারাণের কূলে জেগে ওঠা তার। আলোমে-আরওয়ার দিনশেষে মাটি ও কাদার দুনিয়ায় চারদিকে নানান পাখির ছায়া, পাতায় লিখিত খেলাঘর। মা’র স্তনে মুখ লাগিয়ে মাঝে মধ্যে বিস্ময়ে তাকানোর চোখ। শুয়ে শুয়ে হলুদ পাখির ডাকটিকে খুঁজে আবার ক্লান্ত হয়ে নিঝঝুম ঘুমের মধ্যে সেইসব পাখি ওড়া হাওয়াও যখন শিশুটির স্বপ্নে ডেকে যায়— সে হয়তো ভাবে, মা হারিয়ে গেছে কোথাও দোলনায় আলোর দোল দিয়ে। ফুঁপিয়ে কান্নার সহসায় নিথর করে তোলে বন।
অনন্ত শূন্যতার ভেতর যেতে যেতে একদিন হঠাৎ করেই শিশুরা দেখতে পায়— পৃথিবীর ঘাসের উপর ছোটো ছোটো ফুল। মাটিতে রোদের গন্ধ। নক্ষত্রের থেকে যে-আভা হাজার হাজার ছায়াপথ পার হয়ে লেগে আছে পেয়ারা-পাতায়, কুণ্ডুলি পাকিয়ে ধাতব খেলনার গায়ে আছড়ে পড়ছে রাতে, একটা কি দুইটা দাঁতে সে তারার আলোও কামড়ে ধরে শিশুরা। সে তখন ধীরে ধীরে টের পায় মায়ের অশ্রুত ঘ্রাণ। হামাগুড়ি অথবা প্রথম পায়ে হাঁটার দিনগুলি মনে না পড়ার মধ্য দিয়েই কোথায় যেন হারাতে থাকে। এর আগে সেও শূন্যের শিশু। যেন এক মহাস্তব্ধতার ঢেউয়ে সাঁতরে সাঁতরে এই রূপনারাণের কূলে জেগে ওঠা তার। আলোমে-আরওয়ার দিনশেষে মাটি ও কাদার দুনিয়ায় চারদিকে নানান পাখির ছায়া, পাতায় লিখিত খেলাঘর। মা’র স্তনে মুখ লাগিয়ে মাঝে মধ্যে বিস্ময়ে তাকানোর চোখ। শুয়ে শুয়ে হলুদ পাখির ডাকটিকে খুঁজে আবার ক্লান্ত হয়ে নিঝঝুম ঘুমের মধ্যে সেইসব পাখি ওড়া হাওয়াও যখন শিশুটির স্বপ্নে ডেকে যায়— সে হয়তো ভাবে, মা হারিয়ে গেছে কোথাও দোলনায় আলোর দোল দিয়ে। ফুঁপিয়ে কান্নার সহসায় নিথর করে তোলে বন।
এইসব মনে পড়া ও না পড়ার দিনগুলিতেই মা’র কাঁধে ঘুমিয়ে চলে আসি ধরমপুরে। ভাই আমি আব্বু আর মা। আমার বোনটা তখনও আলোছায়ার সন্ধিতে ভেসে ভেসে আমাদের বাড়ি আসেনি। আল্লার ফুল হয়ে ফুটে ওঠেনি নিখিল হাওয়ায়।
মানুষের স্মৃতি ঠিক কখন থেকে শুরু হয়? কখন সে বুঝতে পারে এই তার সারা জীবনের পথ। হঠাৎ কোনো কোনো সন্ধ্যায়, আমর্ম দুপুরে এই রাস্তায় হাঁটতে আসবে সে, বসবে তার ছায়ার। অস্তগোধূলির দিকে তাকিয়ে দেখতে পাবে অপরাহ্ণের সব পাতা এক এক করে পঁচে যাচ্ছে পুকুরের তলায়। তারপর কুটো হয়ে মাছেদের খাদ্য হয়ে আবার ফিরে আসছে কাদায়। সে-কাদায় পা রেখে আচমকাই কেউ হয়তো অনুভব করবে তার সারা শরীর আটকে যাচ্ছে শ্যাওলায়। আমিও জানি না কবে থেকে এইসব কুহকের দেখা পেতে শুরু করি। আজ অনেক অনেক দিন পর আমার জানালার থেকে যখন ভেসে আসছে ফেরিঅলাদের কণ্ঠ। যখন একটা রিক্সার বেল টুংটুং করে সতর্ক করছে কাউকে। মনে পড়ছে, একদিন আমিও এমন ঘন্টার পেছনে দৌড়ে গেছি শত শত পা। কেউ একজন কাঁধে আইস্ক্রিমের বাক্স নিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে ধানক্ষেত, কাঁচা আইলের ঘাস, চকচকে বিশ্বরোড। আমি খুব ডাকছি তাকে মুঠোয় আট আনা নিয়ে। আমার হাতের পয়সা তখন দাউদের ধাতব হয়ে গলে গলে চুয়ে পড়ছে মাটিতে। তবুও শুনছে না সে। এক অসীম দিগন্তের রং তাকে নিয়ে যাচ্ছে আমার সমস্ত বিস্মৃতির ওই পারে।
শুয়ে শুয়ে হলুদ পাখির ডাকটিকে খুঁজে আবার ক্লান্ত হয়ে নিঝঝুম ঘুমের মধ্যে সেইসব পাখি ওড়া হাওয়াও যখন শিশুটির স্বপ্নে ডেকে যায়— সে হয়তো ভাবে, মা হারিয়ে গেছে কোথাও দোলনায় আলোর দোল দিয়ে।
*
ধরমপুর। হালকা গ্রাম। মফস্সলিপনাই বেশি তার। ভূতের জিহ্বার মতো খসখসে একটা বিশ্বরোড এক পাশ দিয়ে কোথায় যেন চলে গেছে। ছোটো ছোটো পিচের রাস্তা, ইটের আধোপথ পেঁচিয়ে আছে ধরমপুরের শরীর। এলোমেলো বাড়িঘরগুলো কেবলই মনে করিয়ে দেবে এখানে ভাগিদাদিদের মধ্যে প্রায় সময়েই উথলে ওঠে কলহ। প্রায়ই মাটির দেওয়ালের বাড়ি। খুব অল্পই ইটের। ভূশাস্ত্র মতে এখানকার মাটি জাতে এঁটেল। লোহার জঙের মতো লাল। কাফেরের অন্তরের মতো ভীষণ। গ্রীষ্মে মাঠ ফেটে চৌচির। তখন মনে হবে, সীতার পাতালপ্রবেশ যেন এই মাটিতেই ঘটেছিল। ভাঙা ভাঙা দেয়ালের সীমানা। পলেস্তরা ঝরে পড়েছে কবেই। ইটের ক্ষয়ে যাওয়া ধুলা লেগে আছে তাতে। আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা’র দল এমন দেয়াল থেকেই জোগাড় করে তাদের হলদির গুঁড়া। পুবের দিকেই বেশি ধরমপুর। এক চিলিতে সুবিল সেই কবেই করতোয়ার থেকে একা হয়ে বয়ে যাচ্ছে। এখানে বউঝিয়েরা বড়ো কাঠের তক্তা নিয়ে কাপড় কাঁচতে আসে। পুরুষেরা ডুব দিয়ে কাজে চলে যায়। এই নদী সবচেয়ে আনন্দের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের কাছে। এপার থেকে ওপারের দূরত্ব একটি গানের। গামছায় মাছ ধরে। মুঠ মুঠ বালু নিয়ে গোসল করে ওঠা সঙ্গীর দিকে ছুড়ে দেয়। গরুর লেজ ধরে সাঁতরে বেড়ায়। উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গেছে সুবিল। নদীগবেষকেরা হয়তো সুবিলকে বলবে খাল। কিন্তু এখানকার মানুষেরা সে রায় মেনে নেবে না কিছুতেই।পুবের দিকেই ধরমপুর বেশি। সুবিলের পাড় ঘেঁষেই গড়। কী উঁচু! মোনামুনির গাছ। প্রাচীন সাপেদের ভিঁটা। নানান প্রকারের ঝাউ। গোলগোল মধুতে ফুলে থাকা আটাশরির জঙ্গল। অজস্র অ্যাকাশিয়ার বৃক্ষ। প্যাঁচানো হলুদ ফুল। দুই গড়ের মধ্য দিয়ে সরু খাল। চুলবুল করে পানি আসছে কোথাও থেকে যেন। দাড়কে মাছের ঝাঁক সেখানে হইহল্লা করে মেতে রাখছে পানি। পাশেই ঈদ গা। এক কোমর প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ভেতরে কার একটা কবর। নাম মুছে গেছে। সময়ের সাথে সাথে সাল তারিখও বৃষ্টিতে ভেসে ভেসে চিকন নালা কেটে গড়িয়ে গেছে সুবিলের দিকে। উত্তরে তালগাছ। বাঁশঝাড়ে অনেক অনেক গোর। এখানে গরু আলগা করে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেয় অনেকেই। কখনও ঘুমিয়েও পড়ে। গরুগুলো সারা টিলায় ঘাস খায়। তারপর শুধু ধানক্ষেত। পিচের রাস্তা। দুই একটা ট্রাকের ঘরঘর আওয়াজ।
বড়ো কুমড়া ছোটো কুমড়ার দিকে যে-রাস্তাটা চলে গেছে সেখানে ছোট্ট একটা মোড়। দুই একটা ছোটো দোকান। টিন দিয়ে বানানো। বসার টং থাকে। বাস থামে এখানে। তারপর সোজা পূর্ব দিকে মাটির সরু রাস্তা। বামে পাকা করা লম্বা একটা বাড়ি। উপরে টিনের চাল। খুব কৌতূহল ছিল আমার বাড়িটাকে ঘিরে। কিন্তু কোনোদিনই ঢুকতে পারিনি। তারপরেই ঘন জঙ্গলে ঠাঁসা একটা আড়া। আমরা বলতাম খরগোস বন। কোনোদিন স্বপ্নে অথবা বাস্তবে এই জঙ্গলের ভেতর থেকে কানখাড়া করা একটা খরগোশ বেরিয়ে আসতে দেখেছিলাম। কী এক ফুলের লতার নীচে বসে ছিল সে। কচুর মতো গুল্ম। তরোয়ালের মতো লম্বা পাতা। সবুজ। গর্ভ চিরে শাদা ঝির ঝির ফুল সাপের মতো দুলছিল। ঐ ঝোপেই বসে ছিল সে। আমরা এগুতেই কোথাও হাওয়া হয়ে গেল। তারপর থেকেই ওটা খরগোশ বন। অন্যরা হয়তো আলাদা নামে ডাকতো। বনের পরেই উঁচু গড়। সুবিলের মতো অতটা উঁচু নয়। সামনে একলা একটা আকাশমনি গাছ। আরেকটু পুবে এগিয়ে ডাইনে একটা পরিত্যক্ত জমি। কেল্লে ঘাসের মাঠ, কলমির বেড়া দিয়ে ঘেরা। তারপরেই আমাদের বাড়ি। তখনও অবশ্য মইনুল ভাইদের বাড়ি। আমরা ভাড়ায় থাকি। চারটা ঘর। দুইটা পুবদুয়ারি একটা দক্ষিণ। মেইন গেটটা পুব দিকে। সাথে রাস্তা। একটা পেয়ারার গাছ। রান্নার ছাপড়া। তার দক্ষিণে গোসলখানা। আমরা থাকতাম পুবদুয়ারি একটা ঘরে। দখিনদুয়ারি ঘরটাতে মইনুল ভায়ের মা। আমাদের ঘর আর দখিনদুয়ারি ঘরের মধ্যেখানের ঘরে থাকতো মইনুল ভাই। ওই ঘরে দুইটা চৌকি। একটাতে আমি আর ভাই। আরেকটাতে মইনুল। চাচাও থাকতো আমাদের সাথেই। বাড়িটা মাটির। কোঠাঘরঅলা। বাড়ির উত্তর দিকে কাসেম মাস্টারের আমবাগান।
*
লম্বা বারান্দায় শপ বিছিয়ে মা পড়াতে বসাতো। এ বাড়ির বারান্দাতেই আমার প্রথম পড়তে বসা। আমার প্রথম পড়া ‘আদর্শ লিপি’-র পাতা। প্রচ্ছদে দুইটা শাপলা ফুটে আছে। একটা শাপলার কলি। তিনটা পাতা। কালির ঢেউ ঢেউ চিহ্ন দেখলেই আমার কেমন সত্যিকারের শাপলা দেখতে ইচ্ছা করতো। একদিন মাকে বললাম— ও মা, হামাক শাপলা ফুল দেখাবেন? মা বললো— শাপলা ফুল এটি কুনটি পামু! মাধুডাঙা বিলোত ম্যালা শাপলা ফুল হয়। তোর নানীর বাড়িত গেলে দেখিস। আমার কেবল মনে হচ্ছিল, কাজ রেখে নিয়ে যাওয়ার ভয়ে মা মিথ্যা বলছে। কাসেম মাস্টারের আমবাগানের ভেতর দিয়ে পুব দিকে গেলেই তো পুকুর। ওখানে নিশ্চয়ই শাপলা আছে। তখনও ওই পুকুরে যাইনি আমি। বাড়ির আশেপাশেই আমার যাতায়াত। পেছনের গড় আর আকাশমণিই আমার সীমানা। আর জিগার গাছের নীচে যে-দোকান মাঝে মাঝে সদাইপাতি আনতে যাই ওখানে। সন্ধ্যার আগে আগে কেরোসিন তেল। নুন মশলা লবণ। বাড়ির দক্ষিণ দিকে ছিল একটা পুকুর। গড়ের নীচে লম্বা আয়তাকার মাঠ। বিকালে গাদল-গাদল খেলা হতো সেখানে। এরপরেই একটা পুকুর। পুকুরের পশ্চিম পাশে হালকা বাঁশের আড়া, একটা পুরোনো বট।
প্রত্যেক শিশুর কল্পনাতেই কিছু মাঠ এমন থাকে যে প্রান্তরে তার রাজপুত্র আর কোটালের ছেলেকে দেখতে পায় ঘোড়া নিয়ে চলে যেতে। এমন দিঘি থাকে যার গভীরে পৃথিবীর সমস্ত রাজকন্যা রাক্ষসের হাতে কয়েদ। আর সেই প্রাণভোমরাটিকেও শিশুরা দেখতে পায় তারই পরিচিত জগতে। এভাবেই নানান স্থান তার মগজে গেঁথে থাকে। গড়ের নীচের ওই বট আর দিঘিটি ছিল তেমন। মনে হতো, মা আর নানীর কিস্তায় শোনা প্রত্যেকটা ভূত ওই বটগাছেই থাকে। দিনে কোথায় যেন চলে যায় সন্ধ্যা হলেই গোধূলির লালরং মুখ নিয়ে ফিরে আসে আবার। তখন সরসর করে পাতা কাঁপে, পাখিরা ভয়ার্ত ডেকে ওঠে সহসাই। পাশের ওই দিঘির ছিল ধ্যানের মতো পানি। ভাবতাম, এখানেই বন্দী আছে আজানা রাজ্যের সেই রাজকন্যাটি। বড়ো হলে যখন আমার নিঃশ্বাস দীর্ঘ হবে যখন সাঁতার শিখে যেতে পারব এপার থেকে ওইপারে এক ডুবে দেখে আসব গরুর চোখের মতো সেই মায়াবিনীর মুখ।
পুকুর ঘিরে অনেক খেঁজুর গাছ। আমার চেয়ে বড়োরা সে-সব গাছে উঠতো। খেঁজুর পাড়তো। কাঁচা খেঁজুড়ে কামড় বসালেই গড়িয়ে পড়তো কষ। নরম শাঁস। খুব ভালো লাগতো। খুব সকালে গাছের নীচে ছড়িয়ে থাকতো খেঁজুর। দৌড়ে চলে যেতাম ছোটো ছোটো খেঁজুরের লোভে। আঁটি শক্ত হলে লবণ দিয়ে মাখিয়ে বয়ামে রেখে দিতাম। কয়েক দিন পরেই কেমন লাল হয়ে যেতো। পাকা খেঁজুরের স্বাদ সারাদিন মুখে লেগে থাকতো।
একটা হেলানো খেঁজুর গাছ ছিল। পানির সমান্তরালে গিয়ে হঠাত উপর দিকে চলে গেছে। সুযোগ পেলেই ওই গাছের উপর বসে থাকতাম। হাঁসেরা শামুক গুগলির জন্য অনবরত ডুবছে। একদিকে সাঁতার কাটছে মানুষেরা। কোন ক্লাসের বইয়ে ভুলে গেছি। একটা গল্প ছিল এমন— পুকুরের উপর একটা গাছ। সেখানে মা আর বাচ্চা পাখিটা থাকে। মা সারাদিন খাবারের জন্য কোথায় কোথায় যেন চলে যায়। বাচ্চাটার ভালো লাগে না একা একা। সে তার খড়কুটোর বাসা থেকে ঘাড় উঁচু করে চারিদিক তাকিয়ে থাকে। একদিন দেখতে পায় নীচে পানি। সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে নানান রঙের মাছ। পাখির বাচ্চাটা ভাবে, কী সুখ ওদের! সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। আর এই ছোট্ট বাসার মধ্যে শুয়ে-বসে ক্লান্ত সে। তার মনে হতে থাকে, যদি লাফ দিয়ে ওই পানিতে চলে যাই অনেক মজা হবে।যেই ভাবা সেই কাজ। ঝুপ করে লাফ দিল পানিতে। আর যাবে কই! বোয়াল, টোংরা (টেংরা মাছকে টোংরা পড়তাম তখন। জোরে জোরে পড়তাম। চাচা একদিন ঠাস করে থাপ্পর মেরে উচ্চারণ ঠিক করে দেয়। এর আগেও কয়েক বার ঠিক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু টোংরাই পড়তাম সব সময়। তাই ওই চড়) শিং; সব কাঁটাঅলা মাছ ঘিরে ধরলো তাকে। সে কী ভয়! কাঁদতে লাগলো বাচ্চাটা। এসব দেখে একটা হাঁস উদ্ধার করলো তাকে। গল্পটা মনে পড়লেই আমি দেখতে পেতাম শোওয়ানো খেঁজুর গাছের মাথায় সেই বাচ্চাটির ঘর। নীচে অজস্র কাঁটাঅলা মাছ। আর বোনের অশ্রুর মতো গোটা গোটা জল।
এই পুকুরেও শাপলা ছিল না। ছিল শাপলা দেখার স্বপ্ন।
প্রত্যেক শিশুর কল্পনাতেই কিছু মাঠ এমন থাকে যে প্রান্তরে তার রাজপুত্র আর কোটালের ছেলেকে দেখতে পায় ঘোড়া নিয়ে চলে যেতে। এমন দিঘি থাকে যার গভীরে পৃথিবীর সমস্ত রাজকন্যা রাক্ষসের হাতে কয়েদ। আর সেই প্রাণভোমরাটিকেও শিশুরা দেখতে পায় তারই পরিচিত জগতে।
এক জন বৃদ্ধ ভিখারি আসতেন ধরমপুরে। লাঠি নিয়ে টুকটুক করে হাঁটতেন। আমার চেনা রাস্তার বাইরে সেইসব অচিন পথে যে ঘুরে বেড়ায় তাকেই আমার হিংসা হতো খুব। মার কাছে শুনতাম যমুনার চরে আমাদের জমি আছে। সেখানে মশুর-বাদাম-খেরাচি-কুশার [আখ] আরও কত কিছু চাষ হয়। কেউ কেউ গভীর রাতে খেরাচি আর মশুরের ক্ষেতে গরু ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে। গরুরা এক জমি থেকে অন্য জমিতে মটরের লতা আর ঘাসের বনে চড়তে থাকে। চাঁদের আলো পড়ে যমুনায়। মাছেরা অতল পানির থেকে চলে আসে কিনারায়। বাতাসে পানির দল ভেঙে চিরল চিরল ঢেউ ধাক্কা খায় বালিতে। যেন অল্প পরেই মটর ফুলের উপর রাত্রির বিন্দু বিন্দু স্বেদ আরও গোল হয়ে উড়ে যাবে মহাস্তব্ধতায়। কামলার হুর র র র হুর র র করে ডাকতে থাকবে গরুদের। এসব মনে হলেই ঈর্ষায় মরে যেতাম। আমার শুধু ঘর আর বই। ভালো লাগতো না।
ফকির আসার বারটির জন্য অপেক্ষা করতাম আমি। কখনও মক্তবের রাস্তা দিয়ে কখনও খরগোশবনের পাশ দিয়ে আসতেন তিনি। আমাদের দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চ স্বরে ওয়াজের মতো কী সব বলেই ‘মা গো… বিসমিল্লাহ আল্লাহ… মা দুইডা ভিক্ষে দ্যান গো… বলে উঠতেন তিনি। আমি ছেনিতে কয়েক মুঠ চাল নিয়ে ভো দৌড় দিতাম। তখন আমার নাভী বেশ ফুলা ছিল। ছোটোবেলায় নাকি খুব চিৎকার করে কাঁদতাম তাই অমন। উনি আমার নাভীতে লাঠি দিয়ে আলতো খোঁচা মারতেন। আর বলতেন ফকিরের লাঠির খোঁচায় নাকি ভালো হয়ে যাবে নাভি। আমি শরম পেতাম। এক এক দিন কাসেম মাস্টারের বাগানে আমগাছের নীচে বসে আমার সাথে গল্প করতেন তিনি। একদিন উনাকে বললাম, ‘আচ্ছা, আপনের বাড়ি কুনটি?’ নামটা ভুলে গেছি। হয়তো, বারোপুর নয়তো গোকুল কিংবা সুখানপুকুর ছিল সেই নাম। উনি বলতেন— ‘সেডে তো ম্যালা দূরের গাঁও বারে, তুমি চিনবে না’। আমি বলতম— ‘তাও কন। বড়ো হলে সেটি যামু হামি’। উনি সেই দূরের গ্রামের কথা বলতেন। তার বাড়ি ছিল কোনো এক নদীর ধারে। জমিও ছিল কিছু। দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন বহু আগে, এক ছেলেরও; যখন উনার শরীরে ছিল বাইম মাছের মতো জেদ। তারপর নদী ভাঙলে বারোপুর অথবা গোকুল অথবা অন্য কোনো নামের গ্রামটিতে চলে এলেন। সেও প্রায় বহু যুগ। এখন তার ছোট্ট একটা খড়ের ঘর আছে। ঘরে তার বউ। একটা মাটির ঠিলা। দড়িতে বাঁধা একটা মই আনুভূমিক ঝুলে আছে ঘরে। মাটির পাতিল থাকে সেখানে। টিনের প্লেট আর জগও আছে তার। খুব সকালে তার গ্রামের রাস্তা ধরে ময়না কাঁটার বন পেছনে ফেলে হাঁটতে শুরু করেন তিনি। মাঝে মাঝে খোওয়া ওঠা রাস্তা মাঝে মাঝে কাদামাটির পথ হেঁটে হেঁটে চলে যান ভিনগাঁওয়ে। জামের বসে জিরিয়ে নেন। আবার হাঁটতে হাঁটতে কত স্কুল কত মসজিদ পার হয়ে দুপুরের সূর্যপিণ্ড দেখতে পান। তার লাঠির ছায়া হেলে পড়লে বুঝে নেন সময়। কোনো মক্তবের চাপকল থেকে পানি খেয়ে আবার চলতে শুরু করেন। এভাবেই কারো দিঘিতে গোসল কারো বাড়িতে দুপুরের খাবার খেয়ে অনন্ত মুসাফিরের মতো হাঁটতে থাকেন তিনি। যেন এক ধ্রুপদী হিউয়েন সাঙ। যার বোচকার মধ্যে রাশি রাশি পথ খলবল করছে সারাক্ষণ।
কমলার কোয়ার মতো চকলেট দিতেন তিনি। তন্ময় হয়ে তার কথা শুনতাম। আর আমার চোখের সামনে দুলে উঠতো সেইসব পথ। যেন এমন পথের পাশেই কোনো দিঘিতে ফুটে আছে আমার শাপলা ফুল।
আবার ফেরার কথা বলে চলে যেতেন কোথাও ভিন্ন এক ধরমপুরের পথে।




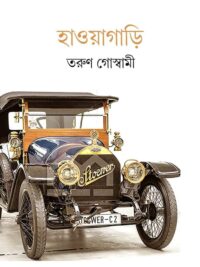





Facebook Comments