ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ
উনিশ শতকের কলকাতার বারাঙ্গনা কন্যারা ও তাদের আলোয় ফেরার কিছু কথা
নগরসভ্যতা আর পতিতাবৃত্তি প্রায় সমবয়সি। মধ্যযুগে নগরসভ্যতার অন্যতম ভূষণ ছিল বারাঙ্গনা পল্লি। বারাঙ্গনা সংসর্গ ছিল মধ্যযুগীয় পৌরুষ ও আভিজাত্যের প্রতীক। সে-সব অন্য প্রসঙ্গ। আমি বুঝতে চাইছি আঠেরো/ উনিশ শতকের কলকাতার বারাঙ্গনা সমস্যার উদ্ভব ও তাদের আলোয় ফেরার কথা।
আধুনিক শহরের সমস্ত কদর্যতাকে সঙ্গে নিয়ে নগর কলকাতার ক্রমবিকাশ হয়েছিল আর এদেশে বারাঙ্গনা বৃত্তির উদ্ভব বৃটিশ শাসনের হাত ধরেই। কলকাতার নগরায়ন শুরু হয় পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে। সংবাদপত্র দূরের কথা ছাপার যন্ত্রের কথাও তখন কল্পনায় ছিল না। শৈশবের কলকাতায় লোকসংখ্যাই বা কত! ১৭১০ সালে কলকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানুটি যে তিনটি গণ্ডগ্রাম নিয়ে কলকাতা নগরীর পত্তন হয়েছিল সাকুল্যে তার লোকসংখ্যা ছিল দশ হাজার। ১৭৪০-৫০ সময়কালে বাংলার গ্রামে গ্রামে মারাঠা বর্গী হামলার ফলে আতঙ্কিত বহু মানুষ নিরাপত্তার জন্য কলকাতায় বসবাস শুরু করল। ব্যবসা-বানিজ্যে ও নানা কারণে কলকাতার লোকসংখ্যা বাড়তে থাকল। কলকাতা তার গ্রামীণ রূপ থেকে শহরে পরিণত হল।
কলকাতায় বিচারালয় স্থাপনের পর কলকাতায় এটর্নি হয়ে এসেছিলেন উইলিয়াম হিকি। নভেম্বর ১৭৭৭ থেকে ১৮০৮ পর্যন্ত হিকি কলকাতায় ছিলেন। লন্ডনে ফেরার পর চার খণ্ডে তাঁর যে স্মৃতিকথা (১৭৪৯-১৮০৯) লিখেছিলেন সেটি শৈশবের কলকাতার সামাজিক ইতিহাসের প্রামান্য দলিল হিসাবে স্বীকৃত। স্মৃতিকথায় হিকি মিস ডানডাস নামে মহানগরের এক বহুজন পরিচিতা বারাঙ্গনা’র কথা উল্লেখ করেছেন। আধুনিক যুগে কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলে বারাঙ্গনা বৃত্তির সূচনা যে ইংরাজরা আসার পরেই হয়েছিল তাতে কোনো সংশয় নেই। হিকি যে সময়ের কথা বলেছেন, তখন নগর কলকাতার নিতান্তই শৈশবকাল। কলকাতার নগরায়ন সবে ক্ষীণ গতিতে শুরু হয়েছে। কোম্পানীর কাজ-কর্ম চালানোর জন্য ইংরাজ ভাগ্যান্বেষীরা তাদের নতুন উপনিবেশে আসতে শুরু করেছে। কলকাতার সেই শৈশবে ভাগ্যান্বেষণে যে- সব ইংরাজরা এসেছিল, তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ‘অস্তগামী মধ্যযুগের উচ্ছিষ্টতুল্য প্রতিনিধি’। অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, উচ্ছৃঙ্খল। তাদের দোসর হল ইংরাজ শাসনের প্রসাদলোভী বেনিয়ান, মুৎসুদ্দিরা। পালকি আর গোরুর গাড়ি যুগের সেই কলকাতায় দেশীয় খবরের কাগজ তো দূরস্থান ছাপার অক্ষরেরও উদ্ভাবন হয়নি। কিন্তু বারবণিতা বৃত্তির প্রসার হয়েছিল ভালোই। ১৭৯৫-এ রুশ যুবক লেবেদেফ যখন কলকাতায় অস্থায়ী মঞ্চ বেঁধে প্রথম বাংলা থিয়েটারের সূচনা করলেন, তখন সেই নাটকে নারী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য বারবণিতা পল্লির মেয়েদের নিয়োগ করেছিলেন। অর্থাৎ ১৭৯৫-এর অনেক আগে থেকেই বারাঙ্গনা পল্লির অস্তিত্ব ছিল। আর শুধু কলকাতা নয়, বাংলার সমৃদ্ধ শহরগুলি যেখানে ইংরাজরা কোর্ট-কাছারি, দপ্তর খুলেছিল সেখানেই সন্নিহিত অঞ্চলে বারাঙ্গনা পল্লি গড়ে উঠেছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর রামতনু লাহিড়ী ও ‘তৎকালীন বঙ্গসমাজ’ গ্রন্থে কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা) আত্মচরিত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে কৃষ্ণনগরের সমকালীন সামাজিক অবস্থার বর্ণন করেছেন। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র লিখেছেন— “…… পূর্বে কৃষ্ণনগরের কেবল আমিনবাজারে পতিতালয় ছিল, গোয়াড়ীতে গোপ, মালো প্রভৃতি জাতির বাস ছিল। পরে ইংরেজরা যখন এখানে বিচারালয় ইত্যাদি স্থাপন করেন, তখন গোয়াড়ীর পরিবর্তন হতে থাকে। কার্তিকেয়চন্দ্র আরও লিখেছেন, “…… বিদেশে পরিবার লইয়া যাইবার প্রথা অপ্রচলিত থাকাতে প্রায় সকল আমলা, উকিল মোক্তারের এক একটি উপপত্নী আবশ্যক হইত। সুতরাং তাহাদের বাসস্থানের সন্নিহিত স্থানে স্থানে গণিকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল”। এই কারণেই আমরা দেখি উত্তর কলকাতায় প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত লোকবসতি কেন্দ্রের আশেপাশেই প্রাচীন গণিকাপল্লীগুলির অবস্থান।
১৭৯৩-এ কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার গ্রাম-সমাজের কাঠামোটাই ভেঙ্গে দিল। সূর্যাস্ত আইনের প্যাঁচে বনেদি জমিদাররা নিঃস্ব হল, আর বেশি রাজস্ব দেবার অঙ্গীকারে নিলামে জমিদারি কিনে ভূমিসম্পর্কহীন এক অর্থলোলুপ মধ্যশ্রেণির উদ্ভব হল। দুর্নীতিগ্রস্ত, উচ্ছৃঙ্খল ইংরেজ আর শিকড়হীন নতুন মধ্যশ্রেণিটির পৃষ্ঠপোষকতায় জন্ম নিল এক কুৎসিৎ সংস্কৃতির-যাকে আমরা ‘বাবু কালচার’ বলে জেনেছি। গড়ে উঠেছিল ইংরাজের দালালি করা এক লোভী, দূর্নীতিপরায়ন, অলস নাগরিক সমাজ। আঠেরো শতকের কলকাতা ছিল এদেশীয় দালাল, মুৎসুদ্দি, বেনিয়াদের কলকাতা আর উনিশ শতকে ‘বাবু’ কলকাতা । আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’ গ্রন্থে কলকাতার সেই বাবুসমাজের বর্ণনা দিয়েছেন এইরকম— “ইহাদের বহিরাকৃতি কি কিছু বর্ণনা করিব? মুখে, ভ্রুপার্শে ও নেত্রকোণে নৈশ অত্যাচারের চিহ্ন স্বরূপ কালিমারেখা । শিরে তরঙ্গায়িত বাবরি চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে কালোপেড়ে ধুতি। অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমরিকের বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনোট করা উড়ানী এবং পায়ে পুরু বাগলস সমন্বিত চিনাবাড়ির জুতা। এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীণা প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, আফ আখরাই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত এবং খড়দহের মেলা, মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতির সময় কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিগকে লইয়া দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিয়া থাকিত”। ইংরেজের শাসন-সহায়ক কদর্য বাবু সমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় বারাঙ্গনাপল্লিগুলো ফুলে ফেঁপে উঠল গোটা উনিশ শতক জুড়ে। রক্ষিতা পোষণ, বারাঙ্গনাগমন তখনকার সমাজ শুধু অনুমোদনই করত না, এইসব বেলেল্লাপনা ছিল তাদের মর্যাদার সূচক। ইংরাজের নতুন ভুমিব্যবস্থা গ্রাম্য সমাজকে ভেঙ্গে তছনছ করে দিল। ফলে বংশানুক্রমিক পেশা ও বৃত্তি থেকে উৎখাত হয়ে চোর ডাকাতের দল সৃষ্টি হয়ে শহরে আশ্রয় নিল, তেমনই দারিদ্র্যের তাড়নায় শহরের বারাঙ্গনা পল্লিতে আশ্রয় নিল মেয়েরা। ১৮৭২ সালের সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যায় যে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বারবনিতারা অধিকাংশই তাঁতি, তেলি, জেলে, কৈবর্ত, ময়রা, চামার, কামার, কুমোর, যুগী, গয়লা, নাপিত, মালি, বেদে ইত্যাদি (সূত্র: ‘অন্য কলকাতা’ / বিশ্বনাথ জোয়ারদার)। সেই সময়ে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বারবনিতাদের সংখ্যা কী রকম লাফে লাফে বেড়েছিল তা জানা যায় এই তথ্য থেকে। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১৮৬৭-এর ১৬ই সেপ্টেম্বরের হিসাব মতো তিন হাজার মেয়ে এই বৃত্তিতে নিযুক্ত। ১৮৮০ সালের এক হিসাবে শহরে বারবনিতার সংখ্যা ছিল সাত হাজার আর ১৮৯৩ সালে সেই সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছিল ২০,১১৬ । (তথ্যসূত্র: ‘অন্য কলকাতা’ / বিশ্বনাথ জোয়ারদার )।
‘বাবু কলকাতার’ সেই কদর্য বেলেল্লাপনার ছবি এখন আমরা কল্পনাতেও আনতে পারি না। শহরের যত্রতত্র গজিয়ে উঠেছে বারাঙ্গনা পল্লি। সম্ভ্রান্ত এলাকা বা বিদ্যালয়ের পাশেও। বিত্তশালী বাবুদের প্রশ্রয়েই এইসব বারাঙ্গনাপল্লি গজিয়ে উঠেছিল, তাই প্রশাসনের সাধ্য ছিল না এর বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার। এইসব ‘বাবু’দের আদর্শ ছিল ইংরাজ রাজকর্মচারীরা। শ্রীপান্থ তাঁর ‘কলকাতা’ গ্রন্থে ‘রোটি আউর বেটি’ রচনায় মন্তব্য করেছেন “সতীদাহ কলকাতায় তখন প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা। সারা ব্ল্যাক টাউন চিতার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, অন্ধকার। সেই অন্ধকারে চলছে বাবু বিলাস, গুরু-প্রসাদী কৌলিন্য রক্ষা। সতীর আর্তনাদে, বিধবার কান্না আর বারবনিতার কাতর আহ্বানে অষ্টাদশ শতকের কলকাতা প্রেতপুরী। পা যেন লজ্জায় জড়িয়ে আসে সেদিকে বাড়াতে”।
শুধু সমাজের নিম্নবর্গের মেয়েরাই নয় কুলীন ঘরের বহু মেয়েও অবস্থার দুর্বিপাকে আশ্রয় নিত বারাঙ্গনাপল্লিতে। সরকারী প্রতিবেদনে স্বীকার করা হয়েছিল যে বারাঙ্গনাদের সংখ্যা বৃদ্ধির একটা কারণ হিন্দু বিধবাদের বারাঙ্গনা পল্লীতে আশ্রয়। বিধবাবিবাহ প্রথা চালু না হওয়ায় লালসার শিকার বিধবা তরুণীদের শেষ আশ্রয় ছিল বারাঙ্গনা পল্লী। সরকারী প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল “হিন্দুর বিবাহ-বিচ্ছেদ নেই, বিধবা হলে হয় পবিত্র হও, নচেৎ বেশ্যা হও”। সরকারী প্রতিবেদন অনুযায়ী হিন্দু বিধবারা প্রধানত হুগলী, বর্ধমান, হাওড়া, চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা থেকে বারাঙ্গনা পল্লীতে আশ্রয় নিত। তরুণী বিধবারা বাবুদের লালসার শিকার হতেন, কেউ কেউ গর্ভবতী হয়ে পড়তেন। তাদের আশ্রয় হত বেশ্যালয়ে। দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি কারণেও মা, মেয়ে দুজনেই আশ্রয় নিত গণিকাপল্লীতে। মুহুর্তের ভুলে অন্তসত্বা নারী আত্মহত্যা না করে বাঁচার উপায় খুঁজেছেন বেশ্যালয়ে আশ্রয় নিয়ে আবার বহুবিবাহের শিকার নারী প্রেমিকের হাত ধরে কুলত্যাগিনী হয়েছেন, অবশেষে এসে জুটেছেন বারাঙ্গনাপল্লীতে। প্রয়াত গবেষক অধ্যাপক বিজিতকুমার দত্ত সরকারী দস্তাবেজ উদ্ধার করে লিখেছেন “সরকারী মহাফেজখানা থেকে যে রিপোর্ট পেয়েছি তা কৌতুহলোদ্দীপক। দেখা যায় দশ বছরের নিচে বেশ্যাদের বাড়িতে বেশ কিছু মেয়ে রয়েছে। সরকার এদের কথা মাঝে মাঝে ভেবেছে। কিন্তু তাদের সংখ্যা এত ব্যাপক যে সরকারের পক্ষে কিছু করে ওঠা কঠিন”। সেই হিসাব মতো, গণিকাপল্লীতে বারাঙ্গনা গর্ভজাত কন্যাসন্তানের সংখ্যা ছিল ৪০৮ জন। এইসব বারাঙ্গনা কন্যাদের পুনর্বাসন বা সমাজের মূলস্রোতে নিয়ে আসার ব্যাপারে তখনকার সরকার যেমন কিছু করতে পারেনি, তেমনই সমাজ সংস্কারকদেরও কোন হেলদোল ছিল এমন তথ্যও জানা যায় না। তারা নিজেরাই মুক্তির পথ, আলোয় ফেরার বেছে নিলেন। এবং এই মুক্তির পথ প্রথম দেখাল থিয়েটার, আর বারাঙ্গনা কন্যাদের থিয়েটারে নিযুক্তির পথ খুলে দিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
তার আগে, লেবেডফের উদ্যোগে বাঙালির প্রথম নাট্যাভিনয়ের ৪০ বছর পরে ১৮৩৫-এর ৬ই অক্টোবর শ্যামবাজারে বাবু নবীনচন্দ্র বসুর উদ্যোগে বাঙালির দ্বিতীয় নাট্যানুষ্ঠানে নবীনচন্দ্র বারাঙ্গনা পল্লী থেকে চারজন অভিনেত্রী নিয়োগ করার সাহস দেখিয়েছিলেন। ১৮৩৫ অর্থাৎ দু-বছর ডিরোজিওর নেতৃত্বে ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে (১৮৩৩-৪৬), ১৮২৮এ সতীদাহ প্রথা রদ হয়েছে। এই আবহে বারাঙ্গনা কন্যাদের আলোয় ফেরার প্রশ্নে বাবু নবীনচন্দ্রের সেদিনের ভূমিকা ঐতিহাসিক গুরুত্ব দাবি করে। ‘হিন্দু পাইওনিয়ার’ বারাঙ্গনা কন্যাদের অভিনয়ের প্রশংসা করে লিখেছিল “দেশব্যাপি অজ্ঞানের মধ্যে এরূপ অপ্রত্যাশিত একটি ব্যাপার ঘটিতে পারিয়াছে, তাগাতে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। …আমাদের সমাজের স্ত্রীলোকদের মানসিক শক্তির এই মহান ও নূতন দৃষ্টান্ত দেখিয়াও যদি লোকে স্ত্রীশিক্ষার অবহেলা প্রদর্শন করেন, তবে তাহাদের হৃদয় কঠিন ও চিত্ত আবেগহীন বলিতে হইবে… এই সকল প্রশংসনীয় কিন্তু ভ্রমে পতিত স্ত্রীলোকদের চারিত্রিক উন্নতি করিবার এই প্রচেষ্টার জন্য নাট্যশালার স্বত্বাধিকারী বাবু নবীনচন্দ্র ধন্যবাদের পাত্র”। কিন্তু সমাজের রক্ষনশীল অংশ তথা সমাজপতিরা রে রে করে উঠলেন। রক্ষনশীলদের প্রবল চাপে নবীনচন্দ্রের থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেল আর সেইসঙ্গে রুদ্ধ হয়ে গেল বারাঙ্গনা কন্যাদের আলোয় ফেরার উজ্বল পথটির, পরবর্তী প্রায় ৪০ বছরের জন্য। অথচ, সমকালীন সময়েই কলকাতায় বারাঙ্গনা গমন এক কদর্য চেহারা নিয়েছিল। ১৮৪৫-এ ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকা লিখেছিল ‘বেশ্যাগমন পাপ এইক্ষণে কলিকাতা মধ্যে যে কি প্রকার বিস্তারিত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা যায় না। ধনি, মধ্যবর্তী*, অতিদীন পর্যন্ত দুষ্কর্মে এমত সাধারণ রূপে মগ্ন হইয়াছে যে অন্য অন্য কর্মের ন্যায় ইহাকে পরস্পরকাহারও নিকট কেহ বিশেষ গোপন করে না— আপনার এই পাপ স্বীয় মুখে ব্যক্ত করিতেও কেহ লজ্জা বোধ করে না”। (‘বঙ্গীয় নাট্য সংস্কৃতিতে নারী’/ নৃপেন্দ্র সাহা— বাংলা একাডেমি পত্রিকা জুলাই ১৯৯৫)। বাবু নবীনচন্দ্রের থিয়েটারের ৩৮ বছর পর বারাঙ্গনা কন্যাদের আলোয় ফেরার দরজা আর একবার এবং চিরতরে উন্মুক্ত হয়ে গেল ১৮৭৩-এ।
১৮৭২-এ বাঙালির প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় ‘ন্যাশনাল থিয়েটার’ প্রতিষ্ঠার পরের বছর ধনকুবের আশুতোষ দেব বা ছাতু বাবুর দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ ‘বেঙ্গল থিয়েটার’ নামে একটি রঙ্গালয় খুললেন আর তাদের জন্য নাটক লিখে দেবার জন্য মাইকেল মধুসূদন দত্তকে অনুরোধ করলেন। মাইকেল সম্মত হলেন একটি শর্তে যে তাঁর নাটকের নারী চরিত্রগুলি মেয়েদের দিয়েই অভিনয় করাতে হবে। বেঙ্গল থিয়েটারের উপদেষ্টামন্ডলীর সভাতেও মাইকেল থিয়েটারে অভিনেত্রী নিয়োগের প্রস্তাব করেন। মধুসূদনের সমর্থন পেয়ে বেঙ্গল থিয়েটার কর্তৃপক্ষ বারাঙ্গনাপল্লী থেকে জগত্তারিণী, গোলাপসুন্দরী, এলোকেশী ও শ্যামাসুন্দরী নামে চারজন অভিনেত্রীকে নিয়োগ করলেন। ১৮৭৩-এর ১৬ই অগস্ট মধুসূদনের ‘শর্মিষ্ঠা’ নাটক দিয়ে বেঙ্গল থিয়েটার তার যাত্রা শুরু করল আর নাট্যাভিনয়ে পুরুষের একচেটিয়া অধিকার খর্ব করে সেইদিন থেকে শুরু হল থিয়েটারে নারীদের অংশগ্রহণের ধারাবাহিকতাও। থিয়েটারে নারীর অংশগ্রহণের প্রথম প্রবক্তা মধুসূদন দত্ত এই যুগান্তকারী ঘটনা দেখে যেতে পারেননি। গোলাপসুন্দরীদের পথচলা শুরু হবার দেড় মাস আগেই তাঁর দেহাবসান হয় (২৯শে জুন ১৮৭৩)। রক্ষণশীলদের প্রবল নিন্দাবাদ সত্বেও নাট্যাভিনয়ে মেয়েদের স্বাভাবিক অধিকারকে আর ঠেকানো যায়নি। পরবর্তী ষাট বছর গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, অমৃতলাল বসু, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, দানিবাবু, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শিশির কুমার ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরীদের সঙ্গে গোলাপসুন্দরী, বিনোদিনী, তারাসুন্দরী, তিনকড়ি, কুসুমকুমারী, কৃষ্ণভামিনী, ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা, প্রভা দেবীরা বাঙালির থিয়েটার ভুবনকে আলোকিত করে গেছেন। তাঁদের অবিস্মরনীয় অভিনয় ও সংগীত প্রতিভার ঐশ্বর্য ইতিহাস হয়ে আছে।
১৮৯৮-এ কলের গান ভারতে চলে এল। কলকাতায় গ্রামফোন কোম্পানী বাংলাগান বিপণনের জন্য রেকর্ড করতে চাইলেন। কিন্তু গাইবে কে? গ্রামফোন কোম্পানী প্রখ্যাত নাট্যাভিনেতা ও পরিচালক অমরেরেন্দ্রনাথ দত্তর স্মরণাপন্ন হলেন। অমেরেন্দ্রনাথ সংগ্রহ করে দিলেন তাঁর থিয়েটারের দুইজন নাচের শিল্পী শশিমুখী ও ফণীবালাকে। থিয়েটারের নাচ-বালিকা, এই দুই বারাঙ্গণা কন্যাই বাংলা গানের প্রথম রেকর্ডশিল্পী। তারপর ২৫/৩০ বছর নীচের মহল থেকে উঠে আসা এইসব শিল্পীরা— গওহরজান, কৃষ্ণভামিনী, হরিমতি, কমলা ঝরিয়া, আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা থেকে কানন দেবীরা বাংলা গানের ভুবনকে ঐশ্বর্যমন্ডিত করে গেছেন। শিল্পীর মর্যাদায় এরা সঙ্গীত জগতে লিজেন্ড হয়ে আছেন। খ্যাতির শীর্ষ স্পর্শ করেও অন্ধকার জগৎ থেকে উঠে আসা এইসব শিল্পীরা কোনদিন মাটি থেকে পা সরিয়ে নেননি। সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী ইন্দুবালা খ্যাতির শিখরে উঠেছিলেন, গ্রামোফোন কোম্পানীর ‘গোল্ডেন ডিস্ক’, ‘সঙ্গীত নাটক আকাডেমি সম্মাননা পেয়েছেন। কলকাতার রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ আর তাঁর পদপ্রান্তে দাঁড়িয়ে উদ্বোধনী সংগীত গেয়েছিলেন ইন্দুবালা। দেশজোড়া খ্যাতি সত্বেও তিনি রামবাগানের নিষিদ্ধ পল্লী ছেড়ে অন্যত্র চলে যাননি। বলতেন ‘আমি রামবাগানের মেয়ে… রামবাগানই তো আমায় সব কিছু দিয়েছে। অর্থ, সম্মান ভালোবাসা সব…’। একদিকে দেশজোড়া খ্যাতির আলো আর অন্যদিকে রামবাগানের নিষিদ্ধ পল্লীর অন্ধকার। এই দুই-এর মাঝেই সুরের আকাশে উজ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন ইন্দুবালা।
এ দেশে যখন চলচ্চিত্র বা সিনেমা এল, প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্রর নির্মাণ শুরু হ’ল তখন আমাদের সমাজ অনেক এগিয়েছে, বাঙালির রুচিবোধের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, নিষেধের বেড়া অনেক ক্ষেত্রেই ভেঙেছে। ১৯১৩তে দাদাসাহেব ফালকে তৈরি করলেন ভারতের প্রথম কাহিনী চিত্র ‘রাজা হরিশচন্দ্র’। কিন্তু তার দশ বছর আগে ১৯০৩তে এক বাঙালি যুবক হীরালাল সেন এমারেল্ড থিয়েটারের অমরেন্দ্রনাথ দত্তর উদ্যোগে ‘আলিবাবা’ নাটকটি সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রায়িত করেছিলেন। মর্জিনার ভুমিকায় ছিলেন তখনকার প্রখ্যাত অভিনেত্রী কুসুমকুমারী। নটী কুসুমকুমারীই অতয়েব এদেশের প্রথম চলচ্চিত্র অভিনেত্রী। সে ছিল নির্বাক সিনেমার যুগ। সেলুলয়েডে শব্দ ধারণের কৌশল তখনও আয়ত্ত হয়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বদলে যাওয়া আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী বাঙ্গালির মনন ও যাপনভাবনায় বদল আসছিল ধীরে ধীরে ঠিকই, কিন্তু তখনও সিনেমা ছিল অন্ত্যজ, সম্ভ্রান্ত পরিবারের বাঙালি মেয়েরা সিনেমায় অভিনয়ের কথা ভাবতেই পারতেন না। অতয়েব থিয়েটারে নীচের মহলের মেয়েরা ছাড়া আর গতি ছিল না। বাংলা সিনেমার সেই শৈশবে সিনেমায় এলেন মঞ্চের অভিনেত্রীরা— কুসুমকুমারী থেকে শিশুবালা, নীরজাসুন্দরী, প্রভাদেবী প্রমুখ অনেকে।
১৯৩১এ বাংলা সিনেমা কথা বলতে শুরু করল। বাংলা চলচ্চিত্রের নির্বাক ও সবাক যুগের সন্ধিলগ্নে বাংলা চলচ্চিত্র পেয়েছিল নীচের মহল থেকে আসা এক নিঃসম্বল, অসহায়া বালিকাকে, নাম তার কাননবালা, পরবর্তীতে যিনি কানন দেবী— বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথম মহানায়িকা। নির্বাক সিনেমার যুগে পাঁচ টাকা পারিশ্রমিক পাওয়া কানন বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে দীর্ঘ ষাট বছরেরও বেশি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থেকে এর অভিভাবিকা হয়ে উঠেছিলেন। নীষ্ঠা, সততা আর তন্ময় সাধনায় নিজেকে অবহেলার অন্ধকার থেকে দীপ্তিময়ী ব্যক্তিত্বে উত্তরণ ঘটিয়েছিলেন কানন দেবী।
বিনোদন শিল্পে মেয়েদের আসা শুরু হয়েছিল সেইদিন, যেদিন মাইকেল মধুসূদন দত্তর পরামর্শে বেঙ্গল থিয়েটারের দ্বার মেয়েদের জন্য উন্মুক্ত হয়েছিল। সে কথা আগেই বলেছি। সমাজের রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করে কোন প্রাপ্তির আশায় আমাদের বিনোদন শিল্পের সূচনাপর্বে এসেছিলেন এইসব বারাঙ্গনা কন্যারা? তারা এসেছিলেন অন্ধকার জগতের গ্লানি অগ্রাহ্য করে মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার তাগিদে। বাঙালির প্রথম বিনোদন মাধ্যম থিয়েটার সেইসব বারাঙ্গনা কন্যাদের কাছে অন্ধকার জগতের গ্লানিমুক্তির একটা অবলম্বন হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাদের একটা তাগিদ ছিল— মুক্তির তাগিদ। থিয়েটারকে তাই তারা নিজেদের মুক্তিতীর্থ মনে করলেন, থিয়েটারকে ভালোবেসে পবিত্র হতে চাইলেন। এই পথ ধরেই থিয়েটারে এসেছিলেন গোলাপসুন্দরী, বিনোদিনী, কুসুমকুমারী, তারাসুন্দরী, কৃষ্ণভামিনী, প্রভাদেবীরা। বস্তুত নাট্যাভিনয়ে তাঁদের যোগদানের কারণেই বাংলা থিয়েটার পুরোমাত্রায় পেশাদারী হয়ে ওঠার দিকে পা বাড়িয়েছিল। গিরিশচন্দ্র স্বীকার করেছেন বিনোদিনী না থাকলে তিনি ‘গিরিশচন্দ্র’ হতে পারতেন না। কিংবা, পেশাদারী থিয়েটারের শেষ লগ্নের শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নাট্যকীর্তি অভিনেত্রী প্রভা দেবীর অবদান কে অস্বীকার করবে? তাঁর ‘দুই পুরুষ’ নাটকের অভিনয় দেখে সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন “গিরিশচন্দ্র গেছেন, কিন্তু আর এক সূর্যের আবির্ভাব হল— নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের। আর এক নতুন ধারার সৃষ্টি হল। সেই থেকে এই ধারারই বাহিকা হয়ে আবির্ভুতা শ্রীমতী প্রভা”। গিরিশচন্দ্র থেকে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার— বাংলা থিয়েটার শিল্পের নির্মাণে ঐতিহাসিক গুরুত্ব দাবি করে নীচের মহল থেকে আসা এইসব অভিনেত্রীরা। গোলাপসুন্দরী থেকে পরবর্তী ৭০/৮০ বছর বাংলা থিয়েটারকে সমৃদ্ধ করেছেন, আলোকিত করেছেন এরাই।
উনিশ শতকের ধনী বাবুদের পরস্ত্রী গমন, রক্ষিতা পোষা তখনকার সমাজ অনুমোদন করত, তাদের নারীলোলুপতা আর অনৈতিক জীবনযাপনের ক্লেদাক্ত বৃত্তান্ত আমরা জানি। কলকাতার নাগরিক জীবনের অঙ্গ স্বরূপ তখন কলকাতায় গণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সম্ভ্রান্ত বাবুদের লালসার শিকার গর্ভবতী হয়ে অনেক তরুণী বিধবা আশ্রয় নিতেন গণিকালয়ে। ধনাঢ্য ব্যক্তির রক্ষিতারাও গর্ভবতী হয়ে পড়তেন। বারাঙ্গণা নারী স্বপ্ন দেখতেন তাদের কন্যারা যেন এই গ্লানিময় জীবনের স্পর্শ না পায়। থিয়েটার তাদের সামনে গ্লানিমুক্তির পথ হয়ে দেখা দিয়েছিল। তখনকার সমাজের একটা ছোটো অংশের সহানুভুতি তাঁরা পেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের অনুগামী উপেন্দ্রনাথ দাস গোলাপসুন্দরীর বিবাহ দিয়ে সংসার পাতিয়েছিলেন থিয়েটারেরই এক যবক গোষ্ঠবিহারী দত্তর সঙ্গে। ভদ্রপল্লিতে বাসা বেধেছিলেন গোলাপ। এক সম্ভ্রান্ত পুরুষ শিশুকন্যাসহ বিনোদিনীকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন, সমাজের মানী লোকেরা যারা তাঁর অভিনয় দেখার জন্য রাতের পর রাত প্রেক্ষাগৃহে ছুটে যেতেন, তাঁকে ধন্যধন্য করতেন। তাঁরা বিনোদিনীর কন্যাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে দেননি, বাধা দিয়েছিলেন। বিনোদিনী পারেননি তার কন্যা শকুন্তলাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে। শকুন্তলাকে বাঁচাতে পারেননি বিনোদিনী, ১৩ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। বিনোদিনী পারেননি, গোলাপসুন্দরী পেরেছিলেন। গোলাপ তখন স্বনামে সুকুমারী দত্ত। মেয়েকে মানুষ করার জন্য গোলাপ থিয়েটারও ছেড়ে ছিলেন বেশ কয়েক বছর। মেয়েকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, প্রচুর অর্থব্যয় করে তার বিবাহ দিয়েছিলেন এক সমভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে। যদিও মেয়েকে দেখার জন্য তার শ্বশুর গৃহে প্রবেশের অধিকার তাকে ত্যাগ করতে হয়েছিল। জানা যায় সুকুমারীর নাতি বিহারের এক প্রসিদ্ধ ডাক্তার হয়েছিলেন।
একটু মর্যাদাময় জীবনের আকাঙ্খায় এইসব বারাঙ্গনা কন্যারা শুধু যে বিনোদন জগৎকেই তাঁদের আলোয় ফেরার পথ মনে করে থেমে থাকেননি, অনেকের পদচারণা ছিল সাহিত্যজগৎ ও সমাজকল্যাণ কাজেও। বাংলা সাহিত্যের পাঠ্য ইতিহাসকাররা তাদের সৃষ্টিকে লিখে রাখননি ঠিকই, কিন্তু ইতিহাস কোথাও না কোথাও সব কথা লিখে রাখে। মাত্র ২৬ বছর বয়সে থিয়েটার থেকে সরে আসার পর বিনোদিনী চল্লিশ বছর কলমচর্চা চালিয়ে গিয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত ‘সৌরভ’ পত্রিকায় বিনোদিনী ও তারাসুন্দরীর কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৯৬তে ‘বাসনা’ ও কনক ও নলিনী’ নামে দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন বিনোদিনী, তারপর ১৯১৩তে নাট্যমন্দির নামক পত্রিকায় নিজের আত্মজীবনী প্রকাশ শুরু করেছিলেন বিনোদিনী, পরে যেটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ‘আমার কথা’ নামে। প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা বিনোদিনীর স্মৃতিকথা সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য “এই চলতি ভাষায় লেখা দ্বিতীয় স্মৃতিকাহিনীটি সেকালের থিয়েটারের গল্প হিসাবে স্মৃতিকথা সাহিত্যে স্থায়ী আসন পেতে পারে”। তারাসুন্দরী, বিনোদিনীদের সারস্বত সাধনা তবু অনালোচিতই থেকে গেছে।
থেমে থাকেননি গোলাপসুন্দরীও (সুকুমারী দত্ত)। স্বামী গোষ্ঠবিহারী তাঁকে ত্যাগ করে চলে যাওয়ায় নিদারুণ অর্থকষ্টে পড়লেন। সেখান থেকেই ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা শুরু করলেন মেয়েদের নাচ ও অভিনয় শেখাবার একটা স্কুল খুললেন। কিন্তু বেশি দিন চালাতে পারলেন না ন্যাশানাল ফিমেল থিয়েটারের উদ্যোগে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য নাটক করলেন। ইতিমধ্যে এক সহৃদয় মানুষ, নবভারত পত্রিকার সম্পাদক বাবু দেবপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সুকুমারীর কন্যার শিক্ষা ও প্রতিপালনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। অর্থকষ্ট সামাল দিতে সুকুমারী নাট্যরচনায় মন দিলেন, নিজের ব্যক্তিজীবন ও নাট্যজীবনের অভিজ্ঞতা উজাড় করে রচনা করলেন ‘অপূর্ব সতী’ নামে একটি নাটক। নাটকটি অভিনীতও হয়েছিল। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস সুকুমারীকে প্রথম মহিলা নাট্যকারের স্বীকৃতি ও মর্যাদা দিয়েছে। বারাঙ্গনা কন্যারা থিয়েটারকে ভালোবেসে পবিত্র হতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন সমাজের মূলস্রোতে মর্যাদার জীবন পেতে। সেই মর্যাদা দিতে সমাজ প্রবল অনীহা দেখিয়েছে, তাদের অনেকেই কিন্তু সমাজকল্যাণের কথা ভোলেননি। বারাঙ্গনা থেকে অভিনেত্রী তিনকড়ি উইল করে তাঁর কলকাতার দুটি বাড়ি দান করেছিলেন বড়বাজার হাসপাতালকে, অলঙ্কারাদির বিক্রয়ের টাকা থেকে দরিদ্র প্রতিবেশিনী ভারাটের প্রত্যেককে সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করেন আর বাকি টাকা রেখে যান নিজের শ্রাদ্ধের জন্য। নীহারবালা থিয়েটার থেকে অবসর নিয়ে (১৯৫০) শ্রী অরবিন্দের পন্ডিচেরী আশ্রমে বাস করতে থাকেন। মৃত্যুর (মার্চ ১৯৫৫) আগে পর্যন্ত পন্ডিচেরী আশ্রমের ছোটোদের নাচ গান অভিনয় শেখানোর ভার গ্রহণ করেছিলেন। কৃষ্ণভামিনী তাঁর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ উইল করে দিয়ে গিয়েছিলেন শিক্ষা বিস্তারের কাজে আর দুস্থ রোগীদের চিকিৎসার্থে। তিনকড়ি, নীহারবালা, কৃষ্ণভামিনীরা ইতিহাসের নির্মাণ করেন কিন্তু ইতিহাস তাদের মনে রাখে না।
গোলাপসুন্দরী, বিনোদিনী, তারাসুন্দরী থেকে ইন্দুবালা, কাননদেবী। সময়ের ব্যবধান বিস্তর। সমাজ মানসিকতাতেও বদল হয়েছে অনেক। কিন্তু অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরনের কাহিনী একই। সমাজের নিচের মহল থেকে বিনোদন শিল্পে আসা মেয়েদের তন্ময় সাধনা, অন্ধকার জগতের সব গ্লানি মুছে দিয়ে দীপ্তিময়ী ওয়ে ওঠার কাহিনি যুগে যুগে একই থেকেছে।
আজ একুশ শতকের স্যাটেলাইট জগতে অতীতকে ফিরে দেখার আগ্রহ আমরা হারিয়েছি, সত্য। তবু এটাও সত্য যে আমাদের বিনোদন শিল্পের তিন প্রধান অঙ্গ থিয়েটার, সঙ্গীত ও চলচ্চিত্র শিল্পের নির্মাণে সমাজের নীচের মহল থেকে আসা শিল্পীদের অবদান অবিস্মরণীয়, এই কথাটা আমাদের মনে রাখতেই হবে।
তথ্যসূত্র : (১) রঙ্গালয়ে বঙ্গনটী/ অমিত মৈত্র, (২) কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত / বিনয় ঘোষ (৩) বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস / ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৪) অন্য কলকাতা / বিশ্বনাথ জোয়ারদার (৫) বাংলা একাডেমি পত্রিকা জুলাই ১৯৯৫ (৬) কলকাতা / শ্রীপান্থ (৭) আমার কথা / বিনোদিনী দাসী (৮) সবারে আমি নমি / কাননদেবী, (৯) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ / শিবনাথ শাস্ত্রী (১০) তিনকড়ি তারাসুন্দরী বিনোদিনী / উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১১) ‘সুকুমারী দত্ত এবং অপূর্ব সতী নাটক’/ ডক্টর বিজিতকুমার দত্ত – নাট্য একাডেমি পত্রিকা, জানুয়ারি ১৯৯২ ।




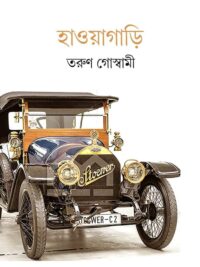





Facebook Comments