
সুমনা রহমান চৌধূরীর প্রবন্ধ
মিঞা কবিতা: স্ফুলিঙ্গ যখন মশাল
“লিখো
লিখে রাখো
আমি একজন মিঞা
এনআরসি-র ক্রমিক নং ২০০৫৪৩
দুই সন্তানের বাবা আমি
সামনের গ্রীষ্মে জন্ম নেবে আরও একজন
তাকেও তুমি ঘৃণা করবে কি
যেভাবে ঘৃণা করো আমায়?”
মূল কবিতা—
“লিখা
লিখি লোয়া
মই এজন মিঞা
এনআরসি-র ক্রমিক নং ২০০৫৪৩
দু-জন সন্তানর বাপেক মই
অহাবার গ্রীষ্মত লব আরু এজনে
তাকো তুমি ঘিন করিবা নেকি
যিদরে ঘিন করা মোক?”
কবি: ড. হাফিজ আহমেদ
মিঞা কবিতা। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সমস্ত অপমান, শোষণ, নির্যাতন, বিদ্রূপ, প্রহার— সব কিছুকে “বুড়া লুইতে-র” জলে ভাসিয়ে জন্ম নিল এক বিপ্লব। কবিতার বিপ্লব। অথবা বিপ্লবের কবিতা। জন্ম নিল আত্মপরিচয়, আত্মসন্মান খুঁজে বের করার এক নতুন লড়াই। আর মুখ বুজে সহ্য নয়। এবারে ঘুরে দাঁড়ানোর পালা। পালটা মারের পালা। ব্রহ্মপুত্র বা বুড়া লুইতের চর অঞ্চলে বাস করা পূর্ববঙ্গীয় মূলের মুসলমান যুবক-যুবতীরা দীর্ঘদিনের অপমান, বিদ্রূপ আর শোষণের প্রতিরোধে হাতে তুলে নিলেন কবিতার মশাল। মিঞা কবিতাগুলো তারই বহিঃপ্রকাশ। স্পষ্ট, নির্ভীক উচ্চারণে তারা জানান দিলেন—
“আমরাও কিন্তু বিপ্লবী হয়ে উঠেছি
আমাদের বিপ্লবে বন্দুক লাগবে না
বোমা-বারুদ লাগবে না
আমাদের বিপ্লব টিভিতেও দেখাবে না
খবরেও ছাপাবে না
কোন দেওয়ালেও দেখবে না লাল-নীল রঙে আঁকা
আমাদের মুষ্ঠিবদ্ধ হাত
আমাদের বিপ্লব তোমাদের অন্তর জ্বালাবে, পোড়াবে
পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলবে…”
(মূল কবিতা থেকে বাংলায় অনূদিত)
তারা বলছেন—
“নাই নাই, শুনক
মিঞাই আপোনাক কাহানিও গোলাম কৰিব বিচৰা নাই
কিন্তু আপোনাৰ গোলামিও আৰু মিঞাই না খাটে সেয়ে,
মিঞাৰ পোৱালীয়ে আজি আপোনাক সঁকিয়াই দিছে
আপুনি যুদ্ধ কৰিব অস্ত্রৰে
মিঞাই যুদ্ধ কৰিব কলমেৰে
কাৰন শুনামতে
অস্ত্রৰ ধাৰতকৈ কলমৰ ধাৰ বেশি চোকা
বেশি শক্তিশালী।
‘জয় আই অহম’।”
বাংলা:
(“না না, শুনুন
মিঞারা আপনাকে কখনো গোলাম করবে বলে ভাবেনি
কিন্তু আপনার গোলামিও আর মিঞারা করবে না
মিঞার বেটি আজ আপনাকে সাবধান করছে
আপনি যুদ্ধ করবেন অস্ত্র দিয়ে
মিঞারা যুদ্ধ করবে কলম দিয়ে
কারণ শোনামতে
অস্ত্রের ধার থেকে কলমের ধার বেশি তীক্ষ্ণ
বেশি শক্তিশালী।
‘জয় আই অহম’।”)
পূর্ববঙ্গীয়মূলের কৃষকদের অসমে প্রব্রজনের ইতিহাস:
মিঞা কবিতার কবিতা হয়ে ওঠার পেছনে রয়েছে দেশভাগের যন্ত্রণা এবং পরবর্তীকালে অসমের উগ্র ভাষিক এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। সেই রাজনীতি বুঝতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে অবিভক্ত অসমের ইতিহাসে। সেই ইতিহাসেই আমরা খুঁজে পাব দেশভাগের যন্ত্রণা এবং তৎপরবর্তী উত্তাল অসমের উগ্র ভাষিক এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতি।
প্রাচীনকাল থেকেই অসমের রাজনৈতিক সীমানা বারবার বদল হয়েছে, ফলত জনসংখ্যা এবং জনবিন্যাসও বারবার পালটেছে। ষোড়শ শতকে আজকের উত্তরবঙ্গ, বাংলাদেশ ও নিম্ন অসমের বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছিল কোচ সাম্রাজ্য। ১৫৮১ সালে কোচ সাম্রাজ্য বিভক্ত হয় দুই ভাগে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং রংপুর নিয়ে একভাগ এবং অন্যভাগে কামরূপ বা কোচ-হাজো। ১৬০৯ থেকে ১৬১৩ সালের মধ্যে মোঘলদের অধীনে চলে যায় কোচ সাম্রাজ্য। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে এক ফরম্যানের মাধ্যমে মোগলদের অধীন থেকে ইংরেজদের অধীনে আসে করিমগঞ্জ, ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া, বঙ্গাইগাও, কোকরাঝাড় এবং চিরাং জেলার কিছু অংশ এবং করিমগঞ্জ জেলাকে বাদ দিয়ে বাদবাকি সব অঞ্চল ইংরেজরা অবিভক্ত বাংলার রংপুর জেলার সাথে একত্রিত করা হয়। ১৮২৬ সালে আহোম রাজা এবং ইংরেজদের মধ্যে ইয়ান্ডাবু চুক্তি সাক্ষরিত হয় এবং বর্তমান করিমগঞ্জ জেলাকে বাদ দিয়ে উপরিক্ত সব অঞ্চল নয়া গোয়ালপাড়া জেলা হিসেবে উপনিবেশিক অসমে অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৬৭ সালে নয়া গোয়ালপাড়া জেলাকে কোচবিহারের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৫৬২ সাল অব্দি কাছাড় এবং হাইলাকান্দি জেলা ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর পরে ১৭৬৫ পর্যন্ত এই দুই জেলাই কোচ রাজ্যের অংশ এবং তারপর ১৮৩২ সাল পর্যন্ত কাছাড়ি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৭৪ সালে সিলেট, কাছাড়, গোয়ালপাড়া— তিনটি বাংলাভাষী জেলাকে ঢাকা ডিভিশন থেকে কেটে এনে অসমের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। আবার ১৯০৫ সালে বৃটিশ সরকার বাংলাকে দু-ভাগ করে পূর্ববাংলাকে জুড়ে দেয় আসামের সঙ্গে। আবার ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর অসমকে পুনরায় আলাদা চিফ কমিশনার ইউনিট করা হয় এবং সিলেট ও কাছাড় জেলাকে অসমের সাথে সংযুক্ত করা হয়। বৃটিশদের এহেন প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের ফলে বাংলাভাষী মানুষদের অসমে অবাধে যাওয়া আসা বৃদ্ধি পায়।
অসমের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো সমৃদ্ধ হয়েছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রব্রজন আর বসতি স্থাপনের মাধ্যমেই৷ উপনিবেশিক সময় থেকে আজ অব্দি অসমে প্রব্রজন ঘটেছে মূলত চারটি পর্যায়ে। বৃটিশদের হাত ধরে অসমে প্রথম প্রব্রজন ঘটে চা-শ্রমিকদের। বৃটিশরা অসমে চা নিয়ে আসে। এবারে চা-বাগানগুলোতে কাজ করার জন্যে প্রচুর শ্রমিকও তো চাই। সুতরাং বিহার, উড়িষ্যা, ছোটানাগপুর, মধ্যপ্রদেশ, ইত্যাদি অঞ্চল থেকে আগমন ঘটে উপজাতি শ্রমিকদের।
অসমে দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রব্রজকগোষ্ঠী পূর্ববঙ্গীয় মূলের ভূমিহীন মুসলমান কৃষকেরা। উনিশ শতকের শেষ দিকে বৃটিশরা রাজস্ব বৃদ্ধির স্বার্থে অসমের অনাবাদী জমিগুলোকে চাষের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এদিকে বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ সমস্যা, বর্মীদের আক্রমণ, কলেরা-বসন্ত-কালাজ্বরের প্রকোপে তৎকালীন অসমের জনসংখ্যা ভীষণভাবে হ্রাস পেয়েছিল৷ জঙ্গল, জলাভূমি সাফ করে বসত তথা চাষাবাদ করার মতো কঠোর পরিশ্রমী জনবলের অভাব তো ছিলই, তার সাথে ওইসব অনাবাদী জমি আবাদ করার মতো দক্ষ ব্যক্তির ও অভাব ছিল। অপর দিকে পূর্ববঙ্গের এই চাষীরা ছিল পরিশ্রমী এবং তাদের জলাভূমিতে চাষবাসের বিশেষ দক্ষতা ছিল, যা স্থানীয় জনজাতির ছিল না। সুতরাং ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধির জন্যে প্রব্রজন আর অভিবাসন ব্যতীত আর কোনো উপায় তৎকালীন বৃটিশ সরকারের হাতে ছিল না। এই কৃষকেরাও কোনো সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় জেহাদের উদ্দেশে নিয়ে অসমে পাড়ি জমাননি। এরা মূলত এসেছিলেন—
১. পূর্ববঙ্গীয় জমিদার এবং ভূস্বামীদের অধীনে ভোগ করে আসা অবর্ণনীয় কষ্টের হাত থেকে রক্ষা পেতে। এই কৃষকেরা মূলত ছিলেন নিঃস্ব, সর্বহারা শ্রেণির মানুষ।
২. ভাগচাষ প্রথার মাধ্যমে ব্যাপক শোষণ থেকে পরিত্রাণ পেতে।
৩. পূর্ববঙ্গের চেয়ে অসমে জমির খাজনা তুলনামূলকভাবে অনেক কম থাকায়।
৪. অসমের জনসংখ্যা কম, তাই চাষবাসে বিশেষ কোনো প্রতিযোগীতা না থাকায়।
৫. নদী তীরবর্তী উর্বর জমি এবং মাছের আকর্ষণে।
৬. বৃটিশ শাসকের রাজস্ব বৃদ্ধির স্বার্থে প্রব্রজনে উৎসাহ দেওয়ার জন্য। এবং
৭. অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির আগ্রহ এবং উৎসাহে।
পূর্ববঙ্গীয় কৃষকেরা অসমে এসে হিংস্র জীবজন্তু, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা ইত্যাদি অতিমারির সাথে সংগ্রাম করে এখানকার দুর্গম অঞ্চলগুলিকে মানুষের আবাসযোগ্য করে তুলেছিলেন। অনাবাদী অনুর্বর জমিগুলোও তাদের ছোঁয়ায় শস্যশ্যামল হয়ে উঠে। কৃষিও যে ব্যবসা-কর্মে পরিণত হতে পারে অসমে সর্বপ্রথম এই কৃষকেরাই সে-ধারণার জন্ম দিয়েছিলেন। বিভিন্ন প্রকার শস্যের চাষ ও অসমে এরাই প্রবর্তন করেছিলেন। এদের অদম্য পরিশ্রমের ফলে অসমে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় কয়েকগুণ। চাষবাসে পূর্ববঙ্গীয় কৃষকদের এহেন দক্ষতা দেখে মধ্যবিত্ত এবং অভিজাত অসমিয়া সমাজও তাদের পতিত জমি আবাদ করে তোলার লক্ষ্যে একান্তভাবে চাইছিলেন এদের আরও বেশি আনয়ন করা হোক। অপর দিকে পূর্ববঙ্গের ভূমিহীন কৃষকেরা জমির কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজই তেমন জানতেন না। সুতরাং তারা যখন দেখলেন অসমে গেলেই জমি মেলে, তখন অসমে তাদের আগমনের হিড়িক পড়ে যায়। এবং সরকার ও স্থানীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণির তাতে উৎসাহও ছিল বিস্তর। পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, গাইবান্ধা, জামালপুর প্রভৃতি জেলা নিম্ন অসমের সংলগ্ন হওয়ার দরুন নদীপথে সহজেই এদের অসমে প্রবেশ ঘটে।
১৯১১ সালের লোকগণনায় অসমে প্রব্রজনকারী জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫৪ হাজার। এবং তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন পূর্ববঙ্গীয় মূলের মুসলমান। ১৯২১ সাল পর্যন্ত যেহেতু অসমে প্রব্রজনের বিরুদ্ধে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না, প্রব্রজনকারীরা ধীরে ধীরে সমতলেও ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেন। এবং অভিবাসী এই কৃষকদের জনসংখ্যা ১৯২১-এ দাঁড়ায় প্রায় পাঁচ লক্ষে। প্রথম অবস্থায় এই প্রব্রজকগোষ্ঠীকে নিয়ে অসমিয়া জনগোষ্ঠীর মানুষদের তেমন কোনো সমস্যা ছিলো না। কিন্তু ধীরে ধীরে সমতলভূমিকে দখল কেন্দ্র করে অসমিয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষোভের জন্ম হয়। স্থানীয়দের উৎকণ্ঠা এবং ক্ষোভ দূরীকরণের লক্ষ্যে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ১৯২০ সালে অসমে “লাইনপ্রথা” (Line system) নামে একটি বিধি প্রবর্তন করে। এই বিধি অনুযায়ী একটা নিদির্ষ্ট সময়ের পরে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত গরিব ভূমিহীন বাঙালি কৃষক মজুরদের জমিবাড়ি উচ্ছেদের যে-অভিযান, তাই ‘বাঙাল খেদা’ নামে পরিচিত। যে-সব স্থানে প্রব্রজনের চাপ বেশি সেখানে লাইন কেটে পূর্ববঙ্গীয় প্রব্রজনকারী এবং স্থানীয় অসমিয়া জনজাতির মধ্যে এলাকা নিদির্ষ্ট করে দেওয়া হয়। আবার ‘মিক্সড এরিয়া’ বলে কিছু অঞ্চল পূর্ববঙ্গীয় প্রব্রজক এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীদের নির্ধারন করে দেওয়া হয়, যেখানে দুই জনগোষ্ঠীই বসতি স্থাপন করতে পারেন। এই লাইনপ্রথা অসমে প্রথম প্রয়োগ করা হয় নগাঁও জেলায়। পরে অন্যান্য জেলাকেও এই প্রথার আওতায় আনা হয়। অর্থাৎ অনুন্নত অসমকে শস্যশ্যামলা করে তুলতে, সরকারের রাজস্ব ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করতে যে-ভূমিহীন উদ্যমী ও দক্ষ কৃষকদের একদিন সাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসা হয়েছিল, সেই তাদেরকেই একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করে, অসমীয়া স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, ভাষিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী ভেবে নির্বিচারে উচ্ছেদ করা শুরু হয়। সেই সময়েই মূলত মৌলানা ভাসানির নেতৃত্বে লাইন প্রথার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলন শুরু হয়। পরে মৌলানা ভাসানি অসম সরকার দ্বারা গ্রেফতার হলে সঠিক নেতৃত্বের অভাবে লাইন প্রথা বিরোধী আন্দোলন ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে অসমে যদিও লাইন প্রথার অবলুপ্তি ঘটে, কিন্তু স্থানীয় অসমিয়া জনগোষ্ঠীর মন থেকে প্রব্রজনবিরোধী আবেগ অথবা পূর্ববঙ্গীয় মূলের এই জনগোষ্ঠীর উপর ক্ষোভ, বিদ্বেষ প্রশমিত হয়নি।
অসমে তৃতীয় ব্যাপক প্রব্রজন ঘটে ‘৪৭-এ দেশভাগের সময়। কয়েক লক্ষ মুসলমান কৃষক-মজুর, যারা দেশভাগের উত্তাল সময়ে ওপারে চলে গিয়েছিলেন, নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি অনুসারে তাদের এপারে ফিরিয়ে আনা হয়। ওই সময়েই সিলেটের করিমগঞ্জ জেলাটিকে অসমে রেখে বাকি সিলেটকে গণভোটের মাধ্যমে কেটে নিয়ে সদ্যনির্মিত পাকিস্তানের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। ফলস্বরূপ দেশভাগ পরবর্তী সময়ে অসমের ভৌগলিক ম্যাপ আবারও এক জটিল রূপ ধারণ করে। অসমে চতুর্থ তথা সর্বশেষ প্রব্রজন ঘটে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময়। পাকিস্তানি সেনা এবং স্থানীয় রাজাকারদের অত্যাচারে পূর্ববঙ্গীয় বহু হিন্দু পরিবার অসমে পালিয়ে আসেন। এহেন প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক অদলবদলের ফলে অসমে বাংলাভাষীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠলেন।
বাংলাভাষীদের এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অসমিয়া জনজাতির কাছে অশনি সংকেত হিসেবে দেখা দেয়। অসমীয়া জাতীয়তাবাদীরা নিজেদের অস্তিত্ব, ভাষা, সংস্কৃতি রক্ষার উদ্দেশ্য পূর্ববঙ্গ থেকে আসা অশিক্ষিত মুসলমান চাষী মজুরদের, যারা সামাজিক এবং রাজনৈতিক— দুইভাবেই ছিল ক্ষমতাহীন, তাদের উগ্র ভাষিক রাজনীতির দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহার করলেন। অসমীয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বাঙালি জনগোষ্ঠীকে অসমে সংখ্যালঘু করে তোলার রাজনৈতিক স্বার্থের খাতিরে পূর্ববঙ্গীয় মূলের প্রব্রজক জনগোষ্ঠীকে বুঝানো হল নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে চাইলে তাদের অসমীয়া সমাজ-সংস্কৃতিকে আপন করে নিতে হবে। তারা বৃহত্তর অসমীয়া সমাজ-সংস্কৃতিরই অংশ। অতএব তাদের উচিত মাতৃভাষা হিসেবে বাংলাকে বর্জন করে অসমীয়া ভাষাকে গ্রহণ করা। অভিবাসী কৃষক মজুরদের কেউ কেউ সামাজিক-রাজনৈতিক নিরাপত্তার কথা ভেবে, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে ১৯৫১ সালের আদমসুমারিতে মাতৃভাষা কলামে অসমীয়া লিখলেন। আবার কারো কারো মতামতের তোয়াক্কা না করেই সেনসাস কর্মীরা তাদের জাতি ‘অসমীয়া’ লিখে দিলেন। এভাবেই অসমীয়া নেতাদের ছল, বল আর চাপের কাছে নতি স্বীকার করে ক্রমে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অভিবাসী মুসলমানেরা সবাই সরকারিভাবে অসমীয়া ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। এবং এরই ফলে ১৯৭১ সালের লোকগণনাতে অসমীয়া জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৬০.৪৯ শতাংশে। এবং অভিবাসী মুসলমানদের নতুন পরিচয় দেওয়া হল ‘ন-অসমীয়া’। মানে নতুন বা নব্য-অসমীয়া। জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা, হোমেন বরগোহাঞি প্রমুখ অসমীয়া সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের হাত ধরে ন-অসমীয়া শব্দটি ক্রমে অসমে বহুল জনপ্রিয়তা লাভ করে।
১৯৭৯ সালে আসুর নেতৃত্বে অসমে শুরু হয় ‘বিদেশী খেদাও আন্দোলন’। সমস্ত অসমীয়া সমাজ এই আন্দোলনকে সমর্থনে এগিয়ে আসে। উগ্র অসমীয়া জাতীয়তাবাদীরা স্লোগান তুললো বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা অসম দখল করে নিচ্ছে। বাংলাভাষী মানেই অসমে বহিরাগত, এটাই সামাজিক তত্ত্ব হিসেবে সমস্ত অসমীয়া সমাজে বহুলভাবে গৃহিত হয়। ১৮৭৪ থেকে ১৯৪৭— এই দীর্ঘসময়ের সমস্ত ইতিহাসকে অস্বীকার করে আসু হিসেব দিল অসমে ৯০ লক্ষ বিদেশি ঘাঁটি গেড়েছে, যার মধ্যে ৫০ লক্ষ বাঙালি হিন্দু এবং ৪০ লক্ষ চর অঞ্চলের ন-অসমীয়ারা। মিথ্যা তথ্য অতি শীঘ্রই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শুরু হল ভাষিক দাঙ্গা। ক্রমে তা পরিবর্তন হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। নেলি, চাউলখোয়া, শিলাপাথার, গহপুর, মুকালমুয়া-সহ বহু জায়গায় নির্বিচারে হত্যা করা হল ভাষিক এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের। আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হল গ্রাম-কে-গ্রাম। অথচ ঐতিহাসিক সত্য হল অসম একটি বহুভাষিক রাজ্য। এবং স্বাধীনতার অনেক আগেই এখানে বাঙালি এবং পূর্ববঙ্গীয় মূলের মুসলমানদের আগমন ও বসবাস। আসুর তথ্য মতে যে ৪০ লক্ষ ন-অসমীয়া বা চর অঞ্চলের মানুষকে বিদেশি বলে হিসেব দেওয়া হয়েছে, ‘৫১ সালের সেনসাসে এবং তার পরবর্তী সময়ে অসমীয়া ভাষিক নেতাদের চাপে এই ন-অসমীয়ারাই তাদের মাতৃভাষা অসমীয়া লিখেছিলেন। অসমীয়া সমাজ-সংস্কৃতির অংশ এই চর অঞ্চলের মানুষেরা, এই কথাই তাদের বলা হয়েছিল। অথচ সমস্ত ইতিহাসকে অস্বীকার করে এদেরকেও বাংলাদেশি বলে চিহ্নিত করা হয়। ন-অসমীয়া পরিচয়ের পরিবর্তে ‘মিঞা’ শব্দটি তুচ্ছার্থে উচ্চারিত হতে থাকে এদের প্রতি। মিঞা মানেই বিদেশি, মিঞা মানেই বাংলাদেশি, মিঞা মানেই অস্পৃশ্য— এই ধারণা অসম আন্দোলন বা বিদেশি খেদাও আন্দোলনের সময় থেকে আজও বহমান। সেই সময়ে বিভিন্ন দেওয়ালে দেওয়ালে স্লোগান লিখা হয়েছিল— ‘মিঞাহঁত অসম এরি গুচি যা’ (মিঞারা অসম ছেড়ে চলে যা)/‘পিন্ধে লুঙ্গি চোরর বেশ, ব’ল মিঞা বাংলাদেশ’ (পরনে লুঙ্গি চোরের বেশ, যাও মিঞা বাংলাদেশ) ইত্যাদি।
উর্দু শব্দ ‘মিঞা’ এই উপমহাদেশের মুসলমান সমাজে একজন ব্যক্তির সম্মানার্থে ব্যবহার করা হয়। ঠিক যেভাবে বৃহত্তর বাঙালি হিন্দু সমাজে ‘বাবু’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষের অসম রাজ্যে ‘মিঞা’ শব্দটি গালি হিসেবে ব্যবহৃত হয় চর অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলমানদের প্রতি। ‘মিঞা’ ডাকটির ভেতরে লুকিয়ে থাকে চুড়ান্ত ঘৃণা, অস্পৃশ্যভাব আর বিদ্বেষ। শব্দটির অর্থ বিকৃত করে এমনরূপে ব্যবহৃত হয় যে, অসমে একটা পশুর সমান মূল্যও এই জনগোষ্ঠীর মানুষদের নেই। এদেরকে আবার কখনো ‘গেদা’, ‘পমুয়া’, ‘চরুয়া’ বলেও অভিহিত করা হয়। পমুয়া শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ যারা পাম-চাষের সঙ্গে জড়িত। অথচ অর্থ বিকৃত করে শব্দটিকে ‘অভিবাসী’-র সমার্থক হিসাবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ব্যবহার করা হয়। একইভাবে চরুয়া শব্দটির অর্থ যারা চরে বসবাস করেন। অথচ এই শব্দটিরও মানে বিকৃত করে অত্যন্ত তুচ্ছার্থে এবং হেয় প্রতিপন্ন করার অভিপ্রায়ে এই জনগোষ্ঠীর প্রতি ব্যবহার করা হয়। এদেরকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী হিসেবেও বহুলভাবে অসমীয়া জনমানসে প্রচার করা হয়। ২০০৫ সালের অসমের ভয়ংকর বন্যায় ভেসে যায় ব্রহ্মপুত্রের চরগুলো। অসহায় মানুষগুলো যখন গুয়াহাটির ফুটপাতে এসে আশ্রয় নেন, তখন গুয়াহাটির নামকরা কলেজ, যা এখন ইউনিভার্সিটির মর্যাদা লাভ করেছে, সেই কটন কলেজের ছাত্ররা ওই সর্বস্ব হারানো মানুষগুলোকে জোর করে তাড়িয়ে দেয় ফুটপাত থেকে। চর অঞ্চলের ‘মিঞা’-দের প্রায়ই এরকম বহিষ্কারের সম্মুখীন হতে হয়। শুধু বন্যা বা দুর্যোগই নয়, চরের ছেলেমেয়েরা যখন উচ্চশিক্ষার জন্যে অসমের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে আসেন অথবা কাজের সুত্রে গুয়াহাটি, ডিব্রুগড়-সহ বিভিন্ন স্থানে যান, সেখানেও নানা বৈষম্য ও তাচ্ছিল্যের সম্মুখীন হতে হয় তাদের। এতটাই সুতীব্র ঘৃণা, অবজ্ঞা অসমীয়া জনমানসে লালিত হয় এই মানুষদের প্রতি।




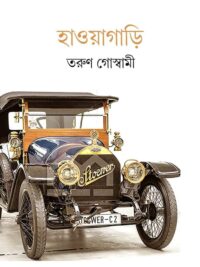





Facebook Comments