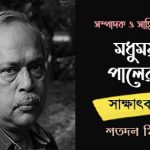
মধুময় পালের সাক্ষাৎকার
এক দেশভিখারির মাটি অন্বেষণ
[লেখক মধুময় পালের সঙ্গে আলাপচারিতায় শতদল মিত্র]
যে নির্জনতা কুমির ডেকে আনে।
…
সার সার ঢিবির বিশাল মৃত সব। কেউ মুখ তোলে না। কেউ প্রশ্ন করে না। প্রণত তারা হাততালি দেয় গাছের ডালে ডালে। বাতাস তাদের আনুগত্যের সংবাদ বয়ে শান্তি প্রচার করে অন্যত্র। রেল লাইনে মাথা ছেঁটে মানুষ দ্রুত খালের জলে গা ধুয়ে নেয়। সাহসী যারা, মুণ্ডু ভাসিয়ে দেয়, এমনিই থাকে। কেউ কেউ সংস্কার বা সুবিধাগত কারণে ক্লিপ-কাঁটা দিয়ে পরচুলার মতো ফের এঁটে রাখে। এখানে ঝুমঝুমি বাজালে গাছেরা ডাল নাড়ে, এবং বলে রাখা ভালো, কোনো ডালে পাতা নেই। এখানে ঝুমঝুমি বাজালে মুণ্ডু-ছাঁটা মানুষ ফেরার পথে দেওয়াল ঘসটে কোমর নাচায়। জানিয়ে রাখা দরকার, এই রুট-গ্রাফ অনেকে গোপনেও খুঁজতে পারেন, গা ধুতে যাওয়ায় ও ধুয়ে ফেরার পথ দু-টি ভিন্ন। যাওয়ার পথ ইড়া। ফিরতে হবে পিঙ্গলা দিয়ে। পশ্চিমে রেল লাইন। পুবে খাল। খালের জল ইতিহাসের সব তৃপ্তিহীন কামের গলিত দেহের ন্যায় সবুজ। রেল লাইন স্রোতস্বতী।
— ‘আলিঙ্গন দাও, রানি’

কোনো প্রথাগত প্রশ্নে না গিয়ে প্রথমেই জানতে চাইব আপনার লেখক হয়ে ওঠা।
দেখো আমার কিন্তু লেখক হওয়ার কোনো ইচ্ছা ছিল না। এখনও নেই। আমার একটাই বাসনা ছিল, আছে— তা হল পাঠক হওয়ার। আমি চিরকালের আগ্রাসী পাঠক। চার মাস বয়সে ওপার বাংলা থেকে চলে আসতে হয়। দাদু-দিদিমার সঙ্গে। ১৯৫২ সাল। উঠি পার্কসার্কাসের গোবরা বস্তিতে। দাদু ময়মনসিং-এর কিশোরগঞ্জে কবিরাজ ছিলেন, পসারও ছিল। এখানে পসার জমল না। জমার প্রশ্নও ছিল না। বাবা ছিলেন কুমিল্লা ব্যাংকের নারায়ণগঞ্জ শাখার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। ব্যাংকে লালবাতি জ্বলায় তাঁকেও চলে আসতে হয় সব ছেড়ে দিয়ে। বাবা ঘর ভাড়া নেন প্রথমে এন্টালি উড়িয়া পাড়ার বস্তিতে, তারপরে উঠে যান পোদ্দার নগরে দখল করা মিলিটারিদের ছেড়ে যাওয়া ব্যারাকের তিন তলার এক কামরা ঘরে। সেখান থেকে ডাঃ সুরেশ সরকার রোডের বস্তিতে। কিন্তু আমার শৈশবের বেশিরভাগটাই কেটেছে দাদু-দিদিমার সঙ্গে গোবরা বস্তিতে। দাদু ছিলেন নেতাজি সমর্থক। অমৃতবাজার পত্রিকা পড়তেন। আমার জীবনে দাদু-দিদিমার প্রভাব অনেকটাই। দিদিমা অনভ্যস্ত হাতে ঘুঁটে দিতেন, গুল দিতেন। ছোটো আমি দিদিমার সঙ্গে খাটাল থেকে গোবর নিয়ে আসতাম। ঘুঁটে, গুল রেল লাইনের ধারে শুকতে দিতাম। দিদিমা ফুল গেঁথে মালা তৈরি করতেন। সেই ঘুঁটে-গুল-মালা বিক্রি করে দিদিমা সংসার চালাতেন। তবুও তিনি বই কিনতেন। দেব সাহিত্য কুটিরের ছোটোদের বঙ্কিম, এছাড়া শরত্চন্দ্রের ‘রামের সুমতি’, ‘নিষ্কৃতি’ এবং পাঠক আমার পথ চলা। এছাড়া স্কুল পাঠ্য কিশলয়, ইতিহাস তো ছিলই। পড়ার এত নেশা ছিল যে, বাড়িতে তো খবরের কাগজ আসত না তাই সেই বয়সেই পাড়ার চায়ের দোকানে দোকানিকাকুকে অনুরোধ করে রোজ কাগজ পড়তাম, অবশ্যই খেলার খবরই, তবুও। এছাড়া আমাদের বাড়িওলার বাড়িতে পুজোয় দেব সাহিত্য কুটিরের পূজাবার্ষিকী— উদয়ন, পূর্বাচল এইসব নামের বই আসত, সেগুলোও চেয়ে গোগ্রাসে গিলতাম। একদিন তো বই-ই চুরি করি বাড়িওলার ঘর থেকে। সুশীল জানার পুরাণ-উপনিষদ্ বিষয়ে ‘সেকালের গল্প’। টুক করে জমার নীচে পেটের মধ্যে লুকিয়ে ফেলি। সবাই খুঁজছে। আর আমি তো তখন ঘামছি। বস্তির ঘর— সবার ঘরেই সবার যাতায়াত, তাই বাইরে লুকিয়ে দ্রুত পড়ে ফেলি বইটা। তখন থেকে স্বপ্ন দেখতাম বড়ো হলে সুযোগ পেলে অনেক-অনেক বই কিনব। সত্যিই আজ আমার ঘরে অজস্র বই। অনেক বিষয়েরই রেফারেন্স ঘরেই পেয়ে যাই।
এই পড়ার নেশাই কি আপনার লেখক সত্তাকে উসকে দিল?
আমার সিরিয়াস লেখালেখির শুরু কিন্তু আমার চল্লিশ বছর বয়সে। তার আগে বঙ্গবাসী কলেজে পড়ার সময় ১৯৬৭, বন্ধুদের অনুরোধে অন্তর্কলেজ প্রতিযোগিতায় নাম দিই। বন্ধু অরুণ ঘোষ অমৃতে গল্প লিখত— রুন ঘোষ নামে, আমার চোখে ও তো হিরো! যাইহোক ‘তরাই’ শব্দটা মাথায় ছিল। প্রথম হই। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘পদাতিক’ উপহার পাই। পরে আর কোনো কবিতা লিখিনি। তারপর রাজনীতি, সংসারের দায়িত্ব— লেখা আর হয়ে ওঠেনি। পরে ১৯৭৯ সালে আবারও বন্ধুদের চাপে এখানকার স্থানীয় এক সাহিত্যবাসরে পাঠ করি টুকরো গদ্য— ‘অপ্রতিম চিত্রকল্প ভেঙে যায়’। প্রথম গল্প ‘মানচিত্র’ প্রকাশ পায় ‘শব্দবর্ণ’ পত্রিকায়। ২-৪ বছর পর আবার লেখা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৯২-এ এক পরকীয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়ি। টানাপোড়েনে ৪-৫ বছর লেখা বন্ধ থাকে। প্রেম ভাঙায় রক্তাক্ত অবস্থায় লিখলাম ‘অবৈধ সন্তানের জন্য’, ‘রক্তকরবী’-তে প্রকাশ পায়। ‘সান্ধ্য প্রতিদিনে’ প্রকাশিত হয়— ‘নদী নদী খেলা’। প্রথম গল্পের বই ‘মধুময় পালের গল্প’, ‘রক্তকরবী’ থেকে প্রকাশ পায়।
চল্লিশ বছর… এত বয়সে এসে লিখতে শুরু করলেন, নিশ্চয় ভেতরের কোনো তাগিদ…
পড়ছি তো বাছবিচারহীন কিন্তু মন ভরছে না। ১৯৬৭ হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সান্নিধ্যে আসি। নকশাল রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ি। ধরা পড়ি। ক-দিন পর ভ্যানে করে নিয়ে গিয়ে রাতের অন্ধকারে ছেড়েও দেয় পুলিশ। আমরা তিনজন ছিলাম। ভাবলাম, যেমন হত সে-সময়, আমাদের এবার পেছন থেকে গুলি করে মেরে দেবে। কী মনে হল ভ্যানের হেড লাইটের দিকে তাকিয়ে পেছন দিকে হাঁটতে লাগলাম, আমার দেখাদেখি অন্য দু-জনও,— যেন সামনাসামনি গুলি চালাবে না! যাইহোক আমাদের না মেরেই পুলিশ যেতে দিল। ছাড়া পেয়ে দেখলাম সবাই আমাদের এড়িয়ে চলছে। সে এক দুঃসহ সময় গিয়েছে। রাজনীতিই আমার ভাবনাকে একটা নির্দিষ্ট শরীর দেয়। বুঝলাম সমাজ বাস্তবতা বা সোস্যাল কনটেন্ট না থাকলে সাহিত্য দাঁড়ায় না। মনের খিদে মেটাতে আমি সেই সময় মানিক, সতীনাথ, জ্যোতিরিন্দ্র, দীপেন্দ্রনাথ পড়তে শুরু করি। ১৯৭৯— আধুনিক বাংলা সাহিত্য নিয়ে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে শিবনারায়ণ রায়-এর একটা আলোচনা শুনি। তিনি বলেন যে, মানিকের পরে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। আমি ‘লালসালু’ পড়েছি— প্রতিবাদ করি জ্যোতিরিন্দ্র, দীপেন্দ্রনাথের রেফারেন্স টেনে। তিনি তাঁর বক্তব্যে স্থির থাকলেন। পরে ‘কাঁদো নদী কাঁদো’, ‘চাঁদের অমাবস্যা’ পড়ি। ভীষণভাবে প্রভাবিত হলাম। ওয়ালীউল্লাহতে পেয়ে গেলাম সোস্যাল কনটেন্টের সঙ্গে ভাষা-শৈলীর তাল-মিল, যা আমাকে লিখতে উদ্বুদ্ধ করল। ভাবলাম নিজের লেখার প্রয়োজন। কেন জানি না আমাদের সাহিত্যে সমাজ বাস্তবতা, মন্বন্তর-দেশভাগ-উদ্বাস্তু সমস্যাকে যেন এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এমনকী কম্যুনিস্ট দল ও লেখকরাও এড়িয়ে গেছে। এই যে মন্বন্তর-দেশভাগ-উদ্বাস্তু সমস্যা-সম্প্রদায়িককতার সমাজ বাস্তবতা, আমি সেই সমাজ বাস্তবতাকে ধরব বলেই লিখতে আসি, উপযোগী ভাষা খুঁজতে থাকি। আর এ-অন্বেষণে আমাকে প্ররোচিত করে প্রথমত মন্বন্তর ও বাঙালি জীবন, দ্বিতীয়ত দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবন— এই দুইয়ের অভিঘাতে বাঙালির বাঙালিত্ব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। বাঙালি দেশ হারাচ্ছে, পাচার হচ্ছে তার ঘরের মেয়ে। বাঙালি ভাষা, সংস্কৃতি হারাচ্ছে। আর তৃতীয়ত আমার লেখার প্রেরণা হয়ে ওঠে নকশালবাড়ি আন্দোলন— এক বিরাট সম্ভাবনার বিরাট ব্যর্থতা, নষ্ট হওয়া। স্বদেশী আন্দোলনেরই যেন অন্য রূপ এই নকশালবাড়ি আন্দোলন। উজ্জ্বল একঝাঁক ছেলে ব্যক্তিস্বার্থে নয়, শুধুমাত্র উন্নততর এক সমাজের আকাঙ্ক্ষায় নিজেদের জীবন-জীবিকা বিসর্জন দিল। এ-বঙ্গে বাঙালির শেষবারের মতো হয়ে ওঠা ওই নকশালবাড়ি আন্দোলন।
এ-প্রসঙ্গে মনে আসে ‘দেশভিখারি’ শব্দটা— যা আপনার সৃষ্টি। এই শব্দটার গভীরতা অনেকখানি। ছিন্নমূল মানুষের প্রতি তীব্র ভালোবাসাই কি আপনাকে ‘দেশভাগ: বিনাশ ও বিনির্মাণ’, ‘ক্ষুধার্ত বাংলা’, ‘মরিচঝাঁপি’— এই বইগুলো প্রকাশে উত্সাহিত করেছিল?
চার মাস বয়সে চলে আসি, ফলে বাংলাদেশের স্মৃতি মূলত মা-দিদিমার কাছে যেটুকু শোনা। দেশভিখারি— এ-শব্দে ভূমিকা দাদুর। তাঁর কাছেই দ্বিজাতি তত্ত্বের কথা শুনি। ছোটোবেলায় শুধু এটুকু বুঝেছিলাম— আমাদের যাবতীয় কষ্টের মূলে দেশভাগ, যার ফলে আমাদের নিজেদের ভিটে, মাটি, দেশ ছেড়ে এককথায় চলে আসতে হয়। আমার দাদু দেশভাগ মেনে নিতে পারেননি, মানা সম্ভবও ছিল না। ছিন্নমূল মানুষের হাহাকার তখন থেকেই আমার মনে চারিয়ে যায়। কোনো কারণ ছাড়াই কোটি কোটি মানুষ যেন দেশভিখারি হয়ে এদেশে টিকে থাকার লড়াই-এ সামিল হয়। যা আমাকে ধাক্কা দেয় আজও। প্রথমে মন্বন্তর, পরে দাঙ্গা, দেশভাগ— আসলে গরিব বাঙালি ধাক্কা সামলাতে পারেনি। কোটি কোটি গরিব মানুষ তাই এক হতে পারেনি। অথচ এ নিয়ে তেমন কোনো লেখালেখি হয়নি। এই উদাসীনতাই আমাকে এ-বিষয়ে কাজ করতে প্ররোচিত করে। বামফ্রন্টের আমলে জানলাম— দেশভাগের কথা বলাটা অপরাধ। বাম আমলে অনেক কিছুই আড়াল করা হয়েছে। আর এ জন্য আমাকে অনেক মূল্যও চোকাতে হয়েছে। মড়াঘাঁটা লেখক বলে উপহাস করত। আসলে ফেলে আসা দেশ ছাড়াও এক টুকরো নিজের মাটির সন্ধানও আমাকে তাড়া করেছে। ও-দেশ থেকে এসে অনেকেই নিজস্ব মাটি, বাড়ি পেয়েছেন। কিন্তু আমাদের কোনো বাড়ি ছিল না— তাই দেশ বা ভূমি অন্বেষণই দেশভিখারি আমার সারাজীবনের খোঁজ। দেশ মানে তো কেবল কাঁটাতার নয়, ভৌগোলিক সীমানা ছড়িয়ে একটা জাগ্রত স্মৃতি— গাছ-মানুষ-জল-মাটি মানুষের মনে থেকে যায়। সেটা মাটি হারানো একটা মানুষের সারাজীবনের খোঁজ। দেশ হারানো মানে একটা বেদনা— যেন মাতৃ-পিতৃবিয়োগ। যেন দেশবিয়োগ। এই যন্ত্রণা থেকেই আমার ‘দেশভাগ: বিনাশ ও বিনির্মাণ’। এই বইয়ের ভূমিকায় দেশভিখারি শব্দটা প্রথম ব্যবহার করি। শঙ্খ ঘোষ অনুমোদন করেন।

দেশভিখারি— আবার দেশবিয়োগ! বাঃ, ভালো বললেন তো!
দেখো তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কেমন নতুন একটা শব্দ সৃষ্টি হল! আসলে মাটির টান! এই মাটির টান, বেদনা থেকেই আমার লেখায় দেশ খোঁজা। এ-দেশে এসে ও-দেশের মানুষরা কলোনি গড়ে সেখানে তাদের স্মৃতির বসত করেছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে কলোনি তার নিজস্বতা হারিয়ে ফেলল। গড়ে উঠল ফ্ল্যাট কালচার। শুধু তো ও-দেশ থেকে আসা মানুষই নয়, হঠাৎ করে বিপুল জনসংখ্যার চাপে এ-বঙ্গের মানুষও তো অর্থনৈতিকভাবে চাপে পড়ে গেল। ফলে দুই বাঙালিই দেশ হারাতে বাধ্য হল। আমাদের আবারও পরিযায়ী হতে হল। ওদিকে হিন্দির আগ্রাসন—বাঙালির ভাষা-সংস্কৃতি, সেই সঙ্গে তার জাতও নষ্টের পথে এ-বঙ্গে। বাঙালির সংস্কৃতি বোধহয় টিকে থাকবে ওপার বাংলায় শুধু।
আপনার কি মনে হয় না যে, ওপার বাংলায়ও মৌলবাদী আক্রমণ, সে-সঙ্গে আরবি-ফারসির সংক্রমণ— ও-বঙ্গেও বাংলা সংস্কৃতি বিপন্ন?
কিছুটা হয়তো, তবে পুরোটা নয়। কেন-না ও-বঙ্গে প্রতিটি রাজনৈতিক দলই বাংলাকেন্দ্রিক, নিজের দেশকে ভালোবাসে, ওদের নিজস্ব পুঁজি। কিন্তু উলটোদিকে এ-বঙ্গে বাংলাকে ভালোবাসে এমন কোনো দল নেই, সবাই কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী— অন্তত বিধান রায়ের পর। অথচ হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, কেরল, তামিলনাড়ু— এদের দলগুলো নিজেদের জাতকে, ভাষা-সংস্কৃতিকে ভালোবাসে। লালন করে।
আপনার কি মনে হয় না যে, মন্বন্তরের অসহায়তা, বা দেশভাগজনিত কারণে যে-দাঙ্গা, অত্যাচার— এটা উঠে আসেনি বাংলা সাহিত্যে, যেমনটা পাই উর্দু সাহিত্যে। এ-দেশে এসে তাদের দুর্ভোগ, তাদের জীবন সংগ্রাম— তার বর্ণনা পাই, কিন্তু কেন আসতে হল নিজের মাটি-ভিটে ছেড়ে তার কোনো উল্লেখ পাই না।
দেশভাগের অত্যাচারের নির্মমতাকে ধরার মতো দম বাঙালির কলমের নেই। হেমাঙ্গ থেকে ঋত্বিক কেঁদেই গেল শুধু! কারণ বলল না। যুক্তি-তক্কোয় বঙ্গবালা পূর্ব পাকিস্তান থেকে অত্যাচারিত হয়ে আসে, কিন্তু সে কি ফিরে যেতে পেরেছিল স্বাধীন বাংলাদেশে? আসলে পঞ্চাশের মন্বন্তর ও ছেচল্লিশের দাঙ্গা কো-রিলেটেড। পঞ্চাশের মন্বন্তর না হলে ছেচল্লিশের দাঙ্গা হয় না। ফাটকা টাকা পেল মুসলিম লিগ। দাঙ্গা করানো হল। লক্ষ লক্ষ লোক মরেছে, কিন্তু সে-তুলনায় বাংলা লেখা কোথায়? মন্বন্তরে ৫০ লক্ষ লোক মারা গেছে— এ-বিষয়ে ৫০টা গল্প লেখা হয়েছে কিনা সন্দেহ! রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের— ‘হাংরি বেঙ্গল’, বেলাল চৌধুরির— ‘ক্ষুধার্ত বাংলা’, তসলিমা নাসরিনের— ‘ফ্যান দাও’-এর মতো সংকলন ছাড়া মন্বন্তর নিয়ে লেখা কোথায়? গোপাল হালদার, তারাশঙ্কর ছাড়া তেমন লেখা নেই (বিভুতিভূষণের ‘অশনি সংকেত’ সে-নির্মম বাস্তবতাকে ধারণ করতে পারেনি)। হার্ড রিয়্যালিটি বাঙালির হজম হয় না। এটা ভাবায়। এ নিয়ে আজও লেখার প্রয়োজন আছে। পঞ্চাশের মন্বন্তর আমাকে আঘাত করে, ভাবায়— সে-ভাবনা থেকেই আমার ‘ক্ষুধার্ত বাংলা’।
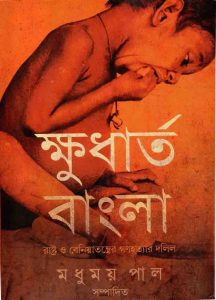




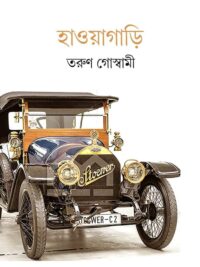





Facebook Comments