প্রবন্ধ

কিংকর দাস
পুরাতনী প্রজ্ঞা অথবা পরম্পরাগত জ্ঞান
১৯৬৯ সালের ২১শে জুলাই ভারতীয় সময় সকাল ৮টা ২৬ মিনিটে মার্কিন চন্দ্রযান অ্যাপোলো ইলেভেন ঈগল যন্ত্রাংশ থেকে বেরিয়ে চঁদের মাটিতে পা রাখলেন প্রথমে নীল আর্মস্ট্রং এবং পরে এডউইন অলড্রিন। আমার বয়স তখন সাত। আমার দাদার সতেরো। তখন অডিয়োভিসুয়াল মিডিয়ার দবদবা শুরু হয়নি। বিশ্ব ও পারিপার্শ্বিক সচেতনতা সম্পর্কে ছাত্রসমাজ ততখানি সবজান্তা সর্বস্ব মানসিকতা সম্পন্ন হয়ে ওঠেনি। তবে চাঁদে মানুষের পদার্পণ ছিল একটা যুগান্তকারী ঘটনা— সে-ঘটনায় সারা বিশ্বজুড়ে তোলপাড় উঠেছিল। আমার দাদাও তার ব্যতিক্রম নয় এবং দাদা কৌতূহলবশত আমার ছোটো দাদুকে ঈষৎ টিপ্পনি কেটে বলেছিল— কই দাদু, তোমার চন্দ্রদেবের দেশে তো মানুষ গিয়ে পৌঁছাল— তো সেখানে তোমার চন্দ্রনাথ তো দূরের কথা প্রাণের টিকিটি পর্যন্ত দেখা মিলল না। দাদার এমনতর প্রশ্ন শুনে অশীতিপর আমার ছোটো দাদু মুচকি হেসে বলেছিল— অর্বাচীন কিশোর, পুরাণে দ্বাদশ চন্দ্রের উল্লেখ আছে, যে-চন্দ্রগৃহে চন্দ্রদেবের বাস সেখানে মানুষের সাধ্য কী পা রাখার। এ-বিষয়ে আমার দাদু একা নয়। এরকম অনেক মানুষের সন্ধান পেয়ে যাবেন যাদের বৌদ্ধিক ধারণায় বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্পর্কে পুরাতনী প্রজ্ঞাটি এমনই অটল এবং অনড় যে, সেই সম্পর্কিত ধারণাটি তাঁরা লালন পালন করেন এমন নয়, তাকে অভ্রান্ত বলে মনে করেনও এবং তাকে নির্বিশেষ করে তুলতে চান— বংশপরম্পরাগত বা যুগ যুগ ধরে লালিত সাবেকি বা চিরাচরিত জ্ঞানচর্চার ফলশ্রুতির নিরিখে।
আমার যেখানে বাড়ি— সেই খড়গপুরের মালঞ্চগ্রামের চণ্ডিপুর পাড়ায়। সেই পাড়াতে বাড়ি রহমত মিঞার। রহমত একজন ধর্মপ্রাণ সরল মনের মানুষ। মক্তব পর্যন্ত তার পড়াশোনা। আপনি রহমতকে জিজ্ঞাসা করুন— চাঁদে মানুষ যাওয়ার প্রসঙ্গে, তা হেসে কুটোকুটি হবে সে। কারণ, মৌলবী সাহেবের পুরাতনী প্রজ্ঞা মোতাবেক বিদিত— চাঁদে গিয়েছিল মাকড়শা আর মহম্মদ আকবর। আর রহমতের সাবেকি জ্ঞানে— সে-ধারণা অটুট এবং চিরস্থায়ী। দু-টি ক্ষেত্রে পুরাতনী প্রজ্ঞা ও সাবেকি বা চিরাচরিত জ্ঞান আপ্তবাক্য তুল্য হয়ে গেছে এবং তা অনুশীলিত হয়েছে— পরম্পরাগত বিশ্বাস—বশবর্তী হয়ে। কোনো ক্ষেত্রেই সত্যতার যাচাই, কার্য-কারণের শৃঙ্খলাগত সূত্রে পরীক্ষিত হয়নি এবং তাদের ধারণায় বৌদ্ধিক স্তরে বিষয়টি প্রজ্ঞা বলে বিবেচিত হয়েছে আর সে-প্রজ্ঞা যেহেতু প্রাচীন ও সনাতন বলে মান্যতা পেয়েছে— তাই যুক্তি শৃঙ্খলা খুঁজতে যাওয়া তাদের কাছে অবান্তর বলে মনে হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এদের কাছে যুক্তি শৃঙ্খলাক্রমটি সর্বতোভাবে বীজগণিতীয় আংকিক পদ্ধতির সমস্যা সমাধানের জন্য ধার নেওয়ার মতো কিছু একটা, যেমন x = y কিন্তু x = y কখনো হতে পারে না। x ও y দু-টি ভিন্ন বস্তু বা অবস্থা বা পরিচায়কবাহী সত্তা, সুতরাং x ও y স্বতন্ত্র। কোন মতেই অভিন্ন নয়। একে-অপরের পরিপূরক বা সম্পূরকও নয়, তবুও একটিকে অপরটির কোনো এক অর্থে সর্বতোসমান ধরে সত্যের সমীপবর্তী হওয়ার চেষ্টা করা। কিন্তু সত্য নামক বিষয়টি যে চূড়ান্ত কোন বিষয় বা সিদ্ধান্ত নয়— তা আমার দাদুর বা রহমত মিঞার বোধে ধরা পড়ে না। এ-জন্য নচিকেতা যখন যমকে প্রকৃত সত্য কাকে বলে এমনতর প্রশ্ন করে বসে, তখন যম বাবাজীবনের তো ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি-র মতো অবস্থা; কেন-না সত্যের সেবক-পালক ও ধারক ধর্মরাজ যম ভালোভাবেই জানতেন— ‘সত্য’ নামক বিষয়টা বড়োই গোলমেলে— তা সরল ও একরৈখিক নয় বরং বহুমাত্রিক জটিল ও কূট; তাই আমতা আমতা করে জোড়াতালি গোছের কিছু একটা বলে, ভুজুং ভাজুং করে নচিকেতাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। কেন-না তিনি তো জানেন— তিনি এমন বলতে পারছেন না যে, সত্য মানে যাহা প্রকাশমান, তাহলে সত্যের অপলাপ করা হবে, যেহেতু অপ্রকাশমান সত্য বলেও তো একটা ব্যাপার আছে— যাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার বা বর্জন করতে হয়; আবার এমনও বলতে পারছেন না যাহা সত্য তাহাই সত্য, তাহলে এক্ষেত্রে কার্যকারণের যুক্তি শৃঙ্খলাকে অস্বীকার করতে হয়। তাই পুরাতনী প্রজ্ঞা আর সাবেকি জ্ঞানের অভ্রান্ততা বিষয়ে আলোচনাক্রমটি সত্যতার যথার্থতা চেয়ে বসে।
পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণে বিজ্ঞানী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সত্যের বন্ধনটি যদি সোজা না হয়— তাহলে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যে কতখানি ভ্রমাত্মক হতে পারে তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জার্মান বিজ্ঞানী কখ্-এর জীবাণুর জন্ম সংক্রান্ত পরীক্ষাটি, কখ্ একটুকরো খড় ফ্লাস্ক বন্দি করে দেখিয়েছিলেন বাইরের কোনোরূপ সংস্পর্শ ছাড়াই ফ্লাস্কের ভিতরে জীবাণুরা কীভাবে আপনা-আপনি জন্মাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু কখ্-এর পরীক্ষণে কার্যকারণ সূত্রের সত্যটি যথাযথভাবে অনুশীলিত না হওয়ায়— বিষয়টি যে অভ্রান্ত নয়— তা অচিরেই প্রমাণ করেছিলেন ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর। কখ্-এর সিদ্ধান্তরূপ প্রজ্ঞাটি ততদিন অভ্রান্তরূপে বিবেচনা পেয়েছিল, যতদিন পর্যন্ত না পাস্তুর কখ্-এর ঐ সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে দেখিয়েছিলেন— ফ্লাস্কের ভিতরে ঢোকানো খড়ের কুটোটি জীবাণু মুক্ত ছিল না। ফলে ট্রাডিশনাল নলেজ এবং পুরাতনী প্রজ্ঞার বিষয়টি যে সর্বাত্মক নির্বিরোধ— নিঃসংশয়— সন্দেহহীন— অভ্রান্ত এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। বরং এ-দুয়ের মধ্যে যুক্তি প্রতিযুক্তির শৃঙ্খলাক্রমটি যত বেশি বেশি করে সংঘটিত হতে থাকবে— তত বেশি করে সত্যের সমীপবর্তী হওয়া সম্ভবপর হবে। আর তা যদি বেদবাক্য তুল্য আপ্তবাক্যরূপে প্রতীতি লাভ করে, তাহলে বিষয়টি আপাত বিরোধশূন্য বলে পরিগণিত হলেও তা সত্য থেকে (কেন্দ্রাভিগ) সেনট্রিফুগাল হয়ে পড়ে এবং যুগ যুগ ধরে এমন ভ্রমময় প্রজ্ঞাকে সত্য রূপে গ্রহণ করে বসে আর ট্র্যাডিশেনাল থটপ্রসেস তা লালিত হতে হতে ধ্রুবরূপে বিশ্বাস লাভ করে অনুশীলিত হতে থাকে। এ-কথা তো ঠিক যে কোপারনিকাস ও গ্যালিলিও, পূর্ব পৃথিবীতে যারা জন্মেছেন এবং পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন— তারা এটাই জেনে গেছেন সূর্য নামক জ্যোতিষ্কটি পৃথিবী নামক গ্রহের চারপাশ জুড়ে ঘুরে চলেছে। আদপে ‘সত্য’ শব্দটি সম্পর্কে জনমানসে আজন্মলালিত ভ্রান্ত বদ্ধমূল ধারণাটি— সত্য সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানলাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে— ফলে wisdom এবং knowledge এ-দু-টি বিষয় একধরনের চরম ও চূড়ান্ত বা পরম মান্যতা লাভ করে বসে। প্রকৃতপক্ষে বস্তুগত জগৎ থেকে আদিম মানুষ কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে আকস্মিক ঘটনাকাণ্ডে জ্ঞান অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল, তারপর সেই অধীত জ্ঞানকে অনুশীলন পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানী প্রজ্ঞায় পরিণত করে— সেই বিশেষ জ্ঞানকে সাধারণ জ্ঞানে পর্যবসিত করেছে। এই বিশেষকে সবিশেষ বা নির্বিশেষ করে তোলাই ছিল primitive society-র সভ্যতার সাথে অগ্রসর হওয়ার প্রাথমিক লক্ষ্যে কিন্তু তা সচেতনকৃতভাবে সংঘটিত হয়েছে এমনটা বলা যাবে না। বরং কিছুটা জ্ঞানে, কিছুটা ব্যবহারিক প্রয়োজনে এবং কিছুটা অজানিতভাবে সাধিত হয়ে থাকলেও— সে-প্রয়াস নিশ্চয় বা অনড় ছিল না— তা মন্থর হলেও গতিশীল ছিল। গতিশীলতার এই প্রেক্ষিতটি গড্ডালিকা প্রবাহ অনুসরণকারী জীবন-যাপনে অভ্যস্ত জনমানসে অনুভূত হয়নি। হয়নি বলেই আজও অধিকাংশ জনমানসে বিজ্ঞান ও সত্য সমার্থকবাচক অভিধার প্রতীতি জন্ম দেয়। আমরা কলকাতার দেওয়ালে বড়ো বড়ো হরফে লিখিত লেখন দেখেছি— মার্কসবাদ সত্য— কারণ, ইহা বিজ্ঞান। যাঁরা এটা লেখেন তাঁরাও ‘সত্য’ সম্পর্কিত বিষয়টির অর্ধসত্যকেই প্রতিষ্ঠা করে। কেন-না সামাজিক সত্য কখনোই পদার্থবিদ্যা বা রসায়ণ বিদ্যার সত্যের ধ্রুবকের মতো সমপদবাচ্য হতে পারে না। তাছাড়া সত্য চির-অব্যাভিচারী বিষয়ও নয়। নিয়ত ব্যাভিচারী বলেই তার স্থিরাঙ্ক নির্ণীত হতে পারে না। আসলে সত্য সম্পর্কিত এই যে স্থাণু ধারণা— তার এইরূপ প্রেক্ষিতটি তৈরি হয়— অন্ধভাবে— হওয়ায় এবং সত্যকে একটি চরম ধ্রুবকরূপে গণ্য করার মধ্য দিয়েই। ফলে অনেক সময় আপাত সত্যকেই চূড়ান্ত সত্য বলে বিবেচনা করে বসে। এর ফলে দৃষ্টিগোচর জগতেও যেমন বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে— তেমনি আপাত দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়— এমন ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। দৃশ্যগ্রাহ্যতার ক্ষেত্রে ভ্রান্তি নিরসনের বিষয়টি আপাত দৃশ্যগ্রাহ্য নয়— এমন ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। বিভ্রান্তির স্থায়িত্ব যত দীর্ঘতাপ্রাপ্ত হবে তার ফলও যে তত মারাত্মক বা বিষময় হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে। শরবতওয়ালা তার কাচের জলভরা গ্লাসে ক্ষুদ্র আকারে শরবতী লেবুটিকে রেখে প্রকৃত আয়তন সম্পর্কে গ্রাহকের মনে যেরূপ ভ্রান্তির সৃষ্টি করে সে-ভ্রান্তি আপতিক; কেন-না লেবুর প্রকৃত অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত সংগোপন থাকছে যতক্ষণ পর্যন্ত লেবুটি জলভরা পাত্রের মধ্যে নিমজ্জমান। জল থেকে লেবুটি তুলে ফেললেই ভ্রান্তির নিরসন ঘটে। এক্ষেত্রে আপাত দৃশ্যমানজনিত যে-বিভ্রম তা সুদূরপ্রসারী নয়। কিন্তু আজও আমাদের সমাজ জীবনে এমন কিছু বিষয় আছে, যেগুলির জন্ম পুরাতনী প্রজ্ঞার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল না থাকার ফলে সামাজিক জীবনে যে-বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে— তার বিষফল আমরা এখনও ভোগ করে চলেছি। সেইরকম একটি সামাজিক প্রেক্ষিত এই আলোচনার প্রতিপাদ্য।
বৈদিক সমাজে শ্রেণিবিন্যাসের বর্গ বিভাজন নির্ণয় হয়েছিল শ্রম-চরিত্র অনুসারে। কালক্রমে সেই শ্রেণি বর্গবিন্যাস জাতিসত্তায় সমার্থবাচক হয়ে উঠল। প্রজ্ঞা বলে সেদিনকার সেই বর্গীকরণ হয়েছিল সেবা ও কায়িক শ্রমের নিরিখে-জন্ম সূত্রে নয়। অর্থাৎ, ব্রহ্মবিদ্যা জানা ও বোঝা ও অধী করার বোধ সম্পন্ন মস্তিষ্কই ব্রাহ্মণ পদবাচ্য বলে গণ্য হবেন। আর এই মান্যতা সমাজই তাকে দিয়েছিল— ঈশ্বর নয়। তিনি ঈশ্বর-বিকল্প প্রতিভূরূপে গণ্য হচ্ছেন একটি সামাজিক তথা রাষ্ট্রের সুরক্ষার প্রয়োজনে, ক্ষত্রিয়বর্গের— চাষবাসের তথা খাদ্য উৎপাদনের শ্রমজীবি হিসেবে বৈশ্য বর্গের যেমন প্রয়োজন হয়েছিল— তেমনই দরকার ছিল সমাজের এই তিন বর্গের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় অন্যান্য কায়িক শ্রমনির্ভর কাজকর্মের জন্য— শূদ্র বর্গের। মনে রাখতে হবে দ্রব্য বিনিময় প্রথার মধ্য দিয়ে সমাজ তথা রাষ্ট্র তখন প্রসারমান তাই তখনও পর্যন্ত বণিক শ্রেণির উদ্ভব ঘটেনি, তাই জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণত্ব— ক্ষত্রিয়ত্ব— বৈশ্যত্ব বা শূদ্রত্ব অর্জন ঘটবে— শ্রেণি বর্গ বিভাজনের সময় এমনতর কোনো ঘোষণাই ছিল না। তাই ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণই হবে— এমনতর বিধান বেদেও উল্লেখ নেই। কায়েমী চক্রের নিজ নিজ শ্রেণি-স্বার্থের তাগিদে মেধার বিষয়টি উপেক্ষা করে স্থিতাবস্থা বজায় রেখেছিলেন। ফলে যে-মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে চতুঃবর্গের সৃষ্টি হয়েছিল— তা পর্যবসিত হল জাতপাতের সংকীর্ণ জাতিবাচক শ্রেণিগোত্রে। সে-কারণে ব্রহ্মবিদ্যার লেশটুকু না থাকা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণের সন্তান— ব্রাহ্মণের পদবাচ্য হয়ে উঠল— ঠিক তেমনিভাবে ক্ষত্রিয়— বৈশ্য— শূদ্রদের বেলাতেও সেই বাস্তব সমানভাবে সত্য হয়ে উঠল। যুগ যুগ ধরে একটি প্রজ্ঞা (wisdom)-এর বিকৃত ব্যবহারে পরম্পরাগত (Traditional) জ্ঞানে (Knonwledge) প্রকৃত বাস্তবটি আড়ালে থেকে গেল। আমরা পেলাম জাতপাতের বিন্যাসে এক অভিশপ্ত সমাজ। যেখানে জন্মসূত্রে একধরনের মানসিক পঙ্গুত্বের শিকার হল শূদ্র বর্গের নবজাতকেরা। বিশেষ করে— সেবাদাস উপশ্রেণির শূদ্রেরা। আজও তার রকমফের ঘটেনি। রামমোহন রায় পুরোহিতদের বেদকেন্দ্রিক ভণ্ডামির মুখোশটিকে ছিঁড়ে ফেলতে চেয়ে সংস্কৃত না জানা আমজনতার জন্য বেদান্ত সমূহের বাংলাতে অনুবাদ করেছিলেন— সেই ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় অলস বাঙালিকুল সেদিকে মুখ তুলে তাকায়ওনি, ফলে ব্রাত্যজনদের হাহাকার বেড়েছে বৈ কমেনি। গান্ধীজি যতই তাদের হরিজন বলে আখ্যায় বিভূষিত করুক না কেন— সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ‘মেথর’ নামক কবিতাতে তাদের যতই শুচিশুভ্র বলে গৌরবান্বিত করুক না কেন— বর্গীকরণে বিষবৃক্ষের শিকড় এত গভীরে নিমজ্জিত যে, কেবল ব্রাত্যজনের পরিবারের সদস্য হওয়ার কারণে শ্রেণিকক্ষের বাইরের দালানে বসে পড়াশোনা করতে হয়েছে ভারতের সংবিধানের জনককে।
আসলে মূল সমস্যাটিকে বৌদ্ধিক স্তরে বিবেচনা করে তার সঠিক নিরসনের নির্দ্ধারণ না করে বাইরের দিক থেকে গৌরবের প্রলেপ দেওয়ার ব্যাপারটি মারাত্মক রকমের হাস্যকর ও ক্ষতিকারক। হাস্যকর সে-কারণে গান্ধীজির ‘হরিজন’-রা ফিরে গেছে দলিত ঘরে। আর ক্ষতি? আজও আমাদের শিশুপাঠ্যে ‘সমাজবন্ধু’ শীর্ষক একটা চ্যাপ্টার আছে— যেখানে ‘কুমোর-কামার-মুচি-মেথর-ছুতোর-ঝাড়ুদার-ডোম ইত্যাদি’ শ্রেণির কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা আছে এবং শিশুমনকে এও জানানো হচ্ছে যে, আপাত নিকৃষ্ট এইসব কাজগুলি ওইসব শ্রেণির লোকেরা করে বলেই তারা মহান। মহানত্ব প্রকাশের নমুনা এর চাইতে আর কি ভালো হতে পারে। অথচ ধরুন, কোনো একটি সরকারি স্কুলে লটারিতে এক ব্রাহ্মণের ছেলে এবং কোনো এক সাফাইকর্মীর ছেলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেলেও শ্রেণিকক্ষে যে-প্রতিস্পর্ধী সাহস নিয়ে মাস্টারমশাইয়ের প্রশ্নের উত্তর ব্রাহ্মণ ছেলেটি যেভাবে মাথা তুলে দিতে পারে— ব্রাত্যজনের পরিবারের সন্তানটি ঠিক সেইভাবে মাথা তুলতে পারে না। পারে না অনেক সময় শিক্ষকদের কারণেও। কেন-না বহুকাল আগেই সমাজ তার মাথা নত করে দিয়েছে। এই নত করার পেছনে এক সচেষ্ট ভ্রান্তি আছে। যে-ভ্রান্তির জন্ম হয়েছিল wisdom-এর হাত ধরে। যে-wisdom আজ পোক্ত ও পুরাতন আর Traditional Knowledge তার ধারক ও বাহক। তাই wisdom মাত্রই চূড়ান্ত অভ্রান্ত এমনটা নাও হতে পারে— আবার সেই wisdom, traditional knowledge দ্বারা যুগ যুগ ধরে অনুশীলিত হলেও তা অভ্রান্ত না-ও হতে পারে। শবকে কাঁধে বহন করা হয় সৎকারের উদ্দেশ্যে, কিন্তু বহু যুগ ধরে আমরা জাতপাতের যে-শবকে কাঁধে বয়ে নিয়ে চলেছি তার সৎকার কবে হবে কে জানে। আর তাই তো আমার দাদু কিংবা রহমত মিঞার traditional knowledge-টি বেশ পাকাপোক্তভাবেই বেঁচে বর্তে থাকে— যুগ যুগ ধরে।


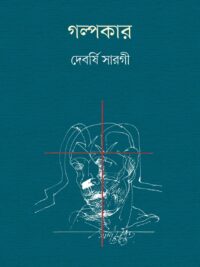
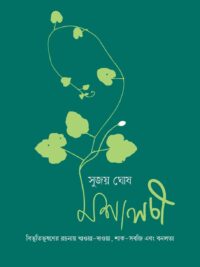
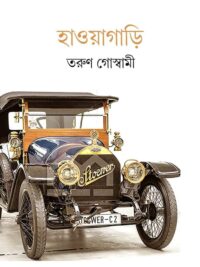
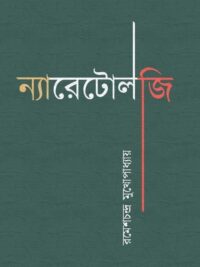
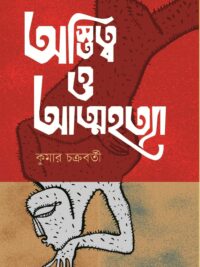



Facebook Comments