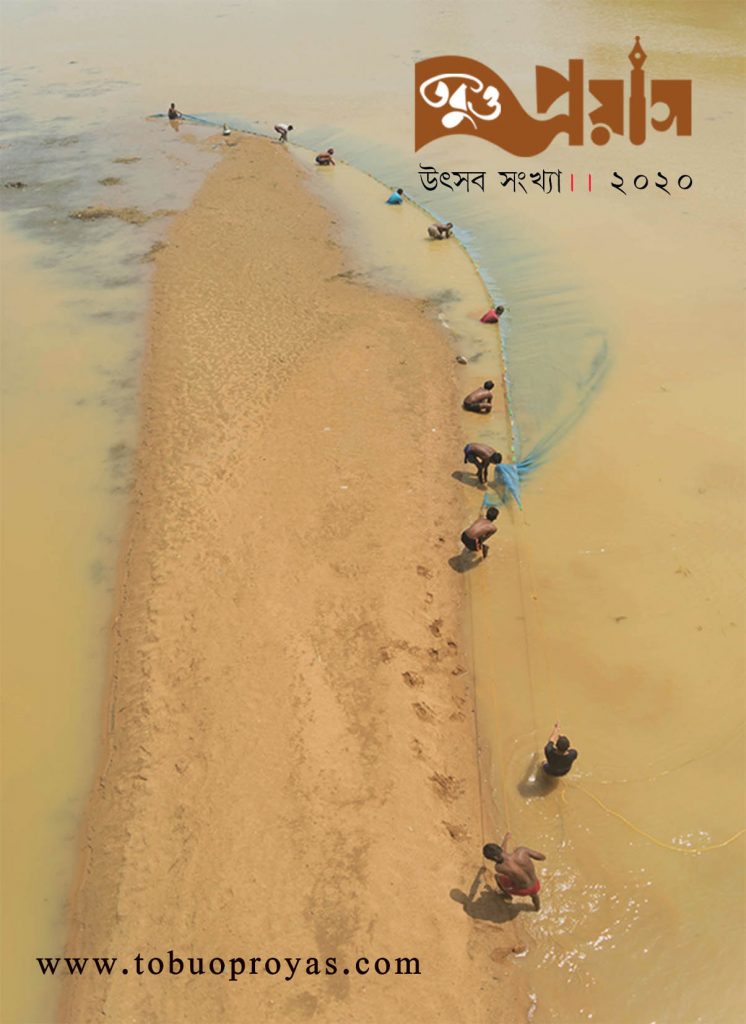ভাষান্তর: অগ্নি রায়
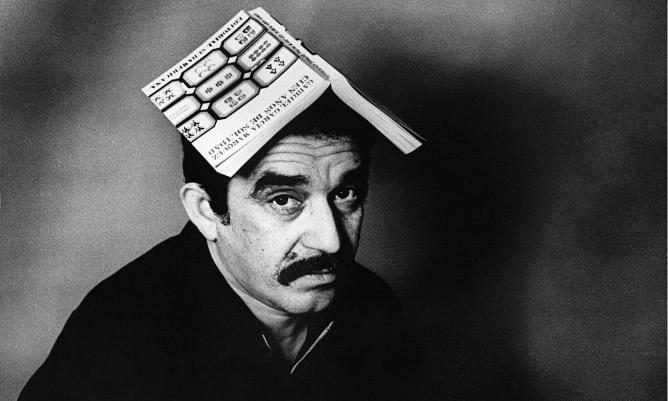
লাতিন আমেরিকার নিঃসঙ্গতা
ফ্লোরেন্সের নাবিক আন্তোনিও পিগাফেত্তা, বিশ্বভ্রমণে বেড়িয়েছিলেন ম্যাগেলানকে সঙ্গে নিয়ে। আমেরিকার দক্ষিণ ভাগের যাত্রার সেই বিবরণ তিনি লিখে রেখে গিয়েছেন। সেই ভ্রমণকথা একদিকে যেমন খুঁটিনাটি তথ্যে ভরা, অন্য দিকে কল্প-অভিযানের মতোই মুচমুচে তার স্বাদ। ওই বিবরণে তিনি লিখেছেন এক বিচিত্রদর্শন বরাহের কাহিনি! যার নাভি নাকি ছিল পশ্চাদদেশে! লিখেছেন নখহীন পাখি, জিভহীন পেলিক্যানদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের কথা। এক আশ্চর্জন্তুর কথাও বলা হচ্ছে, যার মাথা এবং কান খচ্চরের মতন, ধড়টা উটের, পাগুলো হরিণের! পাটাগোনিয়ায় এক আদিবাসীর সঙ্গে সংঘাতের বিবরণ রয়েছে ওই দলিলে। শুধুমাত্র একটা আয়না সামনে ধরে যার আক্রমণ রুখে দেওয়া গিয়েছিল। জীবনে প্রথমবার নিজের প্রতিবিম্ব দেখে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে জ্ঞান হারায় সেই দানবের মতো চেহারার আদিবাসী সর্দার।
ওই সংক্ষিপ্ত কিন্তু চমৎকার বইটিতে এক আধুনিক উপন্যাসের বীজ সুপ্ত। সেই সময়ের সংগ্রামী বাস্তবের সে এক দলিলও বটে। আমাদের কাছে যা মায়ারাজ্য, সেই এল ডোরাডোর কথাও রয়েছে তাঁর বইতে। ওই এল ডোরাডো, মানচিত্রে বার বার নিজের জায়গা পালটেছে সমসাময়িক ভৌগলিকদের আন্দাজ ও কল্পনার সঙ্গে তাল রেখে। উত্তর মেক্সিকোয় আট বছর বিফল মনোরথ এক অভিযান চালিয়েছিলেন আলভার নুনেজ কাবেজা ডি ভাকা। তাঁর ছ-শো সঙ্গীর মধ্যে মাত্র পাঁচজন প্রাণ হাতে ফিরতে পেরেছিলেন। ওই সময়কালীন বহু রহস্যময় কল্পকাহিনির মধ্যে একটি সেই প্রখ্যাত এগারো হাজার খচ্চরের গপ্পো।
স্প্যানিশ আধিপত্য থেকে আমরা আজ মুক্ত হয়েছি ঠিকই, কিন্তু সেই উন্মাদ মনোজগৎ থেকে কত দূরেই-বা যেতে পেরেছি! মেক্সিকোর স্বৈরতন্ত্রী নায়ক জেনারেল আন্তোনিও লেপেজ ড সান্তা জাঁকজমক করে তাঁর ডান পায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেছিলেন! সে-সময়কার প্যাস্ট্রির যুদ্ধে যা খোওয়া গিয়েছিল। টানা ষোলো বছর ইকুয়েডরের শাসক ছিলেন জেনারেল গ্যার্বিয়াল গার্সিয়া মোরেনা। তিনি ঘুম থেকে ওঠার সময় তাঁর চারপাশের প্রেসিডেন্সিয়াল চেয়ারগুলোতে শবদেহ বসানো থাকত ইউনিফর্ম এবং মেডেল-সহ।
চিলি নিবাসী পাবলো নেরুদা, যিনি আমাদের সময়ের এক অনন্য কবি, এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে তাঁর শব্দমায়ায় শ্রোতাদের প্রণোদিত করে গিয়েছেন এগারো বছর আগে। সেই থেকে ইউরোপের মানুষ আরও বেশি করে শিহরিত হচ্ছে লাতিন আমেরিকার অলৌকিক স্পন্দনে। এখানকার নারী ইতিহাসসিদ্ধা এবং তাড়া খাওয়ায় অভ্যস্ত পুরুষের মাথা না ঝোঁকানোর স্পর্ধা আজ কিংবদন্তীতে পরিণত। ক্ষণিক বিশ্রাম নেওয়ার অবকাশও ছিল না আমাদের। একবার এক অসমসাহসী প্রেসিডেন্ট জ্বলন্ত প্রাসাদে আটকে পড়েও একলা বিপক্ষ সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যান, যতক্ষণ তাঁর প্রাণ ছিল। দু-টি রহস্যময় বিমান দুর্ঘটনা আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ যার কূলকিনারা করা আজও সম্ভব হয়নি। ওই দুর্ঘটনায় মারা যান এক মহাত্মা প্রেসিডেন্ট এবং গণতন্ত্র রক্ষার জন্য লড়াই করা এক সেনাও। এর পর পাঁচ পাঁচটি যুদ্ধ, সতেরোটি সামরিক অভ্যুত্থানের পর উঠে আসে এক নিষ্ঠুর নির্দয় স্বৈরতন্ত্রী, যে প্রথমবারের মতো আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় জাতিদাঙ্গা ও গণহত্যার বীজ। বিশ লক্ষ শিশুর মৃত্যু ঘটে। আর্জেন্টিনার কারাগারে বলপূর্বক কয়েদ করা হয় গর্ভবতী মহিলাদের। সেখানে ভূমিষ্ঠ হয় সন্তানেরা। সামরিক শাসকের নির্দেশে তাদের পাঠানো হয় অনাথাশ্রমে। কাউকে কাউকে দত্তকও নেওয়া হয়। নির্যাতনের প্রকোপে স্রেফ মুছে যান দু-লাখ মানুষ। তাঁদের অপরাধ ছিল একটাই— তাঁরা সমাজ বদল করতে চেয়েছিলেন। এইসবের জেরে লাতিন আমেরিকার তিনটি ছোটো এবং বর্ণময় রাষ্ট্র নিকারাগুয়া, এল সালভাদোর এবং গোয়াতেমালা থেকেই উদ্বাস্তু হতে হয়েছে লক্ষাধিক মানুষ।
আতিথ্যের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে যে-রাষ্ট্রের, সেই চিলি থেকে পালিয়ে গিয়েছেন দশ লাখ মানুষ। দেশের মোট জনসংখ্যার যা প্রায দশ শতাংশ। মহাদেশের সবচেয়ে সভ্য দেশ হিসাবে যার খ্যাতি সেই পঁচিশ লাখ মানুষের ছোট্ট দেশ উরুগুয়ে। সেখানেও প্রতি পাঁচ নাগরিকের মধ্যে একজনকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি নির্বাসিত! ১৯৭৯ সালের পর থেকে এল সালভাদোর-এর গৃহযুদ্ধে উদ্বাস্তু হয়ে যাচ্ছেন প্রতি কুড়ি মিনিটে একজন। লাতিন আমেরিকার এই বিপুল সংখ্যক নির্বাসিত ও উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীকে একত্র করলে তা হয়তো নরওয়ের জনসংখ্যার চেয়ে বেশিই হবে।
আজ এটা আমি ভেবে নিতেই পারি শুধুমাত্র সাহিত্যগুণের জন্য নয়, এখানকার বাস্তবতার বেঢপ সাইজ সুইডিশ আকাদেমির নজর কেড়েছে। এই বাস্তব শুধুমাত্র কাগুজে নয়। এই বাস্তবতা আমাদের ভিতরে লালিত হয়েছে। আমাদের প্রত্যহের অসংখ্য মৃত্যু দিয়ে যা তৈরি। কখনোই তৃপ্ত না হওয়া সৃজনের আঁচকে যা লালন করেছে। বিষাদ এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত, ভবঘুরে এবং স্মৃতিমেদুর কলম্বিয়ার নাগরিককে মনোনয়ন করা হয়েছে নেহাতই ভাগ্যক্রমে। যেখানকার কবি এবং ভিক্ষুক, সংগীতকার এবং সন্ন্যাসী, সেনা এবং বাউণ্ডুলে— সকলেই এবং প্রত্যেকেই এখানকার এক অন্য বাস্তবের কুশিলব। আমাদের জীবনকে সব্বার বোধগম্য করে তোলার মতো প্রথামাফিক মালমশলার বড়োই অভাব আসলে। বন্ধুগণ সেটাই আমাদের নিঃসঙ্গতার মোদ্দা কথা।
আমাদের সংকটের ইটপাথরগুলোই আমাদের ঘিরে দেওয়াল রচনা করেছে। পৃথিবীর এই অংশের মানুষ তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক চশমা পরে উপায় খুঁজে পান না, আমাদের বুঝে ওঠার। খুবই স্বাভাবিক যে, তাঁরা নিজেদের যে-বাটখারায় বিচার করেন, সেই একই বাটখারা ব্যবহার করেন আমাদের মাপতেও। সব সংঘাত যে এক নয়, সেটা তাঁরা বিস্মৃত হন। আমাদের নিজস্ব শিকড়ের সন্ধানের যাত্রা যতটা রক্তাক্ত এবং এবং ঝঞ্ঝাময়, তা ওদের থেকে কিছু কম নয়। কিন্তু আমাদের নিজস্ব নয়, এমনই কোনো নকশায় আমাদের জীবনকে ধরতে চাওয়ার সেই চেষ্টা, আমাদের ক্রমশ আরও নির্জন, আরও অজ্ঞাত এবং পরাধীন করে তোলে। বরং ইউরোপ যদি তাদের নিজের অতীত ছেনে আমাদের বুঝতে চেষ্টা করে তাহলে তা অনেকটাই যাথার্থ পাবে। লন্ডন শহরের প্রথম দেওয়ালটি তৈরি হতে সময় লেগেছিল তিনশো বছর। আরও তিনশো বছর চলে যায় শহরের প্রথম বিশপকে বেছে নিতে।
তিপান্ন বছর আগে এই মঞ্চেই টমাস মান তাঁর লেখা উপন্যাস টোনিও ক্রোগার থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আশা জাগিয়েছিলেন, সংযমী উত্তর একদিন আবেগময় দক্ষিণের সঙ্গে করমর্দন করবে। এই তত্ত্বে আমার আস্থা ছিল না। কিন্তু এটাও বিশ্বাস করি যে, ইউরোপে যে-সব মানুষের দৃষ্ট স্বচ্ছ আজও তাঁদের লাগাতার উদ্যোগ, আমাদের সাহায্য করতে সক্ষম। কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁদের দেখার চোখ বদলাতে হবে। শুধুমাত্র আমাদের স্বপ্নের প্রতি তাঁদের মমতা থাকলেই যে, আমাদের নিঃসঙ্গতা ধুয়ে যাবে, ব্যাপারটা তো এমন নয়। বিশ্বের বন্টনে সমস্ত মানুষের জীবন যাপন করার যে-আকাঙ্ক্ষা রয়েছে তাকে যদি হাতে কলমে সাহায্য না করা হয়, তাহলে কোনো বদল আসবে না।
নিজস্ব ধ্যানধারণাকে গচ্ছিত রেখে লাতিন আমেরিকা কারো দাবার বোড়ে হয়ে থাকতে চায়নি। এমনটা চাওয়ার কোনো কারণও নেই। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় তার অভিযান এবং মৌলিক বোধ পশ্চিমের চাওয়া পাওয়ার ছকে পর্যবসিত এটা ভাবা মূর্খামি। নৌ পরিবহনের সুবিধা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ এবং লাতিন আমেরিকার ভৌগলিক দূরত্ব কম হয়েছে এটা ঠিকই কিন্তু তাদের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দূরত্ব কিন্তু ক্রমশ বেড়েই গিয়েছে। সাহিত্যে ক্ষেত্রে আমাদের মৌলিকত্বকে সহজেই স্বীকৃতি দিয়েও, সমাজ বদলের প্রশ্নে আমাদের কঠিন প্রয়াসকে কেন গ্রাহ্য করা হবে না। নিজেদের দেশগুলির সামাজিক ন্যায় প্রবর্তনের যে-লক্ষ্য রয়েছে প্রগতিশীল ইউরোপিয়ানদের, তা কেন লাতিন আমেরিকার ক্ষেত্রেও প্রবর্তিত হবে না। সেই লক্ষ্য পূরণের কৌশল ভিন্ন হতে পারে, কারণ, পরিবেশ ভিন্ন। আমাদের ইতিহাসের অপরিমেয় হিংসা এবং বেদনার কারণ হল যুগবাহিত অসাম্য এবং তিক্ততা, যা এখনও বজায় রয়েছে। আমাদের ঘর থেকে তিন হাজার মাইল দূরের কোনো ষড়যন্ত্রকের ফলশ্রুতি নয় তা। ইউরোপের বহু নেতা এবং চিন্তাবিদ কিন্তু এমন ভুলটাই করেছেন। নিজেদের যৌবনের সক্রিয় আন্দোলনকে ভুলে মেরে দিয়ে এইসব বৃদ্ধেরা বালখিল্যের মতো ভেবেছেন, বিশ্বের দুই মহাশক্তির দয়ার হাতে নিজেদের ছেড়ে দেওয়ার বাইরে কোনো কিছু করার নেই। প্রিয়বরেষু, এটাই আমাদের নিঃসঙ্গতার মূল কথা।
এ-সব সত্ত্বে নিপীড়ন, লুঠপাট এবং একঘরে করে দেওয়ার সতত চেষ্টার মধ্যেও আমরা জীবনের ডাকে বার বার সাড়া দিয়েছি. বন্যা অথবা প্লেগ, দুর্ভিক্ষ অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, এমনকী শতকের পর শতক ধরে চলা যুদ্ধ ব্যর্থ হয়েছে মৃত্যুর কাছে জীবনকে হারিয়ে দিতে। প্রতি বছর মৃত্যুর তুলনায় থেকে জন্মের সংখ্যা সাড়ে সাত কোটি বেশি। জন্মের হার দরিদ্র দেশগুলিতেই বেশি, লাতিন আমেরিকার দেশগুলিও যার মধ্যে পড়ে। অন্য দিকে সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশগুলি এমন ধ্বংসাত্মক শক্তি করায়ত্ত করতে পেরেছে যা গোটা বিশ্বের মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য, আগের তুলনায় একশোগুণ শক্তিশালীই শুধু নয়, এই গ্রহের সমস্ত জীবিত সত্তাকে নিকেশ করে দেওয়ার জন্য তা আগের তুলনায় অধিক ক্ষমতা নিয়ে হাজির।
আজকের মতনই একটি দিনে আমার শিক্ষক উইলিয়াম ফকনার বলেছিলেন, “মানুষ শেষ হয়ে যাবে, এটা আমি মানতে রাজি নই।” ছত্রিশ বছর আগে কোনো মহাকায় ট্র্যাজেডিকে তিনি কেন মেনে নিতে চাননি, কেন তা অস্বীকার করেছিলেন, তা যদি পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারি, কেবলমাত্র তাহলেই আজ এই মঞ্চে দাঁড়ানোর যোগ্যতা আমাতে বর্তাবে। সভ্যতার ইতিহাসে ওই ট্র্যাজেডি আজ বিজ্ঞানের এক সহজ সম্ভাবনা মাত্র। মানবজাতি চিরকাল যাকে কল্পকাহিনি ভেবে এসেছে, আজ সেই অভূতপূর্ব বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে মনে সমান্তরাল এক বিশ্বাস ও কল্পকাহিনি তৈরি করার অধিকারও কিন্তু তৈরি হয়েছে। এখনও দেরি হয়ে যায়নি। সে এক নতুন এবং সর্বগ্রাসী এক ইউটোপিয়া, যা জীবনের কথা বলবে। যেখানে কেউ অন্যের মৃত্যু পরোয়ানায় সই করবে না। যেখানে ভালোবাসাই একমাত্র সত্য হয়ে উঠবে। আনন্দের দিনরাত বোনা সম্ভব হবে। যে-জাতি একশো বছরের নিঃসঙ্গতার অভিশাপ ভোগ করেছে, তারা শাশ্বতকালের জন্য পৃথিবীর বুকে দ্বিতীয় সুযোগ পাবে।