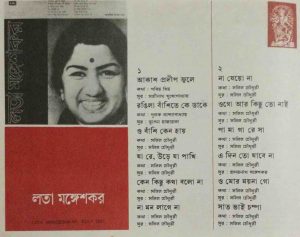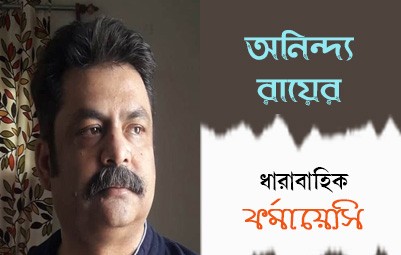সংগ্রাহক: রেভারেন্ড লাল বিহারী দে
ভাষান্তর: গৌরব বিশ্বাস
[সংগ্রাহক পরিচিতি: রেভারেন্ড লাল বিহারী দে। জন্ম: ১৮ই ডিসেম্বর ১৮২৪, বর্ধমানের সোনাপলাশী গ্রামে। কয়েকবছর গ্রামের স্কুলে পড়াশুনোর পর ছোটোবেলাতেই বাবার সাথে কলকাতায় এসে ভর্তি হন, রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাফের স্কুলে (এখন স্কটিশচার্চ স্কুল)। ছাত্রাবস্থাতেই খ্রীস্ট ধর্ম গ্ৰহণ। স্কুল কলেজে শিক্ষকতার পাশাপাশি করেছেন সাংবাদিকতাও। আর গ্রামবাংলার জীবন সংস্কৃতি নিয়ে নিরলসভাবে রচনা করেছেন গ্রন্থ। কৃষকদের দুরবস্থা, জমিদারদের অত্যাচার নিয়ে ইংরেজিতে লিখেছেন— ‘Govinda Samanta’, ‘Bengal Peasant Life’-এর মতো গ্রন্থ। সংগ্রহ করেছেন বাংলার উপকথা। দিদিমা ঠাকুমারা যে-সব গল্প শুনিয়েছেন বংশ পরম্পরায়, সে-সব উপকথাই সংগ্ৰহ করে ইংরেজিতে প্রকাশ করলেন— ‘Folk Tales of Bengal’s’। সম্ভবত এটিই বাংলার উপকথার প্রথম কোনো সংকলন। এই গ্রন্থেরই কাহিনি— ‘The Ghost-Brahman’-এর বাংলা অনুবাদ আমি করেছি। রেভারেন্ড লাল বিহারী দে মারা যান ১৮৯২ সালে কলকাতায়।]
সে বহুকাল আগের কথা। এক গাঁয়ে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করতেন। ব্রাহ্মণ কুলীন ছিলেন না। তাই বিয়ে করে সংসার পাতা তাঁর জন্য বড়ো দুঃসাধ্য ব্যাপার। ব্রাহ্মণ গাঁয়ের স্বচ্ছল মানুষদের বাড়ি ঘুরে ঘুরে অর্থ সাহায্য চাইতে লাগলেন, যাতে অন্তত বিয়ে করে সংসার ধর্ম পালন করতে পারেন। বিয়ের জন্য অর্থের প্রয়োজন। বিয়েতে জন্য বেশি কিছু খরচ না করলেও মেয়ের বাপ মাকে কিছু অর্থ তো দিতে হবে! ব্রাহ্মণ তাই গাঁয়ের দোরে দোরে ঘোরেন, গাঁয়ের বড়ো মানুষদের তোষামুদি করে খুশি রাখার চেষ্টা করেন। শেষ অবধি এদিক-সেদিক করে বিয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় হল। তারপর এক শুভ দিনে বিবাহ সম্পন্ন করে নতুন বউকে ঘরে তুললেন। ব্রাহ্মণ তাঁর মা আর নবোঢ়াকে নিয়ে একসাথে বাস করতে থাকলেন।
কয়েকদিন বাদে ব্রাহ্মণ মাকে বললেন— ‘দেখো মা, এবার তো আমায় তোমার পাশে, বউয়ের পাশে দাঁড়াতে হবে। তোমাদের সুখে শান্তিতে রাখব এমন অর্থ তো আমার নেই। তার জন্য, দূর দেশে গিয়ে যা হোক কিছু কাজকম্ম করে আমি অর্থ উপার্জন করব। কয়েক বছর দূর দেশে কাটাতে হবে আমায়, যতদিন না পর্যন্ত বেশ কিছু টাকা হাতে আসে। আমার কাছে এখন যা আছে, তা তোমায় দিয়ে যাব। ততদিন এই দিয়েই কষ্টে করে চালিয়ে নাও। সেই সাথে তোমার বৌমাকেও একটু দেখে শুনে রেখো।’
তারপর একদিন মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে ব্রাহ্মণ পথে বেরিয়ে পড়লেন। আর ঠিক সেই দিনই সন্ধ্যেবেলায় এক প্রেত হবহু ব্রাহ্মণের রূপ ধরে ব্রাহ্মণের বাড়িতে হাজির হল। নববধূ প্রেতকে নিজের স্বামী ভেবে বসল। সে তো অবাক হয়ে বলল— ‘এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে বড়ো! এই যে বললে, কয়েক বছর তুমি বাইরে থাকবে! এত তাড়াতাড়ি মন বদলে গেল!’
ব্রাহ্মণের রূপধারী প্রেত ইতস্তত হয়ে জবাব দিল— ‘মানে… ওই… যাত্রা করার জন্য আজকের দিনটা ঠিক শুভ নয়। তাই ফিরে এলাম আরকী! তাছাড়া হঠাৎ করে হাতে বেশ কিছু টাকাও চলে এল… তাই আর…।’
ব্রাহ্মণের মা-ও প্রেতকে নিজে ছেলে ভেবে বসলেন। তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহও জাগল না। প্রেত ব্রাহ্মণের ভেক ধরে বাড়ির কর্তা সেজে দিব্যি থাকতে লাগল— সেই-ই যেন আসল ব্রাহ্মণ। বৃদ্ধা মায়ের সন্তান, নবোঢ়ার স্বামী। ব্রাহ্মণরূপী প্রেতকে দেখতে একেবারে আসল ব্রাহ্মণের মতো। কড়াইশুঁটির দুই দানার মতো হবহু এক। আলাদা করার উপায় নেই। পাড়া প্রতিবেশীরাও তাই প্রেতকেই ব্রাহ্মণ ভেবে ভুল করল।
বেশ কয়েকবছর বাদে দূরদেশ থেকে আসল ব্রাহ্মণ বাড়ি ফিরলেন। বাড়ি ঢুকেই তো তাঁর চোখ কপালে। একি! বাড়িতে হুবহু তারই মতো দেখতে আরেকজন! প্রেত দাঁত কিড়মিড় করে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করল— ‘এই, তুই কে রে! আমার বাড়িতে তোর কী দরকার! ব্রাহ্মণ অবাক হয়ে উত্তর দিল— ‘আমি কে মানে! আগে বলো তুমি কে? এটা তো আমার বাড়ি। ইনি আমার মা। এ আমার বউ’।
প্রেত ব্রাহ্মণকে বলল— ‘আরে, তুই তো আজব কথা বলছিস রে! গাঁয়ের সক্কলে জানে, এ আমার বাড়ি। এরা আমার মা, বউ। বহুদিন ধরে আমরা এ গাঁয়ে আছি। আর তুই আজ কোত্থেকে এসে এমন ভান করছিস, যেন এটা তোর বাড়ি, এরা তোর মা আর বউ! তোর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি রে ব্রাহ্মণ! যা যা, দূর হ এখান থেকে!’ এ-সব বলে প্রেত ব্রাহ্মণকেই তাঁর নিজের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল।
এমন অদ্ভুত ঘটনায় ব্রাহ্মণ বাক্যহারা হয়ে গেলেন। এখন কী করা উচিত, হতবুদ্ধি ব্রাহ্মণ ভেবে কূল পেলেন না। শেষ অবধি ভেবেচিন্তে রাজার কাছে গিয়ে ব্রাহ্মণ সব ঘটনা খুলে বললেন। রাজা ঘটনার বিচার করতে এলেন। ব্রাহ্মণ আর ভেকধারী প্রেত দু-জনকে দেখেই রাজা অবাক বনে গেলেন। যেন দুই হবহু প্রতিলিপি। কী করে এ-দ্বন্দ্বের তিনি মীমাংসা করবেন সত্যিই তিনি কিছু ভেবে পেলেন না।
ব্রাহ্মণ দিনের পর দিন রাজার কাছে সুবিচারের আশায় হত্যে দিয়ে পড়ে থাকেন। তাঁর বাড়ি ঘরদোর, বউ আর মাকে ফিরে পাওয়ার কিছু একটা ব্যবস্থা করতে, রাজাকে কত করে অনুরোধ করেন। রাজা ব্রাহ্মণকে কী বলে শান্ত করবেন বুঝে পান না। রাজা তাই প্রতিদিনই বলেন— ‘কাল এসো, দেখছি’। ব্রাহ্মণও প্রতিদিন রাজার দরবার থেকে বেরিয়ে কপাল চাপড়ে কাঁদতে থাকেন— ‘কলির কাল! আমাকেই কি না আমার বাড়ি থেকে দূর করে দেওয়া হল! অন্য একটা বাইরের লোক আমার ঘরদোর স্ত্রী সবকিছু দখল করে নিল… হে ভগবান… আর রাজাই-বা কেমন! প্রজাদের সুবিচার দিতে পারেন না? আমার কপাল পুড়ল…’।
ব্রাহ্মণ প্রায় প্রতিদিনই রাজার দরবার থেকে বেরিয়ে এভাবে কাঁদতে কাঁদতে পথ চলেন। পথের মধ্যে একটা ছোট্ট মাঠ পড়ে। সেই মাঠে একদল রাখাল ছেলে খেলে বেড়ায়। গোরুগুলোকে চড়তে দিয়ে, একটা বড়ো গাছতলায় জটলা করে রাখাল ছেলেরা খেলা করে। বড়ো অদ্ভুত তাদের খেলা। ছেলেদের মধ্যেই কেউ সাজে রাজা, কেউ হয় মন্ত্রী, কেউ আবার হয় কোতোয়াল। রাখাল ছেলেরা প্রায় প্রতিদিনই ব্রাহ্মণকে কাঁদতে কাঁদতে যেতে দেখে।
যে-ছেলেটি রাখালদের রাজা, সে একদিন মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল— ওই ব্রাহ্মণ প্রতিদিন কাঁদেন কেন? মন্ত্রী, তুমি কিছু জানো? মন্ত্রী ছেলেটি কিছু জানত না এ-ব্যাপারে। তাই উত্তর দিতে সে অপারগ। তখন রাখাল রাজা একজন কোতোয়ালকে নির্দেশ দিলেন, ব্রাহ্মণকে তার সামনে হাজির করতে। একজন কোতোয়াল তখন ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বলল— ‘আমাদের রাজা একবার এক্ষুণি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান’। ব্রাহ্মণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে— ‘কেন কী ব্যাপার! এই তো রাজামশাইয়ের কাছ থেকে এলাম। উনি তো আমায় আগামীকাল আসতে বলে ভাগিয়ে দিলেন। এখন আবার আমায় ডাকছেন কেন?’
কোতোয়াল বলল— ‘না না রাজামশাই নন। এ আমাদের রাখাল রাজা।
ব্রাহ্মণ অবাক হয়ে বলল— ‘রাখাল রাজা! তিনি আবার কে? বলছ যখন, চলো গিয়েই দেখি’।
ব্রাহ্মণ রাখাল রাজার কাছে এলেন। রাখাল রাজা ব্রাহ্মণের কাছে তাঁর প্রতিদিন এভাবে কাঁদার কারণ জানতে চাইল। ব্রাহ্মণ সবিস্তারে তাঁর দুঃখের কথা জানালেন রাখাল রাজাকে।
রাখাল রাজা সব কিছু শুনে বলল— ‘হুম। বুঝতে পেরেছি কী সমস্যা। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। আপনি নিশ্চয়ই নিজের সব কিছু ফেরত পাবেন। আপনি শুধু রাজামশায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসুন, উনি যাতে আপনার এই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব আমাকে দেন’।
ব্রাহ্মণ আবার গেলেন রাজামশাইয়ের কাছে। রাজমশাইকে অনুরোধ করলেন, রাখাল রাজাকে তাঁর এই সমস্যা সমাধানের অনুমতি দিতে। রাজামশাই এমনিতেই ব্রাহ্মণের এই বিচিত্র সমস্যার সমাধান নিয়ে তিতিরিক্ত ছিলেন। তাই ব্রাহ্মণের অনুরোধে কোনো আপত্তি করলেন না।
ঠিক হল, আগামীকাল সকালেই এই সমস্যার নিষ্পত্তি করা হবে। রাখাল রাজা সমস্ত ব্যাপারটাই বুঝতে পেরেছিল। সে এক বুদ্ধি বার করল।
পরের দিন সকালে রাখাল রাজা হাজির হল। সঙ্গে সরু মুখের ছোট্ট একটা শিশি। ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণের রূপধারী প্রেত দু-জনই রাখাল রাজার বিচার সভায় উপস্থিত। রাখাল রাজা সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখল। পাড়া প্রতিবেশীদের কথাবার্তাও শোনা হল। তারপর রাখাল রাজা বলল— ‘ব্যস, অনেক কথা শুনলাম। আমি যা বোঝার বুঝে গিয়েছি। এবার এক্ষুণি এ-সমস্যার নিষ্পত্তি করব। আমার হাতে এই যে-ছোট্ট শিশিটা সবাই দেখতে পাচ্ছেন, দু-জন বিচারপ্রার্থীর মধ্যে যিনি এই শিশির ভেতর ঢুকতে পারবেন, আমার আদালত তাকেই সমস্ত সম্পত্তির প্ৰকৃত অধিকারী বলে ঘোষণা করবে এবং তিনিই হলেন আসল ব্রাহ্মণ। এখন দেখা যাক, কে এর মধ্যে ঢুকতে পারে’।
রাখাল রাজার এমন বিচারে ব্রাহ্মণ হতভম্ব হয়ে গেলেন। দুঃখ করে বললেন— ‘নাঃ… রাখাল রাজা, তুমি সত্যিই ছেলেমানুষ। এ না হলে কেমন বিচার! এইটুকু শিশির ভেতর কোনো মানুষ কি ঢুকতে পারে?’
রাখাল রাজা নির্বিকার কণ্ঠে বলল— ‘ও, আপনি তাহলে এর মধ্যে ঢুকতে পারবেন না? ঠিক আছে। আপনি যদি এর ভেতর ঢুকতে না পারেন, তাহলে সম্পত্তি, বাড়িঘর কোনো কিছুই আপনার নয়’।
‘আপনি কি পারেবন?’ প্রেতকে জিজ্ঞেস করল রাখাল রাজা। ‘যদি আপনি পারেন, তাহলে প্রমাণিত হবে, সম্পত্তি বাড়ি ঘর, স্ত্রী, মা সব আপনার। আপনিই আসল ব্যক্তি’।
রাখাল রাজার প্রস্তাবে, প্রেত একগাল হেসে বলল— ‘এ আর এমন কী! এ তো আমার বাঁ-হাতের খেলা’।
পরমুহূর্তেই সবাই দেখল, প্রেতের শরীর ছোটো হতে হতে একটা ক্ষুদ্র কীটের মতো আকার ধারণ করল। তারপর টুক করে ঢুকে গেল শিশির ভিতর। আর রাখাল রাজা সঙ্গে সঙ্গে শিশির মুখে শক্ত করে ছিপি এঁটে দিল। ছিপির ভিতর আটকা রইল প্রেত।
রাখাল রাজা শিশিটা ব্রাক্ষণের হাতে দিয়ে হাসতে হাসতে বলল— ‘যান, এই শিশিটা এবার ছুঁড়ে নদীতে ফেলে দিন। তারপর বাড়ি গিয়ে স্ত্রী আর মায়ের সাথে সুখে বাস করুন’।
এরপর ব্রাহ্মণ নিজের বাড়িতে সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগলেন। সন্তান-সন্ততিতে তাঁর সংসার পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।
“আমার কথাটি ফুরোলো
নটে গাছটি মুড়োলো।।”
হতে হতে একটা ক্ষুদ্র কীটের মতো আকার ধারণ করল। তারপর টুক করে ঢুকে গেল শিশির ভিতর। আর রাখাল রাজা সঙ্গে সঙ্গে শিশির মুখে শক্ত করে ছিপি এঁটে দিল। ছিপির ভিতর আটকা রইল প্রেত।
রাখাল রাজা শিশিটা ব্রাক্ষণের হাতে দিয়ে হাসতে হাসতে বলল— ‘যান, এই শিশিটা এবার ছুঁড়ে নদীতে ফেলে দিন। তারপর বাড়ি গিয়ে স্ত্রী আর মায়ের সাথে সুখে বাস করুন’।
এরপর ব্রাহ্মণ নিজের বাড়িতে সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগলেন। সন্তান-সন্ততিতে তাঁর সংসার পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।
“আমার কথাটি ফুরোলো
নটে গাছটি মুড়োলো।।”