গল্প

সোহম দাস
আমকাঠ
আমাদের গ্রামে সেবার গরম পড়ল প্রচণ্ড। উত্তরের পাহাড়ের দিক থেকে ঠান্ডা হাওয়া গ্রামের ঢোকার আগেই হারিয়ে যেতে লাগল। আমরা বলতাম, ওই কিলিমারা হাওয়া চুরি করছে।
আর সেই গরমের মধ্যেই গ্রামের লোকজন হঠাৎ পাগল হতে শুরু করল। কিন্তু তার কারণ গরম নয়। অন্য কিছু।
আমাদের গ্রামটা ছিল ভারি অদ্ভুত মধ্যবর্তীতে। গ্রামের উত্তর দিকে চনমন করত সবুজ, চিন্তিত পাহাড়। দক্ষিণ অংশের একদম শেষ প্রান্তে মিহির শয়তানের বাড়ি ছাড়িয়ে একটু খানি গেলেই আমরা শুনতে পেতাম এক জলদানবের নাসিকা গর্জন। পশ্চিমের দিকে ধু ধু করত মাঠ, সেখানে ঘাসের চেয়ে বালির ভাগ বেশি। কাকডাঙার মাঠ পেরিয়ে গেলেই ফুরিয়ে যেত সবুজের দেশ। হলুদ বালুভূমির প্রান্তরের শুরু। গ্রামের চাষবাস যা হত সব পুবে। একটা নদী ছিল, সেট আসত ওই পাহাড়ের কোনো এক গুহার মধ্যে থেকে। সে-নদীটার মতো একচোখা আমরা কাউকে দেখিনি। টিরির চেয়েও একচোখা। নদীটার যা তর্জন-গর্জন সব পুবের দিকে। পশ্চিমের দিকে ফিরেও তাকায়নি কখনো। আর এ-সব অদ্ভুতপানা উপদ্রবের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকত আমাদের গ্রাম।
পাহাড়ের কাছাকাছি অংশে ছিল ঘন জঙ্গল। জঙ্গলটা ছিল বিচিত্র সব বন্য জানোয়ারের সমষ্টি। ওপাশে আমরা যেতাম, কিন্তু ফিরে আসতাম সন্ধ্যে নামার আগেই। জঙ্গল থেকে মাঝে মধ্যে দু-একটা হরিণ-টরিণ বেরিয়ে আসত। আমরা তার পিছন পিছন ছুটতাম। ঢেলা, চ্যালাকাঠ, কাটারি, যা থাকত, সে-সব হাতে নিয়ে তাড়া করতাম তাকে। আর সে পায়ের গতি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দু-পেয়ে জীবের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করত। বেশিরভাগ সময়েই আমাদের চেয়ে বহুগুণ গতিতে ছুটে পালিয়ে যেত, আমাদের ধরার সাধ্যি হত না। ছুটতে ছুটতে ঢিল আর চ্যালাকাঠগুলো ছুড়তাম আমরা। সেগুলো বেশিরভাগ সময়েই লক্ষ্যভ্রষ্ট হত।
আমাদের এরকম হরিণ তাড়ার ঘটনার সঙ্গেই আরও একটা ব্যাপার ঘটত। সেটা আরও বিরক্তিকর। যে-কিলিমাদের কথা বললাম, ওরা থাকত ওই জঙ্গলের কাছেই। আমরা হরিণকে তাড়া করা শুরু করলেই কিলিমার সর্দার কিলি আর তার ছেলে টিরি আমাদের পিছন পিছন ছুটত। না, হরিণটাকে ওরা তাড়া করত না। ওরা আমাদের তাড়া করত। ‘হুইলা, হুইলা’ বলতে বলতে ছুটত। ঝাঁকড়া চুলে, খালি উদোম গায়ের লোক ওরা। সেই তারা আমাদের মতো ভদ্রঘরের ছেলেদের পিছনে এমনভাবে ছুটত, যেন আমরা চোর আর ওরা আমাদের ধরতে ছুটছে। কী বিশ্রী, অশ্রাব্য শোনাত ওদের ওই ‘হুইলা, হুইলা’ ডাক।
ওই টিরির একচোখামির উল্লেখই করছিলাম একটু আগে। টিরিরা কেউ আমাদেরকে পছন্দ করত না। আমাদের দেখলেই কেমন জানি আশ্চর্য রকমের ঘেন্না করত।
টিরিরা কেউ হরিণ মারত না। খরগোশ বা পাখি-টাখি মাঝেসাঝে মারত। আমরা দু-বার হরিণ মারায় সফল হয়েছিলাম। একবার একটা বুড়োটে হরিণ ঢুকে পড়েছিল, সে বেশিদূর দৌড়তে পারেনি। তাকে ঘিরে ধরে মারা হয়েছিল। কিন্তু সে-মাংস না ছিল তাজা, না ছিল তাতে স্বাদ। আমাদের ভালো লাগেনি। কবে একটা তাজা হরিণ দলছুট হয়ে চলে আসবে, আর তার মাংস খাব রসিয়ে রসিয়ে, এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলাম আমরা।
আমাদের পাঁচজনের একটা দল ছিল। আমরা গোটা গ্রামের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব নিজেরাই নিয়েছিলাম। কোথায় কোন বাড়ির ছেলে পাশের পাড়ার মেয়ের সঙ্গে পুকুরঘাটে বসে ছেনালি করছে কিংবা কোথায় কে বসে মোড়লের নামে বাপান্ত করছে, তাদের শায়েস্তা করার ভার নিয়েছিলাম আমরা। মোড়লের কাছে এজন্য বেশ সুনাম ছিল। আমাদের পরিবারের লোকজনও বেশ গর্ব বোধ করত। শুধু একজন ছাড়া। দাশরথির বাবা অধিরথি। সে অবশ্য গ্রামেও থাকত না। বাইরে কোথায় কাজ করত। একটা খাতায় কী-সব হিজিবিজি লিখতও। বাড়িতে এলেও এক ছাদের তলায় বাপ-ছেলেকে আমরা কোনোদিন দেখিনি। মোড়লকে বা আমাদের এইসব গর্বের কাজকে সে অবজ্ঞা করত।
হরিণ মারার সুযোগ অবশেষে এসেছিল। একখানা হৃষ্টপুষ্ট হরিণ, বেশ তাজা। আমরা তার অপেক্ষাতেই তো ছিলাম। পাঁচজনে মিলে তাড়া করলাম তাকে। মনোহরের হাতে ছিল কাটারি। হরিণটা দৌড়তে পারছিল না, হাঁপাচ্ছিল। অথচ, পেছনে ব্রহ্মাস্ত্র হাতে তাড়া করে আসছে মৃত্যুবন্ধুরা। এঁকেবেঁকেও ছুটছিল সে। কিন্তু পারল না। মনোহরের ছোড়া কাটারি গিয়ে আমূল বসে গেল তার গলায়। আচমকা আঘাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে। কাটারি বসে গেল আরও। গলা ফাঁক। আমরা উল্লাসে লাফিয়ে উঠলাম।
গোপী আর শ্যামসুন্দর কিছুক্ষণ পরেই ছুরি দিয়ে কাটতে বসল ছাল-চামড়া। আর তখনই সেই অভাবনীয় ঘটনাটা ঘটল। মনোহর চেঁচিয়ে উঠল— “একেবারে ডবল লাভ যে রে।” চেঁচানি শুনে তাকিয়ে দেখি, হরিণটার পেটে বাচ্চা, সেটারও আর প্রাণ নেই। ঠিকমতো দৌড়তে না পারার রহস্যটা এতক্ষণে পরিষ্কার হল। অল্প কষ্ট হলেও ভাবলাম, আমাদের জন্য মরেছে, পুণ্য হবে ওর।
টিরিরা সেদিন বস্তিতে ছিল না। উল, ছোনি, মাঙ্গেকরা জুলজুল করে তাকিয়ে দেখছিল হরিণ-ছাড়ানোর পর্ব। মনোহর ওদের হাতে বাচ্চা হরিণটাকে দিয়ে ভাগিয়েছিল। প্রথমে ইতস্তত করলেও ওরা সেটাকে নিয়ে চলে যায়। টিরি থাকলে এ কাজ সহজে হত না।
তারপর আমরা মাদি হরিণের মৃতদেহ নিয়ে মিছিল করতে করতে যাই মোড়লের বাড়ির ওখানে। মহাভোজ হবে।
***
অথচ, গ্রামের লোকে পাগল হতেই থাকল। কেউ কেউ সঙ্গে বোবাও হয়ে গেল। বোবা লোকজন গ্রামে থেকে গেল। আর যারা ভুলভাল বকতে থাকল, তারা চলে গেল। আর এ-সব নিয়ে ঝামেলা শুরু করল মিহির। মিহির শয়তান।
অবশ্য ওদের কাজই ছিল ঝামেলা পাকানো। ওর ছেলেটাও তাই। সে ছিল আমাদের বয়সি। ওরা ছিল টিরিদের মতোই কালো, আর মানুষ-মারা বিদ্যে-জানা লোকের বংশ। সেজন্যেই ওই ‘শয়তান’ তকমা দেওয়া হয়েছিল। না হলে এমনিতে নাকি ‘ডাক্তার’ না কী একটা বলা উচিত মিহিরকে। সেটাও ওই সতুই আমাদের বলেছিল। সেই কারণে সতুকে আমরা চারজন মিলে গ্রামের মোড়লের কাছে নাক খত দেওয়াই। মোড়ল সতুকে সাবধান করে দিয়েছিল, এ-সব কথা আর যেন সে না বলে। গোপী একবার ওদের ঘরে উঁকি মেরে দেখেছিল। গোটা দেওয়াল জুড়ে নাকি কী-সব মোটা মোটা ইটের মতো জিনিস সাজিয়ে রেখেছে। সেই থেকে আমরা আর কেউ ওদিকে যেতাম না।
মাঝে মাঝেই মিহির বাইরে থেকে নানা লোককে নিয়ে আসত। অদ্ভুতদর্শন তাদের পোশাক, পিঠের ব্যাগে কী-সব যন্ত্রপাতি থাকত। ছুঁচ-টুচ ফোটানোর জন্যে তারা আসত। আবার প্লাস্টিকের শিশি, টিনের কৌটোতে করে কী-সব লাল কিংবা হলুদ কিংবা গোলাপী রঙের তরল পদার্থ নিয়ে আসত। সঙ্গে বড়ির মতো গোল গোল জিনিস। দেখলেই ভয় লাগত। সে-সব খাওয়াতে চাইত তারা। ওগুলো খেলে নাকি রোগ-ভোগ হবে না। সাদা প্লাস্টিকের ছোট্ট একটা শিশি আনত মাঝেমধ্যেই। তার মাথায় ফুটো। তার মধ্যে কী একখানা ওষুধ ছিল, সেটা ওরা বাচ্চাদের খাওয়াতে চাইত। খাওয়ালে নাকি হাত-পা বেঁকার রোগ ধরে না। কী ভয়ের ব্যাপার সত্যিই! আমরা তাই দেখতে পেলেই ঘরে দোর দিয়ে খিল দিতাম।
আমাদের গ্রামের মোড়লের পোষা এক সন্ন্যাসী ছিল। অবতারবাবা বলতাম আমরা। আসল নামও কী একটা ছিল, মনে নেই। মোড়লের সভা হলেই সেই সন্ন্যাসী তার পাশেই বসত। মোড়লের যে-বড়ো বাগানবাড়িটা ছিল, তার লাগোয়া একটা সুন্দর বাড়িতে সে থাকত। সেই সন্ন্যাসীর কড়া হুকুম ছিল, মিহির শয়তান এ-সব লোক আনলে যেন আমরা একেবারেই তাদেরকে ঘরে ঢুকতে না দিই।
গরম পড়ার ঠিক আগে আগেই কলমিদের বাড়িতে ওর দাদু-বাপ-ঠাকুমা সব অসুস্থ হল। বাইরে কোথায় কাজ করতে গিয়েছিল ওর বাপ, সেখান থেকে ফিরেই সে অসুস্থ হল। ওরা অবতারবাবার কাছে না এসে নাকি মিহিরের কাছে গিয়েছিল। মিহির অমনি সেই অদ্ভুতপানা লোকগুলোকে আবার নিয়ে এল। কলমিরা ওদের ঢুকতে দিয়েছিল, তারপর থেকে তিনদিন পুকুরের জল ওরা ব্যবহার করতে পারেনি। তিন দিন পরে মোড়লের বাড়িতে গিয়ে সন্ন্যাসীর বানিয়ে দেওয়া এক বিশেষ ধরনের হলদেটে রঙের তরল দিয়ে ওদের স্নান করিয়ে অপরাধমুক্ত করা হয়। তারপর থেকে ওরা পুকুর ব্যবহারের অনুমতি পায়।
অবশ্য ক-দিন পরেই কলমির বাপ আর দাদু মরে গেল। ওরা নাকি পোড়াবার লোক খুঁজে পায়নি। মোড়ল বলল, পাপের শাস্তি। সত্যিই তো, মিহির শয়তানের আনা যমদূতদের দেওয়া বিষ খাওয়া তো পাপই তো বটে। অবতারবাবার পানীয় খেয়েও সেই পাপ কাটেনি। আমরা খুব ভয় পেলাম। এত বড়ো পাপ যে, অবতারবাবাও কিছু করতে পারল না। সেই থেকে আমরা আরও সাবধান হয়ে গেলাম। গ্রামের সীমানায় পাহারা বসানো হল। বাইরের লোক যাতে ঢুকতে না পারে। গাঁয়ে সমস্যা হলে তা মেটানোর জন্যে তো আমরাই আছি। খামোখা বাইরের লোক আনবারই-বা প্রয়োজন কী!
মিহিরকেও চোখে চোখে রাখবার নির্দেশ দেওয়া হল। সে ইতিমধ্যে লোকে কেন পাগল হচ্ছে, সেই নিয়ে টিকটিকিপনা শুরু করেছিল। তার গতিবিধি নজরবন্দি করে নিয়ন্ত্রণে আনার নির্দেশ এল আমাদের উপর।
***
কিন্তু মিহিরকে বেশিদিন দাবিয়ে রাখা গেল না। হঠাৎ একদিন বিচিত্র এক উপদ্রব শুরু হল।
কলমির বাপ আর দাদুর মরার পরে আরও কয়েকজন মরল, আর নয় অসুস্থ হল। মোড়লের মোটা ভ্রূ এবার অল্প কুঁচকোল। সে অবতারবাবার সঙ্গে বৈঠক করল। সে-বৈঠকে কী হল, আমরা জানতে পারিনি অবশ্য। তারপরেই শুনলাম, আমাদের লম্বা ছুটি। আমাদের মানে গ্রামের লোকদের। আমাদের পাঁচজনের তো আর ছুটি নেওয়ার উপায় ছিল না। কত দায়িত্ব আমাদের। এবার আমাদের বাড়তি দায়িত্ব এসে পড়ল, লোকজনকে রাস্তায় দেখলেই বেতের ঘা দিতে।
শুনলাম, ছুটি না নিলেই নাকি শরীর খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মোড়লের খাস লোক চাটুয়ার কথায় হেসেছিলাম। শরীর খারাপ হবে, এতে আবার বিচলিত হওয়ার কী আছে! অবতারবাবার দেওয়া ওষুধ পেটে পড়লে যমের অসুখও সেরে যায়, এ-কথা তো মোড়লই আমাদের বলেছিল। মোড়লের অনুচর চাটুয়াকে সেকথা মনোহর বলল। কিন্তু চাটুয়া একটা অদ্ভুত কথা বলে বসল। মোড়ল নাকি নিজেও এবার একটু ভয়ে আছে। ভয়ে আছে অবতারবাবাও।
এটা ঠিক যে, আমরা চাটুয়ার কথা শুনে বেশ চমকেছিলাম। এবার তার মানে গপ্পো বেশ জোরালো। তাও আমরা চাটুয়াকে এই কথাটা বেশ জোরের সঙ্গে জানিয়েছিলাম যে, যাই হয়ে যাক, অবতারবাবার ওপর আমাদের যথেষ্ট ভরসা আছে। চাটুয়া বোধহয় এই কথাটার অপেক্ষাতেই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বলল— “আরে সে কি আর বলতে! তোমরা আছো বলেই তো ভরসা।” তারপর খানিক মুখ নীচু করে (মুখের কাছে মুখ এনে নয়, ওটাও বারণ করেছিল চাটুয়া) বলেছিল— “এ-সবকে কাজে লাগিয়ে মিহির কিন্তু আবার ঝামেলা পাকাতে পারে। আবার ওই বাইরে থেকে লোকজন আনতে পারে। খুব সাবধান। তোমরা একটু ব্যাপারটা দেখ।”
এটা আমরা ভেবে দেখিনি। সত্যিই তো! মিহির তো এরকম তালই খোঁজে। মনোহর চাটুয়ার কাঁধ ঝাঁকিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, চাটুয়া খানিক তফাতে সরে গিয়ে বলল— “উঁহু, উঁহু, ওইটি করো না। দূর থেকে বলো, যা বলার।”
মনোহর অতঃপর দূর থেকেই বলল— “ঘাবড়াও মত। আমরা আছি। ও শালা মিহিরকে নির্বংশ করে দেব ঝামেলা বাধাতে এলে।”
চাটুয়া বেশ খুশি হয়ে আবার ঢ্যাড়া পেটাতে চলে গেল।
কিন্তু মিহিরকে সত্যিই বেশিদিন দাবিয়ে রাখা গেল না।
***
চাটুয়ার ঘোষণার ঠিক দিন তিনেক পরের ঘটনা। এর মধ্যে আরও কয়েকজন মরল, হয়তো অসুস্থও হল। সব খবর আমরা রাখতাম না। আর, আরও কয়েকজন পাগলও হল। বিশেষত, যারা নদীর দিকে থাকত। এর আগে যারা পাগল হয়েছিল, তাদের কেউ আমরা চিনতাম না। এত বড়ো গাঁ, সেখানের সব লোককে চিনবই-বা কীভাবে! কিন্তু এবার দু-একজন চেনা লোকের নাম শোনা গেল। ওই কিলিমা বস্তির উলের দাদু পাগল হল, মাঙ্গেকের এক কাকা। সকলেই নাকি নদীর ধারে সকালে পায়খানায় গিয়ে পাগল হয়েছে। আমাদের কেউ পাগল হলে অবতারবাবার কাছে নিয়ে যাওয়া যেত, কিন্তু ওদের জন্য সে-সবের অনুমতি ছিল না। আমরা অবশ্য বেশ নিশ্চিন্তই ছিলাম। আমাদের কেউ পাগল হয়নি।
কিন্তু নিশ্চিন্ত বেশিদিন থাকা গেল না। পাগলদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকল। সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে অসুস্থ হওয়ার সংখ্যাও। দক্ষিণে যেদিকে সেই জলদানবের আস্ফালন, সেদিকেও অনেকে অসুস্থ হল। পশ্চিমে যেখানে খুব বেশি জল পাওয়া যেত না, সেখানেও লোকে এই অসুখের কবলে পড়তে থাকল। গতিক যে খুব সুবিধের নয়, সেটা আমরাও বেশ বুঝতে পারছিলাম। তবু আমাদের ভরসা ছিল, মোড়ল আছে। অবতারবাবা আছে।
অবশেষে যে-ঝামেলা লাগার, সেটা লাগল। আবারও সেই মিহির। সে জেদের সঙ্গে ঘোষণা করল, এবার যদি কেউ এদের কথা না শোনে, বা ওর কথা না শোনে, তবে সকলের কপালে বিপদ নাচছে। ওই অবতারবাবার হলদেটে জলে যে কিচ্ছু হবে না, উলটে ক্ষতি হবে, সে-কথা সে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল। আমরা ভাবলাম, কী আস্পর্ধা রে বাবা! অবতারবাবাকে একেবারে সরাসরি চ্যালেঞ্জ!
একদিন বেলা এগারোটায় গোটা গ্রাম জুড়ে হুলুস্থূল। অবশ্য মূল ঝামেলাটা হচ্ছিল গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব সীমানায়। যে-পাহারাদারদের বসানো হয়েছিল, তাদের সঙ্গে সেই লোকগুলোর প্রবল কথা-কাটাকাটি। আর লোকগুলোর হয়ে তড়পাচ্ছিল মিহির। সঙ্গে ওর ছেলে সতু, আর আরও অনেকে। বাইরের লোকগুলো অবশ্য খানিক বোঝানোর ভঙ্গিতেই বলছিল। কী-সব নাকি পরিষ্কার করবে আর শরীরে ছুঁচ ফোটাবে। এতে আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না, উলটে লাভই হবে। কী সাংঘাতিক ব্যাপার।
খবর গেল মোড়লের বাড়িতে। মোড়ল নিজে বেরোল না, সে তখন নিজের নতুন বাড়ি তৈরি নিয়ে খুব ব্যস্ত। ঝাঁ চকচকে বাড়িটা বানাচ্ছিল বিরাট করে। সেটা নিয়ে সে খুবই ব্যস্ত তখন। এর মধ্যে এ-সব ঝামেলা কারই-বা ভালো লাগে! তাই সে আরও কিছু লোক পাঠাল। তাদের সঙ্গে আমরাও গেলাম। মনোহর বীরদর্পে ঘোষণা করল— “সেদিন চাটুয়াকে যে-কথা দিয়েছি, আজ সেই কথা আমি রাখবই। ও শালা মিহিরকে ঝাড়ে-বংশে খতম করব।”
ঝামেলার জায়গায় পৌঁছে আমরা দেখলাম, লোকে-লোকে ছয়লাপ। চাটুয়া ঢেঁড়া পিটিয়ে যে-কথা বলে গিয়েছিল, তার সিকিভাগও মানা হচ্ছে না। মিহির সমানে ওই লোকগুলোকে ঢোকাবার চেষ্টা করছে, আর তাকে রক্ষীরা বাধা দিচ্ছে। মিহিরের পাশে সতু ছাড়া আমরা টিরি, ছোনিদেরও দেখলাম। আমরা কাজে লেগে পড়লাম। লোকজনকে সরাতে লাগলাম। মোড়লের খাস লোকজনদের দেখে অনেকেই কেটে পড়ল। অত লোকের ব্যূহ ভেদ করে শ্যাম আর মনোহর একেবারে বাইরের অদ্ভুতদর্শন লোকগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মনোহর আগেই মিহিরকে এক ঝটকায় সামনে থেকে সরিয়ে এনে হাতের মোটা লাঠিটা দিয়ে গলাটা চেপে ধরল। রোগাপাতলা মিহিরের নড়াচড়ার ক্ষমতা থাকল না। সতু তার বাপকে সাহায্য করতে মনোহরের হাতের লাঠিটা কেড়ে নিতে চেয়েছিল, তাকে ধরল গোপী। বাকিদের আমরা শায়েস্তা করলাম। টিরিদের জন্য পাহারাদারেরাই উপযুক্ত ছিল, ওদের সঙ্গে আমরা পেরে উঠতাম না। যমদূতের মত দেখতে লোকগুলো আমাদের দেখে বুঝি যমের মতোই ভয় পেয়ে গেল। এতক্ষণ পাহারাদারদের সঙ্গে যেভাবে কথা বলছিল, সেই আওয়াজ মিইয়ে এল। শ্যামের মাথা চিরকালই ঠান্ডা। সে এতক্ষণ নিজে কাউকে আঘাত করেনি। মনোহরের মতো অত মাথা গরম করে না। গম্ভীর গলায় লোকগুলোকে প্রশ্ন করল— “কী ব্যাপার?”
সাদা পোশাকের একজন বলল— “আমরা রোগ সারাতে এসেছি তোমাদের গ্রামে। এই গ্রামে অনেকে অসুস্থ হচ্ছে। আমরা এসেছি, যাতে তোমাদের আর রোগ না হয়। আমাদের কথা শোনো, আমরা খারাপ লোক নই।”
শ্যাম বলল— “কেউ তো আসতে বলেনি তোমাদের।”
লোকটা মিহিরের দিকে দেখিয়ে বলল— “ও বলেছে তো। আমরা তো ওকে অনেকদিন ধরে চিনি। ওকে বিশ্বাস করেই এসেছি।”
— “ওর কথায় চলে এলে? মোড়ল না বললে গ্রামে ঢোকার নিয়ম নেই। ফিরে যাও।”
— “কিন্তু আমাদের কাছে যে অনুমতিপত্র আছে। বড়োসাহেব নিজে দিয়েছেন।”
— “তোমাদের বড়োসাহেবকে বলো, আমাদের মোড়লসাহেবের সঙ্গে কথা বলতে। তিনি অনুমতি দিলে, তবে হবে। আমাদের অবতারবাবা আছে, তোমাদের দরকার নেই এখানে।”
— “কিন্তু এই গ্রামে তো অনেকে মরছে, সে-খবর আমাদের কাছে আছে।”
— “কে দিয়েছে সে-খবর? এটাও কি মিহিরের কীত্তি?”
— “না, সে খবর আমরা পেয়েছি নদীর কাছ থেকে।”
— “নদী? সে কে?”
— “নদীকে চেনো না? যেখানে তোমরা রোজকার কাজ সারতে যাও।”
— “আমরা যাই না। আমরা ভদ্দরলোক, আমাদের বাড়িতেই কাজ করার ব্যবস্থা আছে। ওখানে যায় ছোটোলোকরা।”
— “সে যাইহোক। আমরা খবর নদীর কাছ থেকেই পেয়েছি। আর খবরটা সত্যি। নদী কখনো মিথ্যে কথা বলে না।”
লোকটার এমন ধোঁয়াটে মার্কা কথায় আরও পিত্তি জ্বলে গেল। একে চারিদিকে একটা যুদ্ধ-যুদ্ধ ভাব। লড়াই হতে বেশি দেরি নেই, তার মধ্যে এ-সব ধ্যাষ্টামো আর কারই-বা ভালো লাগে! অমন মাথা-ঠান্ডা যে, শ্যাম, সেও অসহিষ্ণু হয়ে পড়ল। গলা তুলে বলল— “এই এ-সব ছেঁদো কথা রাখো তো। আজেবাজে বকে আমাদের ভুলিয়ে দেওয়ার তাল, আমরা কিছু বুঝি না নাকি? শালা নদী কি তোমার বাপের চাকর যে সে কথা বলবে। এখানে আমাদের কেউ মরেনি। ও-সব নদী-ফদী বাজে কথা। আমরা জানি, মিহিরই তোমাদের বলেছে।”
মিহিরের দিকে তাকালাম সকলে। সে মনোহরের নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, মনোহর তার গলা এমনভাবে চেপে ধরেছে, অস্ফুট কিছু আওয়াজ ছাড়া কিছুই বেরোচ্ছে না। লোকটা বুঝল, ঝামেলা আছে। তাও শেষ চেষ্টা হিসেবে বলল— “এবার আমাদের কাজ করতে দাও ভাই। এ-সব ওই অবতারবাবা-টাবাকে দিয়ে হবে না। এ-রোগ যে সে রোগ নয়, একেবারে মহাকালের ব্যাপার। নইলে বড়ো বিপদ হয়ে যাবে।”
এই বলে তারা জোর করেই ঢুকে পড়তে চাইল। শ্যাম তার বলশালী হাত দিয়ে যে-লোকটা এতক্ষণ কথা বলছিল, তাকে এক ধাক্কা মারল, লোকটা ব্যাগ-সমেত ছিটকে পড়ল। বাকি লোকগুলো এই আক্রমণের সামনে প্রথমে কিছুক্ষণ হকচকিয়ে গেলেও পরে তারাও আক্রমণ করতে এগিয়ে এল। শেষপর্যন্ত খণ্ডযুদ্ধ বেধেই গেল। ইতিমধ্যে আরও লোক জড়ো হয়েছিল। কেউ কেউ ফিরে গেলেও তামাশাটা পুরোটা দেখার লোভ ছাড়তে পারেনি। কে যে কাদের দলে, বোঝা মুশকিল। পাহারাদাররাও এতক্ষণ খুব একটা হাতের সুখ করতে পারছিল না। এবার তারাও যোগ দিল।
মুহুর্মুহু লাঠি চলল শুধু। দলে ভারী ছিলাম আমরাই, আমাদের অস্ত্রও কম নয়। সাদা বিচিত্র পোশাকের লোকগুলো হাতের জিনিসগুলো দিয়েই খানিক প্রতিরোধের চেষ্টা করল। মূর্খের দল। লাঠির সামনে বিশেষ সুবিধা করতে পারল না। তাদের মেরে হাড় ভেঙে দেওয়া হল। মনোহর দু-জন লোকের মাথা ফাটিয়ে দিল। কিন্তু বাইরের লোক বলেই আর অন্য কিছু করা হল না। চলে যেতে বলা হল। ওরাও ভাবেনি, এমন মার খেতে হতে পারে। কিন্তু মোড়লের এলাকায় এ-সব নাকগলানো বরদাস্ত করা হয় না, কোনোদিনই। ওদেরকে সে-সব বুঝিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হল।
কিন্তু মিহিরকে ছাড়ার কোনো প্রশ্নই নেই। মনোহর তো ঠিক করেই ছিল, মিহিরের বংশ শেষ করবে। মিহির ততক্ষণে ধুঁকছে। মুখ দিয়ে লালা-রক্ত মিশ্রিত একটা তরল বেরিয়ে আসছে। সতুরও অবস্থা তদনুরূপ। কিন্তু মোড়লের কড়া নির্দেশ ছিল, ঝামেলা মিটলে মিহিরকে তার কাছে নিয়ে আসতে হবে। সেই নির্দেশমতো মিহিরকে, সতুকে, এবং ওদের বাড়ির সকলকে বেঁধে ঘষটাতে ঘষটাতে নিয়ে যাওয়া হল। সঙ্গে টিরিদেরও। গ্রামদ্রোহীতার শাস্তি। অবশ্য ব্যাপারটা শুনতে যতটা চুপচাপ মনে হচ্ছে, ততটা চুপচাপ ছিল না মিহির বা টিরিরা কেউই। মোড়লের বাড়ির দিকে যখন ওদের হাঁটু ছেঁচতে ছেঁচতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তপ্ত গরমে খোয়াভরতি রাস্তায় ছিলে যাওয়া রক্তাক্ত হাঁটুতে লাল দাগ হয়ে যাচ্ছে, ওরা চেঁচাচ্ছিল। সঙ্গে স্লোগান— “যত খুশি মার আমাদের। যত খুশি রক্ত বার কর। এভাবে সত্যি চাপা যাবে না। সব বেরোবে একদিন। নদীর দিকে গেলেই সকলে কেন পাগল হচ্ছে, আমরা কি জানি না? ভোররাতে ওখানে কী হচ্ছে, আমরা কি দেখিনি?”
কোন সত্যির কথা যে বলছিল, নদী, ভোররাত, এ-সবের মাথামুণ্ডু কিছুই আমরা বুঝলাম না। আমরা বুঝছিলাম, মিহিররাও সব পাগল হতে শুরু করেছে। গ্রামের পাগল হওয়ার ছোঁয়াচ রোগ ওদেরকেও ধরেছে।
কিন্তু ওদের স্লোগান দিলে আমাদেরও তো দিতে হয়। আমরা এক দঙ্গল লোক আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করলাম— “অবতারবাবা জিন্দাবাদ।” আমাদের হাঁকডাকে বাড়ির উঠোনে, ছাতে, গেটের সামনে মেয়ে-বউ-বুড়ো-বাচ্চা-জোয়ান, যত ধরনের দু-পেয়ে জানোয়ার হয়, সব বেরিয়ে এল। স্লোগানের অসম প্রতিযোগিতা দেখতে তারাও দাঁড়িয়ে গেল। মোড়লবাড়ির দিকে এগোতে থাকল আমাদের শোভাযাত্রা।
***
সেদিনের পর আর মাত্র তিন দিন মিহিরকে দেখা গিয়েছিল। ওই তিন দিন ধরে বিচারপ্রক্রিয়া চলে।
মিহিরও যে পাগল হয়েছিল, সেই ব্যাপারে আমরা সকলেই বদ্ধমূল ছিলাম। মোড়লের উঠোনে ওদের বিচার হয়েছিল। মোড়লের নীতিকে অবজ্ঞা করা, বাইরের লোক ঢুকিয়ে মোড়লের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, শান্ত-নিরীহ লোককে খেপিয়ে তোলা, সর্বোপরি মানুষের ক্ষতি করতে চাওয়া, এমন কঠিন সব কারণ চাপানো হয়েছিল মিহিরের ওপর। মূল অভিযুক্ত সে ও তার পরিবার। টিরিরা যেহেতু তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, তাই তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কম। কিন্তু শাস্তি সকলেরই। টিরিদের পাহাড়ের জঙ্গলে নির্বাসন দেওয়া হল। শাস্তি, রোজ হরিণ মেরে খেতে হবে। মিহিরদের শাস্তি আরও গুরুতর। একে এত প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়েছে, উপরন্তু মস্তিষ্কবিকৃতি। অপরাধের ওপর অপরাধ। অবতারবাবা বিধান দিল। কোথাও তাদের পাঠানো হবে, সেখানেই আজীবন থাকতে হবে। কোথায়, তা আর আমাদের জানতে দেওয়া হল না। সেটা রুদ্ধবেড়া বৈঠকে স্থির করা হয়। সেখানে আমাদের প্রবেশাধিকার ছিল না।
কয়েকদিন পরেই আমরা খবর পেলাম, মিহিরের নাকি ওই রোগটা হয়েছিল, তাতেই সে টেঁসে গেছে। আমাদের মোড়লের বড়ো চওড়া হৃদয়, তাই সে যারপরনাই চেষ্টা করেছিল মিহিরকে যথোপযুক্ত চিকিৎসা করাতে। কিন্তু মিহিরের এমনই জেদ যে, অবতারবাবার ওষুধ তাকে খাওয়ানো যায়নি। মিহির উবে যেতে আমরা খুবই খুশি হয়েছিলাম, বলাই বাহুল্য। ও ছিল একটা আপদ। এমন আপদ গ্রামে না থাকাই ভালো। তার উপর পাগল হয়ে গিয়েছিল। আরও সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটতে পারত। আমাদের ভাগ্য ভালো, ও নিজেই ঝামেলা ডেকে এনে আমাদের সুবিধা করে দিল। তবে মনে মনে কিছুটা খারাপও লাগছিল এই ভেবে যে, তাকে আমরা সেভাবে ঠিক উচিত শিক্ষাটা দিতে পারলাম না। আমাদের ইচ্ছে ছিল, তাকে গোটা গ্রাম যদি মাথা মুড়িয়ে, উলঙ্গ করে ঘোরানো যায়। কিন্তু মোড়লের নির্দেশ ছিল, ওরকম কাজ করে ছোটোলোকেরা, আমরা ভদ্দরলোক বলে ও-সব করা যাবে না। সেই কথাই ক-দিন পরে মনোহর বলল— “আহা রে, বেচারা লোকটা ফালতু ফালতু আমাদের সঙ্গে বিলা দিতে এসে নিজেই পাগল হয়ে গেল। নির্বংশ করব বলেছিলাম, কিন্তু বেশ কষ্টই লাগছে মাইরি।”
গ্রামের পাহারা শেষ করে আমরা একপ্রান্তে বসে গুলতানি মারছিলাম। সকলের এখন বাড়িতে থাকার নিয়ম। আমরা অবশ্য যেখানে খুশি ঘুরতে পারি, কেউ আটকাবে না। হঠাৎ শুনি, দাশরথির নাম ধরে কেউ ডাকছে। মহিলার গলা। দাশরথি তাকিয়ে দেখে, তার মা আর ঠাকুমা। সে একটু অবাক হয়েই তার মা-কে জিজ্ঞাসা করল, কারণখানা কী? তার মা বলল— “তোর বাপ পাগল হয়ে গেছে, দাশু। বাড়িতে আয়।”
দাশরথির সঙ্গে তার বাপের বনিবনা ছিল না। তাই দাশুকে খুব একটা চিন্তিত লাগেনি। কিন্তু মায়ের জোরাজুরিতে সে বাড়ি ফিরে গেল। যাবার আগে আমি তাকে বললাম— “বাড়িতে একটা খবর দিয়ে যাস, দাশু, কেসটা কী।” আমরাও ব্যাপারটা শুনে অবাক হলাম। কিন্তু দাশুর কাছ থেকে ছাড়া আর কারও কাছ থেকে জানতে পারার উপায় নেই। আমরা সকলে যে-যার বাড়ি ফিরে গেলাম।
সেদিনই দুপুরে দাশু আমার বাড়ি এল। ওর বাবার খবর জানতে চাইলাম। দাশু খুব একচোট হাসল। ওর বাবা নাকি ভোরে নদীর ধারে পায়খানায় গিয়েছিল। দাশুদের বাড়িতে বাঁধানো বাথরুম আছে, কিন্তু ওর বাবা তো বাড়ির থেকে আলাদা। অতএব, সে নদীতেই যায়। তখন নাকি ওর বাবা দেখেছে, মোড়লের লোকজন নদীতে লাশ ভাসাচ্ছে। একটা নয়, অনেকগুলো, প্রায় দশ-বারোটা লাশ। বাচ্চার লাশও আছে। কিন্তু পুরো মুড়ে রাখা বলে সেগুলো কাদের, তা বোঝার উপায় নেই। সে-কাজ তদারকি করছে চাটুয়া। দাশু এ-সব কথা শুনেই বুঝেছে, বাপের মাথা পুরো বিগড়েছে। “মাইরি, মোড়লসাহেবের শক্তিটা ভাব। ওকে যে-ই বিলা দিতে আসুক, সে মাইরি এমন টেরে যাচ্ছে।”
কথাটা খুব ভুল বলেনি, ঠিকই তাই, মিহিরেরও এক পরিণতি হল। সে যে কোথায়, আমরা কেউ জানি না। দাশুর বাপটারও না এই পরিণতি হয়। আমি বললাম— “বাপটাকে সামলে রাখ। এ-সব বললে গাঁয়ে টেঁকা যাবে না, সে-কথা বোঝা।”
— “আরে সে-মাল কি আর বোঝাবার পর্যায়ে আছে। সে তো পুরো ঢিলা হয়ে গেছে।”
— “তবু তোর বাপ তো।”
— “আরে অমন বাপের মুখে মুতি। দু-পয়সার মুরোদ নেই, এদিকে শালা তেজ। এখন মরুক গে।”
***
দাশুর বাবাকে আর কিছু করা যায়নি। সে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেল। দাশু বাপকে পছন্দ না করলেও লাথি-ঝাঁটা মেরে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যে, এ-সব বললে কপালে দুঃখ আছে। কিন্তু সে বার বার বলতে থাকে, নদীতে সে কী দেখেছে, সব কথা সে গ্রামে রাষ্ট্র করে দেবে। দাশু তার মুখ চেপে ধরেছিল, কিন্তু সে দাশুর আঙুলে কামড়ে দাঁত বসিয়ে দেয়। দাশু রেগে গিয়ে তার বাপকে থাপ্পড় মারে। আমাদের বলে— “আর কিছু করার নেই। মালটা পুরো কুত্তা হয়ে গেছে। খ্যাপা কুত্তা। এমন কুত্তাকে বাড়িতে রাখলে বিপদ।”
দু-দিন ধরে এমন বাওয়াল চলার পর মোড়লের লোক এসে অধিরথিকে নিয়ে যায়। তার মনুষ্যবাসের শেষ দিনগুলোর ধ্বস্তাধ্বস্তির সাক্ষী হিসেবে পড়ে থাকে ঘূণ ধরা কাঠের বিছানা, ছেঁড়া এলোমেলো কাগজে লেখা হিজিবিজি অক্ষর, আর ভিজে যাওয়া দুর্গন্ধময় বালিশ আর চাদর। শেষ তিন-চার দিন সে নদীতে যেত না, পেচ্ছাপ-পায়খানা খাটেই করে ফেলত। তার কাগজগুলো সে খেয়ে ফেলতে লেগেছিল। মোড়লের লোক সেটা করতে দেয়নি। কয়েকটা টুকরো এদিক-ওদিক ছড়িয়েছিল। আমাদের মধ্যে গোপী কিছুটা লেখাপড়া জানত। সে পড়ে বলেছিল— “ধুর, সব পাগলের বাতেলা। নদীতে লাশ ভাসছে, সেই লাশের খবর পেয়ে যাচ্ছে বাইরের গ্রামের লোক, মিহিরকে নাকি গুমখুন করা হয়েছে, আসলে রোগ-ফোগ হয়নি— এ-সব গপ্পো শালা কোত্থেকে পায় মাইরি!”
দাশুর বাবাকেও আর তারপর থেকে আমরা দেখিনি। তবে দাশুর কথায় আমাদেরও খানিক কৌতূহল হয়েছিল। সত্যিই নদীর ধারে ভোররাতে কিছু হচ্ছে কিনা, একবার দেখলে হয়। ক্ষতি কী? আমাদের তো অবতারবাবা আছেই। এ-কথা আমিই প্রথম তুলি। বাকিদেরও দেখলাম, কৌতূহল আছে ভালোই। দাশুও বলল— “হ্যাঁ, চল তো, দেখেই আসি। বাপটার কথা ভেবে মায়াও লাগে। সত্যিই কিছু হচ্ছে কিনা, একবার দেখে আসাই যায়।”
সেইমতো আমরা গিয়েছিলাম। একদিন ভোররাতে। গিয়ে দেখলাম, দাশুর বাবার কথা কিছুটা সত্যি। মোড়লের লোকজন সত্যিই ছিল। সঙ্গে লাঠি নিয়ে চাটুয়া। চেনা লোক দেখে চাটুয়া হাসল— “এখানে এই সময়ে কী ব্যাপার ভাই?”
মনোহর বলল— “এই এলাম। আজ একটু ভোর ভোর বেড়াতে বেরোতে ইচ্ছা করল। তা এখানে কী হচ্ছে গো?’
চাটুয়া উত্তর দিল— “এই আমকাঠের গুঁড়ি ভাসাচ্ছি। রোজই ভাসানো হয়। জানোই তো, আমকাঠের গুঁড়ি ভাসালে রোগ-ভোগ কম হয়। অবতারবাবারই দাওয়াই। তা এই নিয়েই দেখ না, লোকজন কী-সব রটিয়ে বসল। এই তো তোমার বাবাই কী কাণ্ডটাই না করল।”
শেষ কথাটা সে দাশুর উদ্দেশ্যে বলেছিল। দাশু জিভ কেটে বলল – ‘আরে, কী আর করব বলো। আমার বাপটা চিরকালই ওরকম। বেশি তেজ দেখানো স্বভাব চিরকালই। আমাদের সঙ্গে থাকতও না। তাও তো নেহাত বাপ বলে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তা আর হল কই। ও যাক গে, ওকে আমার বাপ বলতে এমনিও ঘেন্না হত।”
আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম ওদের কাজ। আমকাঠ ভাসাচ্ছে ওরা। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আর ক-দিন পরেই হয়তো রোগ বাপ-বাপ বলে পালাবে। মনোহর দাশুর দিকে চেয়ে ব্যঙ্গ করল— “শালা তোর বাপের মাথা খারাপ জানতাম। চোখও যে খারাপ জানতাম না তো। আমকাঠকে বেমালুম লাশ বানিয়ে দিল মাইরি। আজিব আদমি।’
আমরা সকলেই হেসে উঠলাম। প্রাথমিক হকচকানির পর দাশুও হেসে উঠল। তারপরেই সে একটা অদ্ভুত কথা বলল— “মিহির-সতুরা থাকলে ওরাও শালা এগুলোকে মানুষের লাশই বলত। আমাদের অত বড় শ্মশান থাকতে নাকি নদীতে লাশ ভাসাবে। বিলা দেওয়া আর কাকে বলে!”
সত্যি বেচারা মিহির। বেশি বাওয়াল দিতে এসে নিজের জীবনটাকেই চুকিয়ে দিল। অবতারবাবার কথামতো চললে, মোড়লের কথা শুনলে রাজার হালে থাকত। ফালতু ঝামেলা করে নিজেই কোথায় হারিয়ে গেল। ওর কথা মনে পড়তে নিজেদের অজান্তেই চুকচুক করে উঠলাম আমরা। আর ঠিক সেই সময়ে সামান্য কিছু মুহূর্তের জন্য যেন দেখলাম, আমকাঠগুলোর শরীর থেকে ঝুলে এসেছে হাত, নীচের দিকে গজিয়েছে পা, মুখগুলো ঢাকা চাদরে।
পরমুহূর্তেই বুঝলাম, দৃষ্টিভ্রম। ওই তো আমকাঠগুলো ভেসে চলেছে দূর পানে।




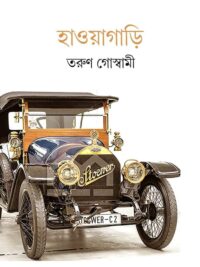





Facebook Comments