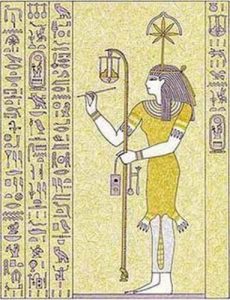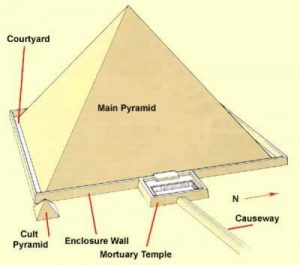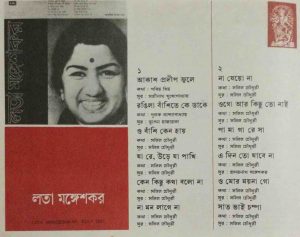প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আশ্চর্য সমন্বয় মাইহার ব্যান্ড
‘মালকোষ’ বা ‘কাফি’ আমাদের জানা বা শোনা রাগ। কিন্তু ‘মালকোষ’ কিংবা ‘কাফি’ কতটা ওয়েস্টার্ন? কী এবং কেন? আপাত দৃষ্টিতে যা সোনার পাথরবাটি, সেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শাস্ত্রীয় সংগীতরসের মূল বার্তায় ঐক্য খুঁজে পেয়েছিলেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। বলা যায়, সৃজনী ইমপ্রোভাইজেশনে নিজস্ব ভাবনায় রাঙিয়ে নিতে পেরেছিলেন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মেলোডি এবং হার্মনিকে। তাই ‘কাফি ওয়েস্টার্ন’ ‘ভল্গা ধুন’— রাগ-রাগিণীর এমন আপাত অশাস্ত্রীয় নামকরণ আজও উৎসাহীর অনিঃশেষ কৌতূহলের কারণ।
গেল শতকের গোড়ার ঘটনা। মাইহারের রাজা ব্রিজনাথ সিং ডেকে পাঠালেন ওঁর সভা-গায়ক এবং গুরু ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ-কে। মাইহারের সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষে দেশ ছেড়েছেন অনেকে। বাস্তুহারা, পরিচয়হীন কতিপয় শিশু শুধু অনাদরে অনাথ অবস্থায় এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। তাদের দেখবার কেউ নেই। রাজার অনুরোধ, সুর শেখাতে হবে এদের। মানে, নাড়া বাঁধিয়ে জবরদস্তি গানবাজনার পাঠ। জুটে গেল আঠাশটি ছেলে। নিতান্তই কিশোর সব। সংগীত কী এবং কেন, সেটাই জানা নেই অনেকের। ওঁদের বাবা হলেন আলাউদ্দিন। কী যে খেয়াল মাথায় চেপে গেল ওঁর। প্রথমে কোলে বসিয়ে, হাতে ধরে যন্ত্রের প্রাথমিক পাঠ। তারপরে সকলকে একসঙ্গে নিয়ে বাজানো। দলের নামও হল জবরদস্ত। ‘মাইহার ব্যান্ড’। মাইহার ব্যান্ড— এ আবার কী নাম? দুই শব্দের জোড়টি যেন কেমন অসঙ্গত। এ নিয়ে নানা প্রশ্নের সামনেও পড়তে হয়েছে আলাউদ্দিনকে। একবার বলেছিলেন তিমিরবরণ— ‘আসলে, বাবার চিন্তা ছিল একদম আলাদা। অতটুকু সব দামাল ছেলে, লেখা জানে না, পড়া জানে না, তাদের ধরে বেঁধে যদি শুদ্ধ শাস্ত্রীয় গান-বাজনার পাঠ দেওয়া হয়, সে-জবরদস্তি কি তারা শুনবে? বাবা ভাবলেন তাই অন্য পথে। শ্যামও থাকুক, কূলও। সিম্ফনি অর্কেস্ট্রার ধাঁচে মাইহার ব্যান্ড। আলাপের দিকটা একদম বাদ গেল। উনি মন দিলেন তালের এক-একটি পকড় ধরে সুর রচনায়। ছোটোদের মনের উপযোগী করে শেখাতেন। খুব ভালো বুঝতেন তাদের চাহিদা। প্রথমে বন্দিশটি গলায় তুলে দেওয়া। সকলকেই গাইতে হবে, বাধ্যতামূলকভাবে। সে এক দেখার জিনিস। গলায় উঠলে পরে যন্ত্রের পাঠ। এবং সেখানেই ওঁর দূরদৃষ্টির পরিচয়। সকলকেই সব বাজনা বাজাতে হত। রিহার্সালের সময় সকাল আটটা থেকে। এখনও সে-রেওয়াজ আছে বলে শুনেছি’। শুধু বাজনাই নয়, মাইহার ব্যান্ডের গোড়ার পর্বে গানের ভূমিকাও ছিল। স্বর-সাধনা করতেন আটজন, পাঁচজন হাতে ধরতেন সরোদ, সেতারেও পাঁচজন, একটি করে বাঁশি এবং সানাই, তিনটি তবলা, একজোড়া বেহালা। চেলো, ক্ল্যারিওনেট, স্যাক্সোফোন, ইত্যাদি সবই একটি করে। একটা ব্যাপার আপাত দৃষ্টিতে পরিষ্কার। দু-একটি পাশ্চাত্য যন্ত্র, এমনকী কণ্ঠ ব্যবহারের যে-নিরীক্ষা আলাউদ্দিন করেছিলেন, তা কিন্তু ব্যান্ডের সনাতন ধারণার বিপরীতেই যায়। ধীরে ধীরে অবশ্য সে-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। আজকের ব্যান্ড, দল হিসেবে অনেক সংহত, ছোটোও। সেখানে কণ্ঠের ব্যবহার নেই, অনুপস্থিত অত্যাধুনিক পাশ্চাত্যের যন্ত্রও। এবং সবচাইতে বড়ো কথা, যন্ত্রগুলি সবই প্রায় তার-যন্ত্র। এই অবস্থা অবশ্য একদিনে আসেনি। কয়েক দশকের অবিরাম ও সৃষ্টিশীল চিন্তাভাবনার ফসল তা।
একটু পিছনে ফেরা যাক। ১৯২৬-এ লখনৌর ভাতখণ্ডে সংগীত মহাবিদ্যালয়ে বসল ব্যান্ডের প্রথম আসর। আঠাশটি দুরন্ত বালক তখন রীতিমতো তুখোড় বাজিয়ে। তাঁদের দিয়ে অসাধ্য সাধন করেছেন বাবা আলাউদ্দিন। এক-আধ ঘণ্টার কম্পোজিশন মনে রাখতে তাঁদের না দরকার হয় কোনো কন্ডাকটারের, না স্ট্যান্ডে ঝোলানো নোটেশন-বোর্ডের। কাজে কাজেই সংগীতচর্চা স্মৃতিনির্ভর। অধিকাংশেরই অক্ষরজ্ঞান হয়নি। এইভাবে সাত-আট বছর ধরে চলল ঘষামাজা। তারপর একদিন আলাউদ্দিন সকলকে নিয়ে সটান কলকাতায়। ১৯৩৪-এর সেই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অতঃপর দীর্ঘ বিরতি। ব্যাঙ্গালোর, দিল্লী, বোম্বাই, সার্ক সম্মেলন— হাতে গোনা কয়েকটি অনুষ্ঠানে কেবল অংশগ্রহণ। বাকি ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন অধ্যাবসায়ের।

আর তাই, পাঁচ বছর ‘মদিনা মঞ্জরী’-র ঘরে বাবা আলাউদ্দিনের কাছে শিক্ষাগ্রহণ শেষে কলকাতায় ফিরে তিমিরবরণ সেই আদর্শেই তৈরি করলেন ওঁর ‘ফ্যামিলি অর্কেস্ট্রা’। অমিয়কান্তি, শিবব্রত, ললিতা, সবিতা প্রমুখ ভাইপো-ভাইঝি, ভাগ্নে-ভাগ্নী সমাবেশে তিমিরবরণের পারিবারিক অর্কেস্ট্রা সমাদৃত হয় সারা ভারতবর্ষে। উৎসাহিত হন স্বয়ং উদয় শংকরও। কিন্তু, সে-অন্য কাহিনি। বাবা আলাউদ্দিনের মাইহার ব্যান্ডের ধাঁচে গুণী ছেলে আলী আকবর খাঁ-ও দেশান্তরে গড়ে তুলেছেন এমনই এক সংস্থা। জর্জ রুকার্ট, ভি-জি-যোগ প্রমুখের সাহায্য এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি গড়ে তুললেন ‘দ্য নিউ মাইহার ব্যান্ড’ সংস্থাটি। পশ্চিমী কিছু যন্ত্র এবং কণ্ঠের ব্যবহারে আলী আকবর খাঁ মাইহার ব্যান্ডের আদি রূপটি চালু রাখার যে-পরিকল্পনা নিয়েছেন, তা ডকুমেন্টেশনের কাজে আসবে। আমেরিকায় জনাদশেক ছাত্র এই নিউ মাইহার ব্যান্ডের ক্রমাগত অনুশীলনে তৈরি হয়ে উঠেছেন। এখানেই অবশ্য শেষ নয়। সুইজারল্যান্ডে কেন জুকারম্যানও আশির গোড়ায় তৈরি করলেন ‘বাসেল মাইহার ব্যান্ড’। ভারতীয় সংগীতের বিপুল ঐশ্বর্য এইভাবেই বিদেশের দরবারেও পরম আদরণীয় হয়ে উঠল।
বাহাত্তরে সুরলোকে গেলেন আলাউদ্দিন। ৮০-র গোড়ায় দু-বার; তারপর ফের ৮৭-র নভেম্বরে কলকাতায় এলেন মাইহার ব্যান্ড। উপলক্ষ, বাবা আলাউদ্দিনেরই জন্মের ১২৫ বছর পূর্তি স্মারক উৎসব। তাঁদের ডেকেছেন যথারীতি আলী আকবর কলেজ অব মিউজিক। ১২ নভেম্বর। হাওড়া স্টেশন। সকলেই নামলেন ট্রেন থেকে। কিন্তু কোথায় সেই দু-জন? বলতে না বলতেই কামরার দরজায় এক বৃদ্ধ। ‘ম্যায় হুঁ গিরিধারীলাল’। দেখে আলী আকবর কলেজ অফ মিউজিক-এর নবীন প্রজন্ম আহ্লাদে আটখানা। ১৯৮৪-র সেই ভয়ংকর সুন্দর বৃষ্টির সন্ধ্যাকে যে ওঁরা ভুলতে পারেননি। সে-আলোচনা না হয় পরে। কিন্তু কোথায় গেলেন ঝুররা মহারাজ? না, আসেননি তিনি। আসার জন্য সবরকম চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও শরীরে অনুমতি মেলেনি। তাহলে কে বাজাবেন নলতরঙ্গ? সে-উত্তর অবশ্য মিলেছে যথা সময়েই।
৫৭, হরিশ মুখার্জি রোডের ছিমছাম একতলায় বসে গল্প শোনাচ্ছিলেন শেখর রায়চৌধুরী। মাইহার ব্যান্ডের স্থানীয় ম্যানেজার থেকে কেয়ার-টেকার— সবই তিনি। ব্যান্ডের চোদ্দজন সদস্য ট্রেনের ক্লান্তিতে কিছুটা অবসন্ন। ভাদুয়া ঘিয়ে ভাজা লুচি আর নিখুঁত নিরামিষ রান্নার গন্ধ ভাসছে। ইতিমধ্যে দু-জন গোঁ ধরেছেন— ‘শেখরবাবু, ভায়োলিন খরিদ করনে হোগা। বহুৎ জরুরত’। ওঁদের থামিয়ে ফের একবার শুরু করেন শেখরবাবু— ‘৮৪-তে মহাজাতি সদনে ওঁদের শেষ আইটেম, রাগ ‘মেঘ’। অনুষ্ঠান শেষ হল; আর আপনাকে কী বলব, বৃষ্টিতে মানুষ সমান জল সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে। রিক্শা করে একে একে ওঁদের ডেরায় ফেরত পাঠাই। এরই মধ্যে হারিয়ে গেলেন ঐ দু-জন, ঝুররা মহারাজ আর গিরিধারীলাল’। বলেই বেহালার খোঁজে ছোটেন শেখরদা।
ঝুররালাল থেকে ঝুররা মহারাজ— দীর্ঘ প্রস্তুতি ও সাধনার দুই প্রান্ত। সাধারণ রাগের আরোহণ-অবরোহণে যাঁর গা দিয়ে ঘাম ছুটত, সেই ঝুররালালকে আলাউদ্দিন প্রায় সব যন্ত্রেই পারদর্শী করিয়েছিলেন। তিনি আর গিরিধারীলাল— প্রথম আঠাশের মধ্যে বেঁচে আছেন তো মাত্র এই দু-জনই। কত বয়স হল আপনার? জিজ্ঞাসা করি গিরিধারীজিকে। ছিপছিপে, ঋজু অবয়ব। মাথায় গান্ধি টুপি। দৃষ্টি সিধে। মাইহার ব্যান্ডের সকলের ‘পণ্ডিতজি’। কানে বোধহয় ইদানীং শুনছেন একটু কম। দ্বিতীয়বার বলতে হল একগাল হেসে— ‘ইয়াদ নেহি। সত্তর সে কুছ যাদাই হোগা’। কী কী বাজাতে পারেন আপনি? প্রশ্নের পরেই বুঝেছি, একেবারে সাদামাটা মেঠো হয়ে গেল ব্যাপারটা। পণ্ডিতজি বলেননি কিছু। বললেন দলের অন্যান্য সদস্যরা। সব, সব যন্ত্রে সমান অধিকার ওঁর। এখন অবশ্য বসেন দলের মাঝখানে হারমোনিয়াম হাতে। সাধারণ তিন অক্টেভের অতি নিরীহ-দর্শন একখানি যন্ত্র, মাইহার ব্যান্ডের প্রাণ যা।
রামলখন পাণ্ডে (সেতার), সুশীলকুমার শুক্লা (হারমোনিয়াম), রামলখন শর্মা (সরোদ), গুণাকর শামলে (হারমোনিয়াম), বিজয়কুমার শুক্লা (বেহালা), গোকারণ প্রসাদ পাণ্ডে (বেহালা), সুরেশকুমার চতুর্বেদী (এসরাজ), রামসুমন চৌরাশিয়া (সেতারব্যাঞ্জো), অশোককুমার বডোলিয়া (তবলা), বিজয় দেব সিং (চেলো), রামায়ণ প্রসাদ চতুর্বেদী (সেতার), শৈলেন শর্মা (নলতরঙ্গ) এবং গিরিধারীলাল (হারমোনিয়াম)— চোদ্দজন যন্ত্রি। তিনটি হারমোনিয়াম আর একজোড়া তবলা, একটি নলতরঙ্গ। বাদবাকি সব তারের যন্ত্র। ১৩ নভেম্বর সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে ওঁদের শুরুর নিবেদন রাগ ‘শ্যামকল্যাণ’। কিন্তু, শ্রোতা ক-জন? বড়োজোর শ-চারেক। এরকম কেন? চমৎকার জবাব দিলেন আলী আকবর কলেজ অব মিউজিকের বর্তমান প্রধান উমা গুহ— ‘বিনি-পয়সার অনুষ্ঠান তো! বাড়ি-বাড়ি গিয়ে কার্ড দিয়ে এসেছি। লোক কেন হবে ভাই?’ বাস্তবিকই আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। প্রায় একক চেষ্টায় এই নিয়ে তিনবার মাইহার ব্যান্ডকে উমা গুহ কলকাতায় আনলেন। এবং আনলেন মধ্যপ্রদেশ সরকারের সঙ্গে প্রায় যুদ্ধ করে। মাইহার ব্যান্ড মধ্যপ্রদেশ কলা পরিষদের পরিচালনাধীন। সরাসরি সরকারি সংস্থা এটি। সুতরাং তাঁদের অনুমতি পাওয়াটা যে কী কঠিন বিষয় তা উমা গুহর থেকে বেশি কেউ জানেন না। সম্পূর্ণ অ-ব্যবসায়িক এই সাংগীতিক দৌড়-ঝাঁপকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজন এবং দায় তাই ছিলই। বাস্তবে কী হল? কাগজের বিজ্ঞাপনের জন্য পাওয়া যায়নি স্পনসর, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে অনেকেই আগাগোড়া নিলেন নীরব শ্রোতার ভূমিকা।
রাগ ‘শ্যামকল্যাণ’। চৌতালের আদিতে দুই মাত্রা যোগ করে চোদ্দ মাত্রার আড়া চৌতাল। তাতে সুর বেঁধেছেন আলাউদ্দিন। লয় মধ্য। যুগল তবলার ঠেকা আর বেহালা-সারোদ-সেতারের একমুখী ওঠানামা। বন্দিশটি চমৎকার। মাঝে নলতরঙ্গ। ছোটো-বড়ো বাইশটি বন্দুকের নল। সাধারণ লোহার শিক দিয়ে তাতে ঘা মেরে শুদ্ধ, কড়ি, কোমল অনুষঙ্গ কানে মেপেছিলেন আলাউদ্দিন। ঘষে, মসৃণ করে সুর অনুসারে তা বসানো কাঠের পাটাতনের ওপর। সেখান থেকে আসছে জলতরঙ্গের সুরাভাষ। একটু কড়া, হয়তো কিছুটা ধাতব, সব মিলিয়ে নিখুঁত সুরের উন্মাদনা, যা ব্যান্ডের লয়কে প্রতি মুহূর্তে বাড়িয়ে দিচ্ছে, অথচ বাড়ানোর সেই মুহূর্তটিকে আলাদা করে ধরা যাচ্ছে না। এই যন্ত্রই তাহলে বাজান ঝুররা মহারাজ। শৈলেন শর্মা কিন্তু কখনোই তার অনুপস্থিতি মনে করাচ্ছে না। অনবদ্য ভঙ্গি। দ্রুতলয়ে যখন একের পর এক কঠিন-কঠিন মাত্রায় দুরূহ তেহাইয়ের কাজে ব্যস্ত শিল্পীরা তখন হঠাৎ করেই মনে এল একজন ভারতীয় জুবিন মেহেতার কথা। তার দলে শত জোড়া বেহালা, স্যাক্সোফোন, ড্রাম সেট, পারকাশান, বিবিধ বাঁশি— এ-সবের সামনে আড়াল হয়ে থাকে পাতার পর পাতা নোটেশন। বিশেষ মাইক্রোফোন, বিশেষভাবে তৈরি মঞ্চ এবং বিশেষ প্রবেশমূল্য ছাড়া অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রশ্ন ওঠে না। অথচ এই সাধারণ পোশাকের অতি-অসাধারণ ভারতীয় সংগীতজ্ঞরা শুধুমাত্র শ্রুতিতে ধরে রেখেছেন আলাউদ্দিনের রচনাকে, বংশ পরম্পরায়। এক চুল এদিক ওদিক হয়নি। ওরাই বলছিলেন, অনেকে পরামর্শ দিয়েছেন এটাসেটা বদল করতে। পণ্ডিতজি অবশ্য সে-পরামর্শ মানেননি। অনুষ্ঠানের পরদিন জানালেন গিরিধারীলালও— ‘দেওয়ার আছে এখনও অনেক কিছু। বয়স হয়েছে, সেটাই ভয়। স্মৃতি তঞ্চকতা করবে না তো?’
শুধু মহাজাতি সদনের অনুষ্ঠানেই নয়, কালীঘাট কালীবাড়ি-প্রাঙ্গণ, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন— সর্বত্রই শুনে বুঝেছি, ওঁদের পরিবেশনের গায়ে সেঁটে আছে অরিজিনালিটির শিলমোহর। যেমন, ‘পুরিয়া ধানেশ্রী’। মুখ্য যন্ত্র বেহালা, নলতরঙ্গ যেন খানিকটা চাপা। সেরকমই কম্পোজিশন। আর শুধু লয় নয়, তালের পরিবর্তনও প্রতিমুহূর্তে। তিনতালে শুরু, মাঝে হঠাৎই দাদরায় কম্পোজিশনকে আমূল পালটে নেওয়া। আবার শেষ প্রান্তে তিনটি জবরদস্ত তেহাইয়ের সাহায্যে ফের তিনতালে আসা। আর সবই ওঁরা করছিলেন একে-অপরের দিকে না তাকিয়েই। সুরে সামান্যতম বিচ্যুতি নেই। তার প্রশ্নই ওঠে না। হঠাৎই নিখুঁত সরগম শুরু করলেন ওরা, পুরিয়া ধানেশ্রীতেই। যেন স্বরসাধনার প্রথম পাঠ। ক্রমশ ধরা যাচ্ছিল ব্যান্ডের কেন্দ্রীয় কৌশলটিকে।